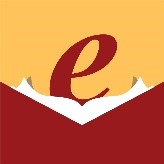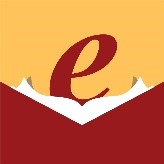সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বঙ্কিমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪ – ১৮ এপ্রিল, ১৮৮৯) বাংলা সাহিত্যে আগমন। সঞ্জীবচন্দ্রের অন্যতম সার্থক এবং সুসমঞ্জস রচনা “পালামৌ”—বস্তুতঃ উনবিংশ শতক থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাঁর সাহিত্যকীর্ত্তি এই “পালামৌ”কে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর গদ্য সাহিত্যে, তাঁর রচনায় লেখকের আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে এই অভিযোগ নানা মহলের সাহিত্য সমালোচকের, স্বয়ং লেখক এই অভিযোগকে অস্বীকার করেননি। তবে একথা অনস্বীকার্য সঞ্জীবচন্দ্রের এই আলস্য ও অবহেলার পাশাপাশি এক অকৃত্রিম সজাগ অনুরাগ তাঁর সাহিত্যে বিদ্যমান যা সচরাচর দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সরস ভঙ্গীতে সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যকীর্ত্তি নিয়ে বলেছিলেন, “তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায়; সে-স্থলে অনেক জিনিস ফেলাছড়া যায় অথচ অল্প জিনিসই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিণী নহে।” এই কৃতী অথচ অলস সাহিত্যিকের অল্প সংখ্যক সাহিত্যের হদিস পাওয়া যায়। অনুজ বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন, “তিনি যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনি তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন”।