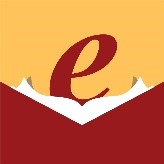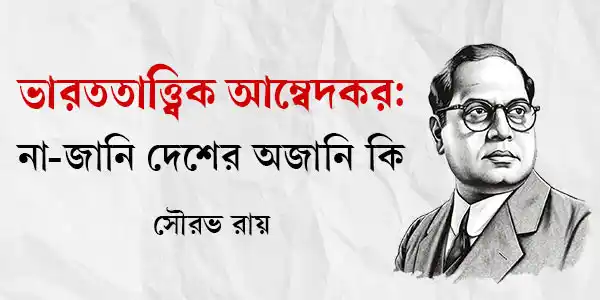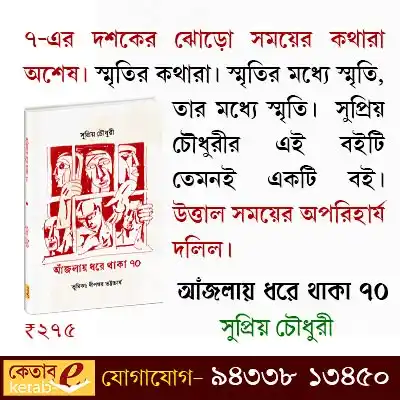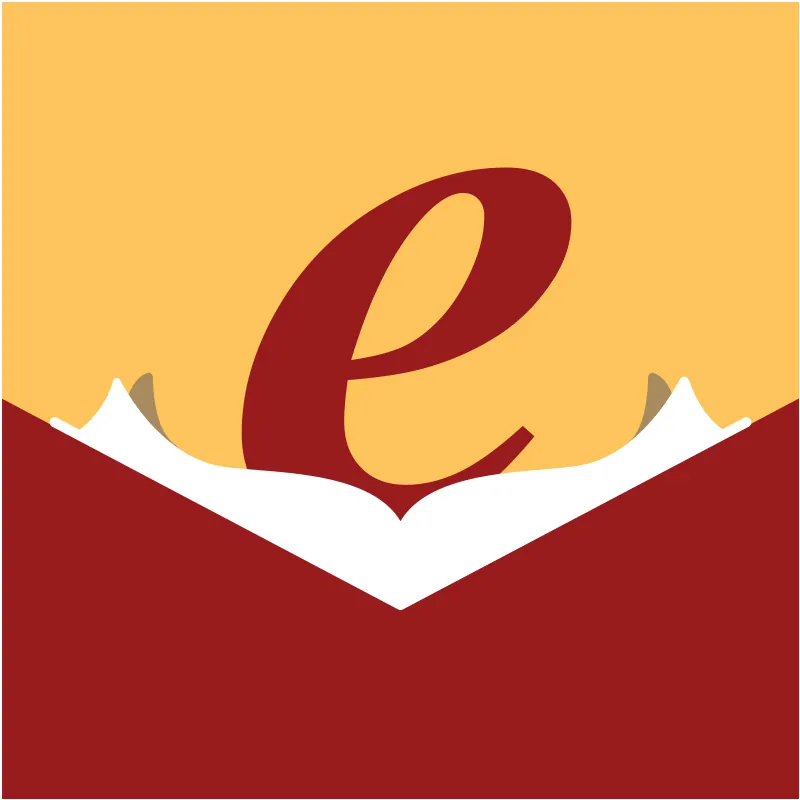আম্বেদকরকে ‘জাতিবাদী রাজনীতিক’ বা সংবিধানের রচয়িতা নয়, এক গভীর ভারততাত্ত্বিক হিসেবে পুনরাবিষ্কার করে এই প্রবন্ধ। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও জ্ঞানচর্চার কাঠামো ভেদ করে লেখক উন্মোচন করেছেন ভারতচিন্তার আড়ালে বিস্মৃত প্রকৃত চিন্তা-চেতনার বিপ্লব, আম্বেদকর যার অন্যতম পথিকৃৎ।
ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের রচনাবলী খুবই সহজলভ্য। ইংরিজি, হিন্দি, মারাঠি এমনকি বাংলাতেও। ভারত সরকার ও মহারাষ্ট্র সরকারের নানা সংস্থা থেকে ছাপা আম্বেদকরের রচনাবলী সংকলিত হয়েছে স্বল্পমূল্যে, উচ্চমানের বিবিধ খণ্ডে। নানা দলিত চেতনা উজ্জীবনী সংগঠন সেগুলি বিনামূল্যে পিডিএফ ডাউনলোডের ব্যবস্থা রেখেছেন তাঁদের ওয়েবসাইটে। নানা ভাষায় তাঁর বহু বইয়ের বিভিন্ন চটি সংস্করণ পাওয়া যায় প্রগতিশীল বা বহুজনিক নানা প্রকাশনীর স্টলে। সহজলভ্য হবার সাথে সাথে আম্বেদকরের লেখা সহজপাঠ্যও বটে। ইংরিজিতে ওঁর যা যা লেখা পড়েছি, সেগুলিতে যুক্তি কখনও কখনও জটিল হলেও ভাষা সরল, গতি সবল, এবং উদ্দেশ্য স্বচ্ছ (সোজাসাপটাভাবে পাঠকের সহমত আদায়)। আম্বেদকরের রচনাশৈলী দুঁদে উকিলি ভাষণের দোষ-রহিত কিন্তু সেই ভাষণশৈলীর সহজাত নানা গুণে ভরপুর।
সহজলভ্য এবং সহজপাঠ্য হলেও আম্বেদকর অবশ্যপাঠ্য নন—না স্কুলে-কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে, না বিবিধমণ্ডলে (অবশ্য ঐচ্ছিকপাঠ্য বা অবসরপাঠ্য হিসাবে ভারতে ধীরে ধীরে জাতে উঠছেন তিনি, কিন্ত বহুদিন ধরেই তাঁর পূর্বাশ্রম আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অবশ্যপাঠ্য)। পণ্ডিতমণ্ডলে আম্বেদকরের নিজস্ব রচনার চেয়েও অধুনাপ্রকাশিত অরুন্ধতী রায়ের ‘দি ডক্টর এন্ড দি সেন্ট: দি আম্বেদকর-গান্ধী ডিবেট: কাস্ট, রেস অ্যান্ড অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট’ অধিক-চর্চিত। ভারতীয় সংবিধানের রূপকার, নীল কোটপ্যান্ট-লাল টাই-সাদা শার্ট-মোটা কালো ফ্রেমের চশমা পরা একটি রাগী-গোছের মানুষ, যিনি গান্ধীজির সাথে কি-জানি-কেন—বোধহয় জাতপাত নিয়েই খুব লড়েছিলেন, এই আবছা ভাবমূর্তিতেই সাবর্ণ জনমানসে আম্বেদকর বেশি প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও ঐচ্ছিকপাঠ্য হিসাবে আম্বেদকরের রচনা যখন পড়ানো হয়, তখন তাঁকে গান্ধীর ‘অপর’, করমচাঁদের ঘনকৃষ্ণ উলটোপিঠ হিসাবেই ধ্যান করা হয়, যাতে কিছুদূর ওই আম্বেদকরমার্গে বিচরণ করে আবার গুটি গুটি পায়ে আমড়াতলার মোড়ে, অর্থাৎ এম কে গান্ধী চৌকেই ফিরে আসা যায়।
কিন্তু ইংরিজিতে যাঁর রচনাসমগ্র চল্লিশ খণ্ডব্যাপী, ব্রিটিশ ভারতের যিনি শ্রমমন্ত্রী, স্বাধীন ভারতের আইনমন্ত্রী, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে অর্থশাস্ত্রে যিনি ডাবল ডক্টরেট, ভারতকে যিনি সরকারি চালক তথা পণ্ডিতের বিহঙ্গদৃষ্টি আর নবযান বৌদ্ধ আন্দোলনের উদগাতা ও সঞ্চালকের তৃণমূলবোধ—এই যুগল-জানালা থেকে সারা জীবন দেখে গেছেন আর তা নিয়ে লিখে গেছেন, ভারতসম্পর্কিত সার্বিক জ্ঞানতত্ত্বে তাঁর একান্ত নিজস্ব কিছু পাঠ কি নেই, যা আমাদের জানা জরুরি?
নেই তাই পড়ছ, থাকলে কোথায় পেতে
সহজ কথায় উত্তর দিতে গেলে, অনেক আছে কিন্তু থেকেও নেই।
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা গৌরী বিশ্বনাথনের ভাষায়: “যে বিশেষাধিকার বলে গান্ধীর পক্ষপাতশূন্য ভাবমূর্তির দেবতায়ন হয়েছে, সেই একই বলে আম্বেদকরের ভাবমূর্তির দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে পক্ষপাতী রাজনীতিক হিসাবে। ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রশস্তিতে গান্ধীর পাশে আম্বেদকরের জন্য জায়গা খুব কমই ছাড়া হয়েছে। এমনকি প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে অস্পৃশ্যতা নিয়ে লেখা বহু বিশিষ্ট সাহিত্যেও আম্বেদকরের অবদান প্রসঙ্গ নিঃশেষে মুছে ফেলা হয়েছে।” (২০০১: ২২০)
আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝি। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রগতিপীঠ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শিল্প ও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে মাস্টার ডিগ্রি করার সময়ে আমাদের কোনো বিষয়ের পাঠ্যসূচিতেই আম্বেদকরের কোনো রচনা ছিল না। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক উৎস পড়তে গিয়ে আম্বেদকরের প্রসঙ্গ এল। বৃহৎসংহিতায় (খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) কাষ্ঠমূর্তি তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠেরও বর্ণবিভাজন করা রয়েছে—দেবদারু হল ব্রাহ্মণ কাঠ, বেলকাঠ ক্ষত্রিয়, শালকাঠ শূদ্র ইত্যাদি। আরও নানা শিল্পশাস্ত্রে রং (যার আরেক নাম বর্ণ) তাদেরও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বিভাজন রয়েছে ফলে সেই রঙের পাথর বা মাটির জাতবিচারও সেইভাবে হয়—লাল পাথর ক্ষত্রিয়, কালো মাটি শূদ্র, শ্বেতবর্ণ সব কিছু অবশ্যই ব্রাহ্মণ। উদাহরণগুলি পড়াতে পড়াতে আমাদের অধ্যাপক যশোদত্ত সোমাজি আলোনে বলেছিলেন—বর্ণবাদ-জাতিবাদ ভারতমানসে কায়েম একটি আদি বাস্তব ব্যবস্থা, যা নেহাতই ঐতিহাসিক বা সামাজিক বা তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক বা খবরকাগুজে বা আইনি বা সাংবিধানিক ভুঁইফোড় হট টপিক নয়। ভারতের যে-কোনো বিষয় আর যে-কোনো পরিপ্রেক্ষিতকে গভীর আর সঠিকভাবে বুঝতে গেলে জাতিবাদ-বর্ণবাদকে বুঝতে হবে ও আম্বেদকরকে পড়তে হবে। এই হঠাৎ পাওয়া গলিপথ বেয়েই আমার আম্বেদকরের লেখার সাথে পরিচয়, নইলে আরও অনেকের মতই আম্বেদকর না পড়ে আমার সব ঠিকঠাকই চলে যাচ্ছিল—বর্ণবাদ-জাতিবাদ মন্দ অতএব তার বিনাশ হওয়া উচিত—এই প্রমিতপন্থার মামুলি মানসিক স্বীকৃতিতে।
জাতিবাদ-বর্ণবাদ যদি ভারতীয় জনগণমানসে কায়েম একটি আদি ব্যবস্থা হয়, ভারতসম্পর্কিত সার্বিক জ্ঞানতত্ত্বে সেই আলোচনার স্থান কেন্দ্রিক হওয়া উচিত এবং তা নিয়ে জীবনব্যাপী গবেষণা, রচনা ও আন্দোলনের সুবাদে আম্বেদকরকে এক প্রমুখ ভারততাত্ত্বিক বলে সবার মেনে নেওয়ার কথা। কিন্তু ভারততত্ত্ব তো দূরস্থান, তাঁকে বর্ণবাদ-জাতিবাদতত্ত্বের কোনো কেউকেটা হিসাবেও মেনে নেওয়া হয় না এই দেশে। এই অবজ্ঞা নিঃসন্দেহে খুবই সচেতন ও কাঠামোগত। কিন্তু একে নেহাতই জাতিবাদী ষড়যন্ত্র বলে হাওয়ায় ঘুসি মেরে বা চোখের জলে বুক ভিজিয়ে কাজ সারলে চলবে না। কারণ তাহলে এর সচেতন, সবিস্তার ব্যবচ্ছেদ করা যাবে না, যা এই লেখাটির মূল উদ্দেশ্য।
পক্ষপাতের পাঁচ পা
এই আম্বেদকর উধাও রহস্যের অন্যতম একটি মূল রয়েছে গৌরী বিশ্বনাথনের ওপরের উদ্ধৃতির একটি শব্দে—‘পক্ষপাত’। ঐতিহাসিকভাবে যে-কোনো প্রমিত জ্ঞানচর্চার, বিশেষত পশ্চিমী ঘরানার জ্ঞানচর্চার আদর্শ হিসাবে একটি আবশ্যিক শর্ত হিসাবে ধরা হয় পক্ষপাতশূন্যতাকে। কারণ, যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানচর্চাকারী নাকি কোনো পূর্বসিদ্ধান্ত ভেবে বা কোনো বাঁধাধরা ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌঁছোবে ভেবে কোনো জ্ঞানলাভের পথে হাঁটে না, সে আবেগহীনভাবে সব লব্ধ জ্ঞানের সত্যতা পরখ করে, সব দিক থেকে তাকে যাচাই করে, এবং এইভাবে যুক্তি ও পক্ষপাতহীনতার কষ্টিপাথরে পাশ করা সব উচ্চমানের জ্ঞান একত্র করে সে তার জ্ঞানের খাড়াই সৌধ বানায়। কিন্তু কোনো পূর্বসিদ্ধান্ত বা ভবিষ্যৎ লক্ষ্য বাঁধা থাকলে নাকি সেই পক্ষপাতী জ্ঞানচর্চাকারী যুক্তির পথ থেকে টলে যাবে, অসত্যের আলোআঁধারিতে ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখবে, রজ্জুকে সর্প বলে ভুল করবে ইত্যাদি। আর এই স্খলনের ফলে তার জ্ঞানসমগ্র পুস্তকের বদলে ইস্তেহার হয়ে উঠবে।
আম্বেদকরের বর্ণবাদ-জাতিবাদবিষয়ক জ্ঞানচর্চায় পক্ষপাতের পরিমাণ যাচাই করার আগে দুটি উদ্ধৃতি পড়া যাক। একটি আম্বেদকরের রাজনীতি নিয়ে, আরেকটি তাঁর রচনা নিয়ে। সমাজতাত্ত্বিক ভিভেক কুমার আমাদের মনে করিয়ে দেন: “একবার আম্বেদকরের সাথে দলিত প্রসঙ্গ আলোচনা করার পর, গান্ধীজী (তাঁর সেক্রেটারি) মহাদেব দেশাইকে বলেন যে আশ্চর্যজনকভাবে আম্বেদকরের মতে তাঁর নাকি কোনো মাতৃভূমি নেই। দেশাই ব্যাখা করেন যে তার কারণ আম্বেদকর জন্মসূত্রে অচ্ছুৎ। খুব অবাক হয়ে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এদ্দিন ভাবতেন যে আম্বেদকর একজন বিবেকবান ব্রাহ্মণ যিনি অচ্ছুৎদের মুখপাত্র।”
অধ্যাপক যশোদত্ত সোমাজি আলোনের লেখায় আমরা পাই: ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত আম্বেদকর তাঁর ‘হু ওয়্যার দ্য শূদ্রাজ’ (‘শূদ্র কারা?’)বইয়ের ভূমিকায় লেখেন, “আমি আমার ব্রাহ্মণবিরোধী রাজনীতির মুখড়া হিসাবে এই বইটি লিখিনি।” কিন্তু খ্যাতনামা মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক আর এস শর্মা পুরো বইয়ের অনুপুঙ্খ পাঠ না করে বই থেকে একটা খুঁত তুলেই এটিকে নস্যাৎ করে দেন, “এক খ্যাতনামা রাজনীতিক এই বইটি লিখেছেন শূদ্রত্বের উৎস সন্ধানে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাঁর গবেষণা শুধু সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুবাদের ওপর নির্ভরশীল। আরও দুঃখের কথা এই যে, লেখক দেঁড়েকষে শূদ্রত্বের এক মহান উৎস সন্ধানে উদ্যোগী। আজকাল নিচু জাতির শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে এই প্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।”
আম্বেদকর নিজের রাজনীতিচর্চা আর জ্ঞানচর্চাকে আলাদা রেখে তথাকথিত নিরপেক্ষতার সাধনা করেননি। তেমন আবার নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণত্বের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে জাতিবাদ-বর্ণবাদকে শুধু একপাক্ষিক ন্যায়-অন্যায়ের হিসেব দিয়ে বুঝে ক্ষান্ত হননি, তাকে ঐতিহাসিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সব দিক থেকে বুঝতে আর বোঝাতে চেয়েছেন। সে-কারণেই তাঁর রাজনীতি শুধু চলছে না-চলবে না-তে আটকে থাকেনি। অন্যদিকে গান্ধী এবং শর্মার মতে, আম্বেদকরের মতো এক শূদ্রের না থাকার কথা নিজের শূদ্রত্বকে নিজে বোঝার ক্ষমতা কিংবা সেই শূদ্রত্বের অবিচার ঘোচানোর জন্য রাজনৈতিক লড়াই করার ক্ষমতা। দুটি ক্ষেত্রেই যাঁর কাজ (পড়ুন বামুনের) তারই সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে (আম্বেদকরের নিজের জাত মাহাররা আবার বৃত্তিগতভাবে লড়াইতে পাকা, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পুরোনো হিস্যা)। কিন্তু তা সত্ত্বেও, আম্বেদকরের দেখানো আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তিভূত ব্রাহ্মণত্বকে গাল পেড়ে (ব্রাহ্মণ্যবাদী হলেও গান্ধী কিন্তু জাতে বামুন নন, তিনি বানিয়া অর্থাৎ বৈশ্য) কাজ সারলে আমাদের চলবে না। আম্বেদকরের জ্ঞানচর্চায় তাঁর নিজের সংজ্ঞায়িত নিরপেক্ষতাকে পরতে পরতে খুলে দেখতে হবে।
ভারতচর্চার শাখাপ্রশাখা ও আম্বেদকরের জল-অচল জ্ঞানচর্চা
আম্বেদকরকে এই লেখার শিরোনামে আমি ‘না-জানি’ দেশের ‘অজানি কি’ হিসাবে উল্লেখ করেছি। এই দুটো বিশেষণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য একটু ভেঙে বললে আম্বেদকরের রাজনীতিচর্চা-জ্ঞানচর্চার একঘরে-করণের ঐতিহাসিকতা-তাত্ত্বিকতা আলোচনার একটু মুখড়া হবে।
নিজে অচ্ছুৎ মাহার জাতিতে জন্মানোর পরে—ও সেই জীবনজানালা দিয়ে ব্রাহ্মণত্বকে বুঝতে বুঝতে ধাপে ধাপে শিক্ষাগত আর বৃত্তিগত যোগ্যতার শিখরে ওঠার চর্যা—এই দোরোখা যাপন তাঁর রাজনীতিচর্চা-জ্ঞানচর্চার কাঠামো এক অনন্যপূর্ব ছাঁদে গড়ে দেয়। তিনি ছিলেন বম্বের এলফিনস্টোন স্কুলের প্রথম দলিত ছাত্র, পরে বম্বে ইউনিভার্সিটির এলফিনস্টোন কলেজে পড়াশুনা, সেখান থেকে বরোদায় সরকারি চাকরি আর তারপর বরোদার রাজার স্কলারশিপে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি আর সেখান থেকে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স—এই যাত্রা, আর সেই নিশিতকঠিন পথের বিরাট অর্জন তৎকালীন উঁচু জাতির উচ্চবিত্ত শিক্ষিত লোকের কাছেও ছিল অভাবনীয়। আম্বেদকরের ইংরিজি আন্তর্জাতিক জ্ঞানশিক্ষায় ছিল মার্ক্স থেকে ম্যাক্সমুলার সবার উজ্জ্বল উপস্থিতি, সাথে ছিল হাড়ভাঙা খাটনিতে শেখা সংস্কৃত জ্ঞান, এবং ছিল জাতিবাদ-বর্ণবাদকে তাঁর যে ভারতীয় পূর্বজরা যাপন আর জ্ঞান, এই যুগলবোধ থেকে দেখেছেন—যেমন, জ্যোতিবা ফুলে, স্বামী ধর্মতীর্থ—তাঁদের রচনার গভীর প্রভাব। তাই এইসব লব্ধ জ্ঞানের শাখাপ্রশাখার তুলনা করে, যেখান থেকে যতটা তাঁর নিজের সঠিক বলে মনে হয়েছে তাই নিয়ে আম্বেদকর গড়েছিলেন তাঁর জীবনব্যাপী রাজনীতিচর্চা-জ্ঞানচর্চা। কিন্তু আম্বেদকরের সতীর্থদের জাতিবাদ-বর্ণবাদ বিশ্লেষণে উপরোক্ত এই বিবিধ শাখাপ্রশাখার কোনো-না-কোনো একটিতে খামতি ছিল। তাই ভারতের বিরাট-জটিল জাতিবাদ-বর্ণবাদের অনেকটাই তাঁদের খণ্ডবিশ্লেষণের আওতার বাইরে রয়ে গেছিল ‘না জানি দেশ’ হিসাবে। এইখানে বলে রাখা ভালো যে আম্বেদকরের আগে, পরে, আর সমসময়ে দেশি-বিদেশি অনেক পণ্ডিতরাই জাতিবাদ-বর্ণবাদ নিয়ে লিখেছেন আর ভেবেছেন, আম্বেদকরের মতো জীবনভর না হলেও।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
ওপরে আম্বেদকরের জ্ঞানচর্চাপদ্ধতির এই বিবরণ পড়ে যদি একে পক্ষপাতশূন্য সেরার সেরা, সর্বজ্ঞানীবন্দিত হবার উপযুক্ত জ্ঞান বলে মনে হয়, বাস্তব পরিস্থিতিতে এর মূল্যায়ন ছিল ঠিক তার বিপরীত। বরং আম্বেদকরের লব্ধ জ্ঞান ভারতজ্ঞানচর্চার যে বিভিন্ন ঘরানা আছে তার কোনোটির মান্য রীতিরেওয়াজের সাথে খাপ খায় না। জ্ঞানচর্চার রীতিরেওয়াজদের এইক্ষেত্রে বহু-বছর-লালিত, বহু-পণ্ডিত-পালিত, ঐতিহাসিকতাপুষ্ট পক্ষপাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। তাই সেইসব ছাঁচে খাপ না-খাওয়াতে পারার কারণে, নানা ফাটলের ফাঁক দিয়ে হারিয়ে যায় আম্বেদকরের ‘অজানি কি’ জ্ঞানচর্চার অবদান।
সবশেষে, ভারতসম্পর্কিত জ্ঞানতত্ত্বে জাতিবাদ-বর্ণবাদের স্থান যে পরিসরে নয়, একেবারে কেন্দ্রে, আম্বেদকরের জ্ঞানচর্চার এই প্রতিপাদ্য সেই আমলের সমস্ত মান্যরাজনীতিচর্চা—তা জ্ঞানের রাজনীতিই হোক বা শাসনের—ও দেশভক্তিবাদের গভীর পরিপন্থী ছিল। স্বাধীনতা পাবার মুখে যখন ভারতচিন্তার ধারা সর্বতোভাবে ‘মেরা ভারত মহান (থা—হ্যায়—রহেগা)’-এর খাতে বইছিল, তখন বর্ণবাদ-জাতিবাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সেতু বেঁধে দেওয়া আম্বেদকরীয় জ্ঞানচর্চা-রাজনীতিচর্চা ছিল সেই সোনার ভারতের জন্য এক মূর্তিমান কলঙ্ক এবং উচ্চবিত্ত-উঁচুজাত কংগ্রেসমুখ্য শাসকশক্তির কাছে এক বড়ো বিপদ। গণমত তখন ছিল যে বিভেদকামী ইংরেজ নিচুজাতকে খেপিয়ে তুলেছে নিজেদের স্বার্থে, রাজনৈতিক আত্মপরিচিতি দেবার লোভ দেখিয়ে (কমিউনাল এওয়ার্ড ১৯৩২)। কিন্তু এই রাজনৈতিক বিভেদ যে ঐতিহাসিকভাবে হিন্দুসমাজের নিজস্ব বিভেদব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত সে-বিষয়ে নীরবতা ছিল হিরণ্ময়। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, ভারতের বর্ণবাদ-জাতিবাদকে ঐতিহাসিকভাবে বুঝতে গিয়ে তৎকালীন ভারতের ইতিহাসগবেষণাকে, হিন্দুত্বকে আর ভারতসংস্কৃতিকে নতুনভাবে বুঝতে-শিখতে ও লিখতে হয় তাঁকে। সব দিক থেকেই তাই তিনি খাপছাড়া সাব্যস্ত হন। আর বিরুদ্ধপক্ষের অভিযোগ জমে ওঠে যে তাঁর তলোয়ার সদাই খাপখোলা।
ভারতজ্ঞানচর্চার এই যে রীতিরেওয়াজগুলি, যেগুলিকে আমি মহাপক্ষপাত বলে গাল পাড়লাম? সেগুলি কী কী? একে একে তাদের মোড়ক খুলে দেখা যাক, তারপর সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মিলিয়ে দেখব আম্বেদকরের জ্ঞানচর্চার ভারত-ইতিহাসতত্ত্ব আর তাঁর বর্ণবাদ-জাতিবাদ বিশ্লেষণকে।
আদিম কালের বামুনে নথি, তোড়ায় বাঁধা পুণ্যিপুঁথি
প্রথমেই আসা যাক আদি ভারততত্ত্ব, যাকে ইন্ডোলজি বলা হত সেই ভারত-জ্ঞানচর্চার রীতিরেওয়াজগুলির দিকে। এর আদি উৎস উপনিবেশিক, সাহেবদের ভারতকে বোঝার উদ্দেশ্য থেকে। তাই এর পদ্ধতি সবসময় উৎসসন্ধানী এবং লিখিত পুঁথি নির্ভর—যেই পুঁথিগুলির বেশিরভাগই সংস্কৃত (কিংবা পরবর্তী কালে পালি) এবং সেই জ্ঞানচর্চার রক্ষক আর চর্চাকারী ব্রাহ্মণেরা। গবেষণাপদ্ধতির এই পুঁথি-অতিনির্ভরতা থেকে তৈরি হয় এক অনাদি-অখণ্ড-অনাহত গরিমাময় ভারতের ধারণা, যাতে অতীতে (অন্তত নাকি মুসলমানেরা আসার আগে) সবই ভালো ছিল, এবং সব কিছুই ছিল (মেঘনাদ সাহার বিখ্যাত বক্রোক্তি ‘সবই ব্যাদে আছে’) এবং এখন তার থেকে যা যা খারাপ হয়েছে তা আমাদের নিজের দোষে এবং আধুনিকতার দোষে। যেমন বর্ণবাদ পুণ্য বৈদিক যুগে এক কার্যকরী শ্রমবিভাজন প্রথা ছিল যার থেকে মামলা কালে কালে একটু বিগড়ে গিয়ে অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির উদ্ভব হয়েছে যা আধুনিক শিক্ষার আলো আর আইনের শাসন পেলেই ঘুচে যাবে। মোটের ওপর এই বিশ্বাস সেকালের সব জ্ঞাণীগুণী (রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী কেউ বাদ নেই) আর জ্ঞানচর্চাকারীদের মনে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। এর একটি প্রতিপাদ্য ছিল—ইন্দো-ইউরোপীয়রা ফর্সা-নাকউঁচু-তাগড়াই আর্যরা ভারতে বহিরাগত এবং তারাই ভারতে এসে সভ্যতর উঁচু জাতি হয়ে বসেছে আর ভারতের আদি অধিবাসী কালো-রোগা-বেঁটে-খাঁদা অসভ্যতরদের দাবিয়ে ছোটো জাতি করে রেখেছে। সাহেব শাসক আর দেশি শাসিতদের কাছে দুইভাবে সমান মান্যতা পায় এই প্রতিপাদ্য। প্রথমত উচ্চ জাতিভুক্ত হওয়ার ফলে, এটি শাসকদের শাসনের ‘স্বাভাবিক অধিকার’ দান করে। দ্বিতীয়ত এটি বহিরাগতদের দ্বারা শাসিত হবার লজ্জা (ভারতীয়রা যদি এতই মহান তবে পরপদানত কেন?) নিবারণ করে। যেহেতু আর্যরা আদতে ইউরোপীয়, তাহলে ব্রিটিশ শাসন তো ইউরোপশাসিত ভারতের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে মাত্র দুশো বছরের এক আধুনিক অধ্যায় মাত্র। আর শাসিতদের মধ্যে যারা উঁচু জাতির তাঁরা শাসকজাতির উত্তরপুরুষ হবার বিশ্বাসে গোপনে গর্বিত হন আর স্বাধীন ভারতে নিচু জাতিকে পরপদানত করার জোর পান। ওরিয়েন্টালিস্ট ইন্ডোলজি যা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের দ্বারা পুষ্ট জ্ঞানভাণ্ডার (শুধু ব্রিটিশ নয়) তা একভাবে ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী জ্ঞানভাণ্ডারের এক ইউরোপমান্য সংস্করণ, কারণ নিজের অতীতকে জানার জন্য শিক্ষিত ভারতীয়দের যে রাস্তা ছিল তা আগেই গড়ে দিয়েছিল ইউরোপীয় ভারতচর্চা যা ব্রাহ্মণ্যবাদী জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাপারটা অনেকভাবেই ভারতের মাটিতে ফলানো তুলো ব্রিটেনের ম্যানচেস্টারে বোনা কাপড় হয়ে ভারতে ফিরে আসার মতো। ভারতীয়দের দাম দিয়ে সে-কাপড় কিনতে হত।
কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাসচর্চার এই বামুনে পুঁথিনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। কারণ মান্য উৎস হিসাবে আর অন্য কিছুকে মেনে নেওয়া হত না। অঙ্কবিদ-ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি যেভাবে পুরোনো মুদ্রার ওজন, স্থাপত্য এবং পুঁথি একত্র করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে নতুনভাবে পড়েছিলেন, সে অসাধারণত্ব শুধু তাঁরই। আম্বেদকরকেও অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত পুঁথির ওপরেই। বামুনে পুঁথি পড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকে বোঝা মাছেদের জলে বাস করে জলকে বোঝার মতোই কঠিন। কারণ সব ব্রাহ্মণ্যবাদী পুঁথি মনুস্মৃতির মতো শূদ্রদের সোজাসাপটা ভাষায় হীন প্রতিপন্ন করে না। অতএব সেই কুটিল-গম্ভীর ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বরূপ বোঝার জন্য এবং তার মাধ্যমে জাতিবাদ-বর্ণবাদকে বেনাকাব করার জন্য আম্বেদকরকে গভীরভাবে খুঁটিয়ে পড়তে হয়েছিল এইসব সংস্কৃত পুঁথি আর সেগুলিকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হয়েছিল বৌদ্ধ পালি পুঁথির সাথে (কিন্তু সব বৌদ্ধ পুঁথি পালিতে লেখা নয় আবার সব ব্রাহ্মণ পুঁথি সংস্কৃত নয়)। এই চর্চার ফলে আম্বেদকরের রচনায় প্রচলিত ভারত-ইতিহাসের ছাঁচ ভাঙা হতে থাকে। সেই কারণেই ‘অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট’-এ আম্বেদকর সুস্পষ্টভাবে লিখতে পারেন: “বর্ণবাদ-জাতিবাদ শ্রমবিভাজন নয়, শ্রমিক বিভাজন।” পুঁথি-অতিনির্ভরতার আর শিলাশাসন-তাম্রশাসন-নির্ভরতার আরেক কুফল—ভারতের ইতিহাসের রাজনীতিচর্চা শুধু শাসকরাজার রাজত্বকালের শুরু এবং শেষ নির্ণয় করাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ধর্ম, ভারতের সমাজ সব কিছু থাকে বায়ুভূত আর গ্রন্থভূত। বিশেষত প্রাচীন ভারতের ধর্ম থাকে মোটের উপর তূরীয় বেদান্তিক রূপে, বৌদ্ধ ধর্মও থাকে শুধু ক্ষমাঘনতা আর করুণার নিদর্শন হিসাবে। সব সংঘাত আর সামাজিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গ আর উল্লেখ ধুয়ে মুছে যায়। এর বিপ্রতীপে আম্বেদকরের প্রাচীন ভারততত্ত্ব ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যশোদত্ত সোমাজি আলোনে এই বৈপরীত্য আমাদের বিশদে বুঝিয়ে দেন: “বহ্মজাল সুত্ত আর অম্বঠঠ সুত্ত ছিল আম্বেদকরের কাছে দুটি জরুরি উৎস। মৌর্যযুগের শেষে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকাল থেকে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের যে ক্ষয় ও ব্রাহ্মণ্যবাদের যে পুনরুত্থান শুরু হয় তা ভারতকে সুবর্ণময় গুপ্তযুগের দিকে নিয়ে যায়—এই হল ভারতের ইতিহাসের অতিপ্রচলিত অভিমত। কিন্তু আম্বেদকর স্বামী ধর্মতীর্থের ইতিহাসতত্ত্বের অনুসারী। এই তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে বলে যে বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতি মৌর্যযুগের শেষে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ছিল। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের ও তৎসংক্রান্ত সংস্কৃতির পুনরুত্থান স্বর্ণযুগে উত্তরণ নয়, তা অধঃপতন, এই নিম্নলিখিত কারণে:
(১) ব্রাহ্মণদের রাজ্যশাসন করার অধিকার দেয় এমনকি ক্ষত্রিয় রাজাকে হত্যা করার শাস্ত্রীয় অধিকারও;
(২) ব্রাহ্মণদের সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে উপরে, সবচেয়ে বিশেষাধিকারভোগী শ্রেণীতে বসায়;
(৩) বর্ণকে জাতিতে পরিবর্তন করে;
(৪) বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ আর ঘৃণার বীজ বোনে।
(৫) নারী আর শূদ্রদের মর্যাদাভ্রষ্ট করার পাকা ব্যবস্থা করে;
(৬) জাতিবাদ-বর্ণবাদের ধাপকাটা অসাম্যব্যবস্থা গড়ে তোলে; এবং
(৭) কঠোর আইনি ব্যবস্থা আর অপরিবর্তনীয় সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে।”
এই প্রতিপাদ্যের প্রভাবে লেখা আম্বেদকরের ‘রেভলিউশন এন্ড কাউন্টাররেভলিউশন ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া’ আবার আপাতদৃষ্টিতে খুব গোঁড়া মার্ক্সবাদী ভিতের মনে হয়, কিন্তু তার ধারা আর বিবরণ মোটেই একলষেঁড়ে নয়।
এই প্রতিপাদ্যগুলি যাচিয়ে দেখার জন্য আম্বেদকরকে সব ব্রাহ্মণ্য পুঁথি সময় মিলিয়ে মিলিয়ে পড়তে হয়, বিশেষ করে বেদান্ত সূত্র, গীতা, আর পুরাণগুলি। খতিয়ে দেখতে হয় কোথায় কোথায় বৌদ্ধপুঁথি আর ব্রাহ্মণ্যপুঁথির আখরে মিল, অমিল, গরমিল। পুঁথির লেখনকে শুধু শব্দপ্রমাণ হিসাবে না ধরে পুঁথিলেখকের মন এবং তার সামাজিক অবস্থানকে আরও ভালোভাবে বুঝতে চেয়েছেন তিনি ভারতীয় এবং পশ্চিমী লেখকদের লেখা পড়ে, এবং সেই আলোয় বুঝতে চেয়েছেন পুঁথির আখরকে। আর এইভাবে খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় আম্বেদকরের ভারতচর্চার অপক্ষপাতকে, যেখানে প্রমাণাভাবে তিনি ফুলে বা ধর্মতীর্থের প্রতিপাদ্য খারিজ করেন কিংবা আর্যরা সম্পূর্ণরূপে বহিরাগত এই তত্ত্বের বিরোধী প্রামাণ্য ঐতিহাসিকতা গঠনের প্রচেষ্টা করেন, যা রাজনৈতিকভাবে তাঁকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাভারকর-গোলওয়ালকরের সাথে এক দলে ফেলে দেয়, যাঁরা সম্পূর্ণ অন্য উদ্দেশ্যে আর্যদের বহিরাগমন তত্ত্ব খারিজ করতে চাইতেন নানা উদ্ভট গালগল্প দিয়ে। কিন্তু পাছে তাঁকে বা তাঁর লেখাকে কেউ ভুল রাজনৈতিক রঙে রাঙায়, এই ছুঁতমার্গীভীতি আম্বেদকরের ছিল না, যা তাঁকে কোনো তত্ত্বের সম্পূর্ণ ময়না তদন্ত করা থেকে নিরস্ত করবে। যেমন, ধর্মকীর্তির প্রতিপাদ্য, বর্ণবাদ অভিযোজিত হয়ে জাতিবাদে পরিণত হয়েছে, এটি আম্বেদকরের মতে ভুল ব্যাখ্যা। ‘ইন্ডিয়া অ্যান্ড কমিউনিজম’-এ তিনি লেখেন—“জাতিবাদ বর্ণবাদ থেকে অভিযোজিত হয়নি। সঠিকভাবে বলতে গেলে এই পদ্ধতি অভিযোজনের বিপরীত। জাতিবিভাগ বর্ণবিভাগের বিকৃতি। বর্ণব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজনের ধাপকাটা অসাম্যটুকু ধার করে জাতিব্যবস্থা তৈরি হয়েছে।” এবং ব্রাহ্মণরা একা-একাই জাতিবাদ ভারতের সবার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, ধর্মকীর্তির এই ব্যাখ্যা আম্বেদকরের মতে একটি অতিসরলীকরণ। বর্ণবাদ-জাতিবাদ একটি ব্যবস্থা যা নানা পদ্ধতি, সুবিধা আর ভিতের ওপর টিকে থাকে, তা শুধু ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত অন্যায় বা বিশ্বাসের ব্যাপার না।
লাল ইতিহাস শ্রেণীতে থেমে যায়, লাল ইতিহাস জাত এড়িয়ে যায়
আদি ভারততত্ত্ব (ইন্ডোলজি, সাহেবদের প্রাচ্যবিদ্যা বা ওরিয়েন্টোলজি থেকে সম্ভূত) আমাদের এক রাজনীতিহীন ভারত-ইতিহাসের ধারা দেয়—যেখানে রাজনীতি শুধু রাজাদের সিংহাসন থেকে ওঠা-নামা আর রাজত্বকালের শুরু এবং শেষ দিয়ে নির্ধারিত হয়। সেই ধারায় ধর্ম শুধুই আত্মগত এবং তুরীয়, কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তি নয়, সংস্কৃতি শুধুই রাজদরবারি ললিতকলা। সেই ধারা থেকে ভারতের মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক ধারা সরে দাঁড়ায়—বস্তুবাদী, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অতীতকে দেখতে চায়। কিন্তু আম্বেদকর জাতিবাদ-বর্ণবাদকে বুঝতে গিয়ে যেভাবে ভারত-ইতিহাসকে অন্যভাবে বুঝতে ও হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মকে পরস্পরের ‘অপর’ হিসাবে বুঝতে বাধ্য হয়েছিলেন, ভারতের মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকরা কিন্তু বর্ণ-জাতি-কে অন্যভাবে বোঝা তো দূরস্থান, বোঝার যোগ্য বলেই মনে করেননি। আর বর্ণবাদ-জাতিবাদের সাথে ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যা মার্ক্সীয় জ্ঞানচর্চার কাছে খুবই অরুচিকর একটি বিষয়। যে জটিল আর কায়েমি কিন্তু সততপরিবর্তনশীল বর্ণ-জাতিবাদী বিভাজনব্যবস্থাকে সারা ভারত চিরকাল বুঝে এসেছে এবং বুঝে চলেছে, তাকে মার্ক্সবাদী ইতিহাসচর্চার ধারা শ্রেণীবিভাজনের (ক্লাস ডিভিশন) মাধ্যমে বুঝতে চেয়েছে। যদিও শ্রেণী মার্ক্সবাদী মতে নেহাতই গোদা আয়ভিত্তিক এক বিভাজন নয়, একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভাজনও বটে কিন্তু মনে রাখা ভালো মার্ক্সের শ্রেণীবিভাজনতত্ত্ব আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থার নিরিখে গঠিত। কিন্তু শরদ পাটিল, যিনি ছিলেন একইসাথে মার্ক্স, ফুলে ও আম্বেদকর অনুসারী ঐতিহাসিক, শরদ পাটিল আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, আম্বেদকর নিজেও অংশত ছিলেন তাঁর জাতিবাদ-বর্ণবাদচর্চার প্রথমদিকে এই ধারণার শিকার, যদিও পরে এই বিষয়ে তাঁর ধারণা আরও সুস্পষ্ট হয়। ‘ইন্ডিয়া অ্যান্ড কমিউনিজম’-এ, আম্বেদকরের নিজের কথায়—“শ্রেণীব্যবস্থা বর্ণব্যবস্থার সমার্থকও নয়, বিপরীতার্থকও নয়। যদিও জাতি এবং বর্ণ আলাদা, কিন্তু জাতিবাদ আর শ্রেণীবাদের যোগ শুধু ধাপকাটা অসাম্যবাদের মাধ্যমে না। হিন্দুদের মধ্যে যেমন অগণিত জাত রয়েছে, নানা জাত আবার নানা শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু একইসাথে নিজের জাতির অবস্থান সম্পর্কে এবং নিজের শ্রেণীর গরিমা সম্পর্কে সচেতন। এর মধ্যে কোন সচেতনতা তাঁর মধ্যে কখন কাজ করে তা নির্ভর করে কোন জাতের সাথে তার নিজের জাতের সংঘাত লাগছে তার ওপর। যদি সেই জাত তার নিজের শ্রেণীর ঘেরাটোপের মধ্যে হয় তাহলে সে নিজের জাতি-সচেতনতা দেখায়। আর সেই জাত যদি তার নিজের শ্রেণীর ঘেরাটোপের বাইরে হয়, তাহলে সে নিজের শ্রেণী-সচেতনতা দেখায়। এর প্রমাণ হিসাবে যে কেউ বম্বে আর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ব্রাহ্মণবিরোধী আন্দোলনকে খুঁটিয়ে দেখতে পারেন। হিন্দুরা যে একইসাথে জাতিসচেতন আর শ্রেণীসচেতন তা সেখান থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়।” কিন্তু শ্রেণীসচেতনতা বলতে আম্বেদকর এখানে যা বোঝাচ্ছেন তা ঠিক মার্ক্সকথিত বিপ্লবোপযোগী শ্রেণীচেতনা নয়, হিন্দুদের নিজশ্রেণীগরিমা সম্পর্কে সচেতনতা। মার্ক্সবাদী ইতিহাসের বর্ণবাদ-জাতিবাদ সংক্রান্ত সব প্রতিপাদ্য—অর্থাৎ ‘জাতি এবং শ্রেণী সমার্থক’ থেকে ‘শ্রেণী জাতিতে পরিবর্তিত হয় অন্তর্গতির মাধ্যমে’ থেকে ‘প্রাচীন ভারতে শ্রেণীবিভাজন দেখা দিয়েছিল আগে, জাতিবিভাজন পরে’ অতএব ‘শ্রেণীর স্পষ্টতম প্রকাশ হয় জাতির মাধ্যমে’—এগুলির সব কটিই আমাদের বলতে চায় যে, আগে শ্রেণীবাদ বুঝতে হবে, তাহলে বর্ণবাদ-জাতিবাদ আপনাআপনি বোঝা যাবে। শরদ পাটিল আমাদের বলেন যে ভারত সম্পর্কে বিশেষভাবে অজ্ঞ ১৮৫৩ সালের যুবক মার্ক্স বলেছিলেন যে (তখনও ইন্ডোলজি চর্চার শিকড় ভারতে চাড়ায়নি), আধুনিক শিল্পায়ন ঠিকঠাক শুরু হলেই শ্রেণীসংঘাত শুরু হবে এবং এসব পুরোনো জাতপাতব্যবস্থা ঘুচেমুছে যাবে। কিন্তু ১৯৭৯ সালে সিপিআই-এর পণ্ডিতপ্রবর এস জি সরদেশাই বলেছিলেন যে ভারতে আধশতাব্দী কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরেও মার্ক্সের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়নি। কিন্তু মার্ক্সবাদী ভারতীয় ইতিহাসের ধারার মধ্যে এই পূর্বসংস্কার রয়েই গেছে। ইন্ডোলজির সাথে আম্বেদকরের জ্ঞানচর্চার সম্পর্ক যেমন সাদায়-কালোয় ছিল না, তেমনই মার্ক্সবাদী ইতিহাসচর্চার সাথে বা তার তত্ত্বদৃষ্টি বা ইডিওলজির সাথে আম্বেদকরের বিশ্লেষণী চেতনা আদায়-কাঁচকলায় ছিল না। আনন্দ তেলতুম্বড়ের মতে আম্বেদকরের সংঘাত ছিল ভারতীয় মার্ক্সবাদীদের আন্দোলনপদ্ধতি আর জাতিব্যবস্থা-অচেতনতা নিয়ে।
ভারতীয় সমাজতত্ত্ব: সিঁড়ি ভাঙ্গার অতিসরলীকৃত অঙ্ক
স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় সমাজতত্ত্ব ইতিহাসনির্ভরতা অর্থাৎ পুঁথি-তাম্রশাসন-শিলাশাসন নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ‘বুক ভিউ’ পুরোপুরি বদলে ফেলে আগাগোড়া ‘ফিল্ড ভিউ’ নেব ভাবা সহজ, করা কঠিন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতীয় সমাজতত্ত্বের মধ্যে জাতীয়তাবাদ আগাগোড়া ঠাসা থাকায়, হরেদরে এই ‘ফিল্ড’-এর সংজ্ঞা অর্থাৎ ‘ভারত’ নামক ক্ষেত্রটির সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায় ভারত নামক রাষ্ট্রের সীমানা। কিন্তু প্রাচীন-জটিল-বিরাট ভারতীয় সমাজের গড়ন-ধরন-নড়ন-চড়ন ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ এর মাঝরাত থেকে কার্যকর হওয়া একটা গণ্ডি দিয়ে বেঁধে দেওয়া যায় না। আর তাই দিয়ে উপনিবেশবাদী জ্ঞানচর্চার মহীরুহ একবারে উপড়েও ফেলা যায় না। আদি ভারততত্ত্ব বা ইন্ডোলজি এবং তৎসম্ভূত ভারতীয় ইতিহাসতত্ত্বের ক্ষেত্রে যেমন ভারতইতিহাসের সামাজিকতা ও রাজনৈতিকতা মিলিয়ে যায় লিখিত ঐতিহ্য আর অনাহত সংস্কৃতিতে, মার্ক্সবাদী ইতিহাসে ভারতের সামাজিকতাকে অর্থনৈতিক তত্ত্বের খাপে এঁটে দেওয়া হয়, তেমনি ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে, সমাজতাত্ত্বিক সুজাতা পটেলের মতে, ভারতের সামাজিকতাকে এক ঐতিহ্য বলে ধরে দেওয়া হয়, যার কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক দিক নেই। আর যেহেতু এই ঐতিহ্যকে ভারতীয় সমাজতত্ত্ব পুঁথির লেখন দিয়ে বুঝতে চায় না, তা বোঝানো হয় বিদেশি সমাজতত্ত্ব আর দেশি গ্রামের মাঠগবেষণা বা ফিল্ডওয়ার্ক দিয়ে।
সুজাতা পটেলের লেখা থেকে আমরা পাই যে, ভারতীয় সমাজতত্ত্ব চর্চার শুরু ব্রিটিশ রাজপুরুষ ও আমলাদের সরকারি ও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে—প্রথমে ভারতীয় ভাষাচর্চা ও পরবর্তীকালে ভারতের সমাজচর্চার মধ্যে দিয়ে, যেখানে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ইউরোপীয় ‘স্টক’ আর ‘রেস’-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে থাকে আর সাথে যোগ হয় ইউরোপমান্য ব্রাহ্মণ্যবাদী পুঁথিলব্ধ বর্ণবাদের জ্ঞান। এই যদি স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ভারতীয় সমাজতত্ত্বচর্চার ‘বুক ভিউ’ হয়, তাহলে ‘ফিল্ড ভিউ’ ছিল ভারতীয় গ্রামভিত্তিক। ইংরেজ সোশ্যাল এনথ্রোপলজিস্ট এলফ্রেড ব়্যাডক্লিফ-ব্রাউনের দ্বারা তত্ত্বায়িত(যাতে শুধু ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদেরই শুধু না, গান্ধীরও ছিল গভীর বিশ্বাস) ভারতীয় গ্রাম এক লক্ষ্মণরেখায় বাঁধা, যেন দ্বীপবন্দি এক স্বনির্ভর সমাজ যেখানে সব জাতির লোকেরা মিলেমিশে সুখে-দুঃখে থাকে। ভারতীয় গ্রামের এই ছবি জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় গভীরভাবে প্রোথিত। এই বিদেশি বা উঁচুজাতির গ্রামবাসী বা শহুরে পণ্ডিতমান্য গ্রামের চিন্তার সাথে আম্বেদকরের মতো একজন নিচু জাতের মানুষের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা একেবারেই মেলে না। ভারতীয় সংবিধানের খসড়া কমিটির নভেম্বর ৪, ১৯৪৯-এর মিটিংয়ে আম্বেদকর বলেন, “ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর গ্রামবাসীদের প্রতি অসীম প্রেম সত্যিই বড়ো করুণার যোগ্য। ভারতের প্রতিটি গ্রাম আদিযুগ থেকেই স্বনির্ভর এক-একটি খুদে গণতন্ত্র, মেটকাফের এই ভ্রান্ত প্রচার থেকেই এর উদ্ভব। ভারতের গ্রামের অনাহত অচলায়তনের আসাল কারণ তার মহান সম্প্রীতি বা স্বনির্ভর সমৃদ্ধি নয়, এর কারণ তার প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাতিসমাজের অনড় সীমানা। সেই কারণেই ভারতের গ্রামের নিচুজাতিসমাজের শ্রমের পিঠের ওপর দিয়ে যুগে যুগে এত ঝড় আর বিদ্রোহ-বিপ্লব বয়ে গেছে যার সুফল হিসাবে সুখ-স্বাধীনতা তারা কিছুই পায়নি। তাই সব কিছু বদলে গেলেও গ্রামসমাজ বদলায় না। গ্রামমাত্রই অজ্ঞতা, সঙ্কীর্ণতা, আঞ্চলিকতা আর সাম্প্রদায়িকতার আখড়া। আমি গভীরভাবে প্রীত যে সংবিধান খসড়া কমিটি স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক একক হিসাবে ভারতের গ্রামকে না বেছে ভারতের ব্যক্তিমানুষকে বেছেছে।”
১৯১৯ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম সমাজতত্ত্ব বিভাগ ছিল বম্বে ইউনিভার্সিটিতে। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী সমাজতত্ত্বচর্চাকে ‘বম্বে স্কুল অফ সোশিওলজি’ বলা হয়ে থাকে। তৎকালীন ঘটমান দলিত আন্দোলনের পীঠস্থান খোদ বম্বে শহরের এই জ্ঞানপীঠের দলিত সমাজকে আলোচনা করার এই অনীহা তাঁদের জাতীয়তাবাদী জ্ঞানচর্চাপদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। ডিপ্রেসড ক্লাস বা হরিজনদের নিয়ে বেশি গবেষণা বিভেদকামিতার নামান্তর। ‘বম্বে স্কুল অফ সোশিওলজি’-র দিকপাল হিসাবে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেওয়া হয় গোভিন্দ সদাশিব ঘুরয়ে (১৮৯৩ – ১৯৮৩) বা জি এস ঘুরয়েকে। তাঁর দুই ছাত্র— মাইসোর নরসিমহাচার শ্রীনিভাস (১৯১৬ – ১৯৯৯), এম এন শ্রীনিভাস আর আকষয় রমনলাল দেশাই (১৯১৫ – ১৯৯৪), এ আর দেশাই-এর মধ্যে প্রথমজনকে আমরা বর্ণবাদ-জাতিবাদের সংস্কৃতায়ন তত্ত্বের কল্যাণে বেশি জানি। আর সময়ক্রমের অনুসারে জি এস ঘুরয়ের ছিল সংস্কৃত আর ইন্ডোলজিতে নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং দেশাইয়ের ছিল মার্ক্সবাদী ইতিহাসচর্চায় ব্যুৎপত্তি। কিন্তু ভারততত্ত্ব চর্চায় বর্ণবাদ-জাতিবাদের কেন্দ্রিকতা তাঁদের তিনজনের কাজেই সমানভাবে উপেক্ষিত।
পি জি যোগদান্ড আর রমেশ কাম্বলের গবেষণাপত্রে আমরা পাই যে, আম্বেদকরের ১৯১৬ সালে লেখা ‘কাস্টস ইন ইন্ডিয়া: দেয়ার জেনেসিস, মেকানিজম এন্ড ডেভেলপমেন্ট’-এর ১৬ বছর পরে ঘুরয়ের ‘কাস্ট এন্ড রেস ইন ইন্ডিয়া’ (১৯৩২) প্রকাশিত হয়, তবুও এ বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে তিনিই অগ্রগণ্য বিবেচিত হন, আম্বেদকর নন। বহুপঠিত এবং বহু সংস্করণে প্রকাশিত এই বইয়ের ৪৭৬ পাতার মধ্যে মাত্র ৩০ পাতা (৩০৬-৩৩৬) ‘শিডিউল কাস্টস’ শিরোনামে জাতিবাদ-বর্ণবাদের আধুনিক সমস্যার প্রতি নিবেদিত যার সমাধান কোনোভাবেই সংরক্ষণ নয়, বরং বাকি সমাজের সাথে ক্রমআত্তীকরণ, এ ছাড়া বর্ণবাদ-জাতিবাদ সংক্রান্ত বাকি সব আলোচনা শুধু ঐতিহাসিক গবেষণার আগ্রহের বিষয়, সামাজিক সমস্যা নয়।
ফরাসি রাজনীতিবিজ্ঞানী ক্রিস্টফ জাফেরলটকে উদ্ধৃত করে যোগদান্ড ও কাম্বলে লেখেন, “আম্বেদকরের যুক্তি ছিল যে ব্রাহ্মণরা একা হাতে সমাজের ওপর জাতিব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়নি। সমাজের বাকিরা অন্তর্বিবাহে উৎসাহ দেখিয়ে ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এই বিষয়ে আম্বেদকার ফরাসি মনস্তত্ত্ববিদ গ্যাব্রিয়েল টার্ডের অনুসারী, যাঁর সামাজিক নকলনবিশির তত্ত্বমতে: (১) সমাজের নিচের ধাপেরাই ওপরের ধাপের নকল করে, উলটোটা কখনোই হয় না। (২) দুই ধাপের ফারাক যতটা বেশি, নকল করার তাগিদও ততটাই জোরালো। আম্বেদকরের মতে, ব্রাহ্মণরা যখন নিজেদের পুণ্যতার সর্বসেরা ধাপে প্রতিষ্ঠা করতে পারল, তাদের নকলনবিশির মাধ্যমে জাতিব্যবস্থা তত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল। অন্য জাতিরাও সতী, বাল্যবিবাহ, বিধবাদের পুনর্বিবাহ রদ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য প্রথা পালন করতে লাগল। এদিক থেকে দেখতে গেলে আম্বেদকর শ্রীনিবাসের বহুচর্চিত তত্ত্ব ‘সংস্কৃতায়নের’ পূর্বসূরী। কিন্তু দু-জনের তত্ত্বের মধ্যে মূল তফাত হল এই যে, আম্বেদকরের মতে এটি জাতি তৈরি হবার পদ্ধতি, আর শ্রীনিবাসের মতে এই পদ্ধতি এক নিচু জাতি থেকে উঁচু জাতিতে ওঠার।”
এম এন শ্রীনিবাসের বহুনন্দিত সংস্কৃতায়ন (স্যান্সক্রিটাইজেশন) আর পশ্চিমায়ন (ওয়েস্টার্নাইজেশন) তত্ত্ব কিন্তু ছোটো দুটি গ্রামের (কর্ণাটকের কোডাগাহাল্লি আর কুর্গের একটি গ্রাম) দুটি ছোটো সার্ভের ওপর ভিত্তি করে গঠিত। শ্রীনিবাসের মতে নিচু ধাপের জাতরা জাতে ওঠার জন্য উঁচু জাতের সংস্কৃতবহুল সংস্কৃতিকে নকল করতে থাকে (বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রথা আর জীবনের বিভিন্ন নিয়মকানুন) ও নিজেদের জাতিপরিচয় এক বা কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সফল হয়। এর পরের ধাপে তারা নিজেদের সংস্কৃতির পশ্চিমায়ন স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে করে, সামাজিক উন্নতির আরও উঁচু ধাপে ওঠার জন্য। এই তত্ত্বের মূল তথ্যগুলি সঠিক হলেও এই তত্ত্ব এমন একটি বাস্তবতার আভাস দেয়, যার আদতে খুব বেশি সার নেই। এই তত্ত্বচালিত হয়ে জাতে ওঠার সিঁড়িভাঙা অঙ্ক খুব সহজ মনে হয়। একটু চেষ্টা করলেই যেন জাতিব্যবস্থার অচলায়তন ভেঙে অনেকগুলো ধাপ টপকে উপরে চলে যাওয়া যায় এবং অনেকেই তা গিয়ে থাকে, এটি আদতেই সত্যি নয়। বড়োজোর সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে কয়েক প্রজন্মের মধ্যে জাতিব্যবস্থার এক-আধ ধাপ ওঠা যায়, যদি সার্বিক পরিস্থিতি সতত অনুকূলে থাকে। নিচু জাতে জন্মানোর ‘কলঙ্ক’ কাটিয়ে উঁচু জাতের সমান মান্যতা পাওয়া যে কত কঠিন, আম্বেদকরের নিজের জীবন তার সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ। জাতিব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো অন্যায়, মানসিক-সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক সব দিক দিয়েই একটি জাতকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটি ধাপে স্বেচ্ছাক্রমে আটকে রাখা এবং সেই আটকে রাখার পদ্ধতি যুগের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে বদলাতে থাকা। সেই অন্যায়কে বেমালুম হালকা করে দেয় এই তত্ত্ব, জাতের সিঁড়ি ভাঙার অতিসরলীকরণ দেখিয়ে।
আপাতদৃষ্টিতে পক্ষপাতহীন এই তত্ত্বগুলিও যে আদতে কীভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী, তার আরেকটি উদাহরণ হল আরেক প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বোসের (১৯০১-১৯৭২) ‘উপজাতি আত্তীকরণের হিন্দু পদ্ধতি’ তত্ত্ব, যার চুম্বক হল যে হিন্দুসমাজে উপজাতিদের স্থান পাওয়ার একটি পদ্ধতি হল সাগ্রহে নিজেদের হিন্দু ছোটোজাত বলে মেনে নেওয়া (হিন্দুসমাজের গড়ন বোঝার জন্য এই তত্ত্ব শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ন তত্ত্বের বাকি অর্ধেক হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে)। সমাজতাত্ত্বিক অভিজিৎ গুহ তাঁর একটি সাম্প্রতিক রচনায় দেখিয়েছেন এই তত্ত্ব কত স্বল্প এবং নড়বড়ে গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বোসের সমকালীন নৃতত্ত্ববিদ তারক চন্দ্র দাস এই একই বিষয়ে আরও অনেক গভীর ও নিপুণ গবেষণা করে উপজাতিদের ছোটো জাত হতে চাওয়ার আগ্রহকে ভিত্তিহীন বলে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাধারার পরিপন্থী (সবাই হিন্দু জাতিব্যবস্থার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে চায় না) বলে তারক চন্দ্র দাসের সেই গবেষণা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়ে এসেছে।
উপসংহার: আম্বেদকরবাদ সত্য কারণ ইহা বিজ্ঞান?
এই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ ভাগ পুরোটাই আরভিন্দ শর্মার ২০০৫ সালের একটি লেখা থেকে ধার করা। যেখানে তিনি বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন জাতিবাদ-বর্ণবাদ বিশ্লেষণের আদি স্তম্ভ ‘আর্যদের বহিরাগমন ও ভারতীয় অনার্যদের শূদ্রীকরণ’ তত্ত্বের প্রচলিত প্রতিপাদ্য, আম্বেদকরের বিশ্লেষণ ও খণ্ডন এবং আম্বেদকর-পরবর্তী গবেষণায় সেই প্রতিপাদ্যগুলির বর্তমান বিশ্লেষণ। এই কেস স্টাডি বেছে নেবার কারণ বহুবিধ। আম্বেদকরের কাছে এই প্রতিপাদ্যকে প্রশ্ন করার কারণ অনেক, কারণ যদি বর্ণবাদ-জাতিবাদ পাঁচ হাজার বছর আগের একটি বহিরাগত প্রজাতির দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া একটি প্রথা হয় তাহলে তা একটি অপরিবর্তনীয় প্রাগৈতিহাসিক আসবাবে পরিণত হয়ে যায় যা নিয়ে আমাদের কিছুই করার থাকে না। এই প্রথা যে আমাদের নিজেদের ইতিহাসের এবং নিজেদের দেশের অংশ, যুগে যুগে যা রূপবদল করেছে ধাপকাটা অসাম্যকে কায়েম রাখতে তা কোনোভাবেই উচ্চবর্ণ-উচ্চশ্রেণীর কুক্ষিগত বর্ণবাদী-জাতিবাদী জ্ঞানচর্চাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো যাবে না। কিন্তু আম্বেদকরের খণ্ডনপদ্ধতিতে লক্ষণীয় এই যে তিনি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখে নিজের প্রতিপাদ্যের প্রতি পক্ষপাত করেন না বরং সব ভারতজ্ঞানচর্চার ঘরানার সম্মতিপ্রাপ্ত এই প্রতিপাদ্যের কোন কোন অংশ সম্পূর্ণত ভুল আর কোন কোন ভাগ অংশত ভুল এবং সেগুলির সঠিক রূপ তখনও অব্দি প্রাপ্য প্রমাণের নিরিখে কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করায় বেশি মনোযোগী। এবং এই শিবিরভুক্তিঅনীহা আর পক্ষপাতশূন্যতার জন্য যে তাঁকেই উলটে পক্ষপাতী বলা হবে, তা জেনেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী পণ্ডিতদের গবেষণার মধ্যে যতটুকু খাঁটি মনে হয়েছে, নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন—
“আম্বেদকর এই প্রচলিত প্রতিপাদ্যকে সাত ভাগে ভাগ করেন: ১) বেদরচয়িতারা আর্য ছিল; ২) বহিরাগত আর্যরা ভারত দখল করেছিল; ৩) তারা ভারতের লোকদের দাস বা দস্যু বলত, যারা প্রজাতিগতভাবে আর্যদের থেকে ভিন্ন ছিল; ৪) আর্যরা ছিল শ্বেতকায় আর ভারতীয়রা কৃষ্ণকায়; ৫) আর্যরা দাস আর দস্যুদের জয় করে; ৬) দাস আর দস্যুদের পরাভূত করে আর্যরা তাদের নাম দিয়েছিল শূদ্র; ৭) আর্যরা দেহবর্ণবাদী ছিল তাই চতুর্বর্ণব্যবস্থা করে শ্বেতকায়দের আর কৃষ্ণকায়দের (দাস ও দস্যু) পাকাপাকিভাবে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করেছিল।
এই সাতটি ভাগের সত্যতা আণুবীক্ষণীকভাবে পরীক্ষা করার জন্য আম্বেদকর আটটি সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন গঠন করেন—১) দাসেরা আর দস্যুরা কি এক না আলাদা? ২) তারা আর শূদ্ররা কি এক? ৩) দাস বা দস্যু কি প্রজাতিগত বিভাজন? 8) এরা যে ভারতের মূলনিবাসী তার কী প্রমাণ আছে? ৫) ভারতের মূলনিবাসীরা কি অসভ্য বর্বর ছিল? ৬) শূদ্ররা কি অনার্য? ৭) দাস কি শুধু একটি নাম না কি ঋগ্বেদে তাদের দাসবৃত্তি করার কোনো কথা আছে? ৮) দাসেরাই কি শূদ্র?
আম্বেদকরের উত্তর—১) দাসেরা আর দস্যুরা কি এক না আলাদা? কিছু কিছু জায়গায় তাদের সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হলেও, অনেক জায়গায় তাদের আলাদা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন বেদে দাসেদের কথা আলাদা করে ৫৪ জায়গায় আছে আর দস্যুদের কথা ৭৮ বার। তারা একই হলে এতবার আলাদা আলাদা করে তাদের কথা থাকত না। খুব সম্ভবত তারা তাই আলাদা। আম্বেদকরের এই প্রতিপাদ্য পরবর্তী গবেষণা থেকে প্রভূত সমর্থন পেয়েছে।
২) তারা আর শূদ্ররা কি এক? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে জিজ্ঞাসা করতে হবে শূদ্র কারা? আম্বেদকরের মতে এই প্রশ্নের একটি শাব্দিক উত্তর আছে আর একটি ঐতিহাসিক। বেদান্তসূত্র আর বিষ্ণুপুরাণ মতে ‘শূদ্র’ শব্দ ‘শুচ’ ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ শোক করা, তাই ‘শূদ্র’ শব্দের অর্থ ‘শোকার্ত মানুষ’। ঐতিহাসিক উত্তর হল শূদ্ররা একটি উপজাতি। দুটি উত্তরেরই যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যা অখণ্ডনীয়।
৩) দাস বা দস্যু কি প্রজাতিগত বিভাজন? মহাভারতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে আম্বেদকর দেখান যে দস্যুরা সব বর্ণে আর সব আশ্রমেই ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে দস্যু শব্দের অর্থ হল যারা আর্যদের ধর্ম পালন করে না। (এখানে আম্বেদকর এও বলতে পারতেন যে চার বর্ণের যে-কোনো বর্ণই দাসবৃত্ত করতে পারে। তাই দাস মানে যে দাসবৃত্তি করে।) ঐতিহাসিকভাবে আম্বেদকার ‘দাস’ শব্দকে জেন্দ আবেস্তার হিংস্র ড্রাগন আঝিদাহকের আরেকটি নাম হিসাবে দেখান আর ‘দস্যু’ শব্দকে ইন্দো-ইরানীয়দের প্রতি ইন্দো-আর্যদের একটি গালি হিসাবে উল্লেখ করেন। যদিও আম্বেদকর জেন্দ আবেস্তার ওই ‘দাস’-সংক্রান্ত প্রমাণের সূত্রটির সংখ্যা হারিয়ে ফেলেন তাই তাঁকে ঋগ্বেদের থেকে প্রমাণ দিতে হয়। কিন্তু জর্জ থম্পসন পরে ১০৯এন৭ সংখ্যক ওই জেন্দ আবেস্তার সূত্রটির উল্লেখ করে আম্বেদকরকে সঠিক প্রমাণ করেন।
8) এরা যে ভারতের মূলনিবাসী তার কি প্রমাণ আছে? দাস আর দস্যুরা যদি ইন্দো-ইরানীয়ান হয়ে থাকে তাহলে ইন্দো-আর্যানদের মতোই তারা বহিরাগত ছিল।
৫) ভারতের মূলনিবাসীরা কি অসভ্য বর্বর ছিল? ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে তাঁরা শহরে থাকতেন, ধনসঞ্চয় করতেন, সম্পত্তি আর রত্নভাণ্ডারে রাখতেন, দুর্গ দখল করতেন—অতএব অসভ্য বর্বর তো তাঁদের কোনো মতেই বলা যায় না। আম্বেদকর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করেন যা আমাদের প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুবই জরুরি। হরপ্পায় ঘোড়ার কোনো অস্তিত্ব না পাওয়া গেলেও দস্যুদের কাছে আর্যদের মতোই রথ, ঘোড়া আর একইরকম অস্ত্র ছিল।
৬) শূদ্ররা কি অনার্য? আম্বেদকরের উত্তর শুরু হয় পি ভি কানের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে, যার মূল বক্তব্য হল যে যাকে আমরা আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখি তা আসলে আর্যদের দুটি গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্ব—বৈদিক আর অবৈদিক। কানের এই কথা মেনে নিলে দাস-দস্যু-শূদ্র সংক্রান্ত তর্ক এক নতুন মাত্রা পায়। কিন্তু আম্বেদকর বলেন যে কানের কথা বড়োজোর আংশিকভাবে সত্য। তা পুরোপুরি সত্য হবার পথে বাধা এই প্রমাণগুলি—(১) অনেক শাস্ত্রেই শূদ্রসহ চার বর্ণের উল্লেখ আছে—বলি সংক্রান্ত প্রসঙ্গে; (২) ছান্দোগ্য উপনিষদ বলে বেদচর্চায় শূদ্রদের অধিকার আছে; (৩) ভারদ্বাজ শ্রৌত সূত্র আর কাত্যায়ন শ্রৌত সূত্রে শূদ্রদের বৈদিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের উল্লেখ আছে; (৪) মীমাংসাসূত্র বলে বদ্রিরও এই মত; (৫) পুরাণে শূদ্রের বলিদানের অধিকারের ভূরিভূরি উদাহরণ আছে। (৬) মনুস্মৃতিতে জাত্যাপকর্ষ দ্বারা ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বে অবতরণ বা জাত্যোৎকর্ষ দ্বারা শূদ্রের ব্রাহ্মণত্বে উত্তরণের উল্লেখ আছে (মূলত কয়েক প্রজন্ম ধরে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ফল)। (৭) অর্থশাস্ত্র স্পষ্টভাবে বলে শূদ্ররা আর্য। তাই পি ভি কানের মতে দাস ও দস্যুরা অবৈদিক আর্য, অনার্য না, এর মধ্যে আংশিক সত্যতা আছে।
৭) দাস কি শুধু একটি নাম নাকি ঋগ্বেদে তাদের দাসবৃত্তি করার কোনো কথা আছে? দাসবৃত্তিকারী অর্থে দাস শব্দের উল্লেখ ঋগ্বেদে মাত্র পাঁচ বার রয়েছে। দাস শব্দের অর্থ পরবর্তীকালে দাসবৃত্তিকারী হয়েছে বলেই আমরা তার অন্যান্য অর্থগুলিকে অবহেলা করবো এটা মোটেই কোনো কাজের কথা নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কোনো কোনো ভাষায় ‘আর্য’ শব্দের অর্থ দাসবৃত্তিকারী। ইংরাজি শব্দ স্লেভ-এর অর্থ পরে দাসবৃত্তিকারী হলেও এর উৎস ‘স্লাভ’ অর্থাৎ যুদ্ধবন্দি স্লাভিক। তেমনি ফিনিশ ভাষায় দাসবৃত্তিকারী অর্থে ‘অরজা’ শব্দ ‘আর্যান’ বা যুদ্ধবন্দি আর্য থেকে এসেছে। তেমনই স্বামী শব্দের অর্থ সংস্কৃতে প্রভু কিন্তু সাউথ আফ্রিকায় ভারতীয় চুক্তিদাসদের ‘স্যামিস’ বলা হয় যা স্বামী শব্দের অপভ্রংশ।
8) দাসেরাই কি শূদ্র?
বৈদিক প্রমাণের হিসাবে শূদ্রদের মোটেই শোকার্ত বা প্রান্তিক বলে মনে হয় না। এদিকে আর্যরা যে আর্য যুদ্ধবন্দিদেরও দাসবৃত্তির কাজে লাগাত তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। তাই পরাজিত দাস আর দস্যুদের শূদ্র করে দাবিয়ে দেওয়া হল, ব্যাপারটা এতটাও সরল না। ব্রাহ্মণে রাজার অভিষেকের জন্য জরুরি রত্নীদের কথা আছে আর তাদের মধ্যে একজনকে শূদ্র হতেই হবে, সেটিরও উল্লেখ আছে। এর সমর্থন নীলকন্ঠ লিখিত নীতিময়ূখেও পাওয়া যায়। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেককারীদের মধ্যে শূদ্র ছিলেন। শান্তিপর্বে উল্লেখ আছে যুধিষ্ঠিরের মন্ত্রীসভায় তিনজন ব্রাহ্মণ আর চারজন শূদ্র ছিলেন। মৈত্রায়ণী সংহিতা আর পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে আছে যে ধনী শূদ্রেরা জনপদ আর পুরসভায় বিভিন্ন উচ্চ রাজনৈতিক পদে থাকতেন এবং ব্রাহ্মণদের থেকেও সম্মান পেতেন। তা ছাড়াও আম্বেদকর আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, ঋগ্বেদে ‘শূদ্র’ শব্দটি আছে ১ বার ‘দাস’ ৫৪ বার আর ‘দস্যু’ ৭৮ বার। এই শব্দগুলির বৈদিক মানে অন্যরকম ছিল। কিন্তু ‘দাস’ আর ‘দস্যু’ শব্দের উল্লেখ পরে খুব কম পাওয়া যায়। আর ‘শূদ্র’ শব্দের উল্লেখ বাড়তে থেকে। এর থেকে মনে করা যায় যে দাস আর দস্যুরা আর্যদের সাথে মিশে যায় কিন্তু শূদ্ররা মেশে না। যদিও আম্বেদকরের এই সিদ্ধান্ত খুব জোরালো না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পেছনের যুক্তি বহুলসমর্থিত। ম্যাক্সমুলারের রচনা থেকে আম্বেদকার উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে সিদ্ধান্ত গণপতিতে শূদ্রের উপনয়নের বিধান আছে।
এবার ফিরে যাওয়া যাক প্রতিপাদ্য ৭)-এ: আর্যরা দেহবর্ণবাদী ছিল তাই চতুর্বর্ণব্যবস্থা করে শ্বেতকায়দের আর কৃষ্ণকায়দের (দাস ও দস্যু) পাকাপাকিভাবে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করেছিল। আম্বেদকর সংক্ষেপে এবং বিস্তারে, দু-ভাবে এর খণ্ডন করেন। তিনি বলেন যে দেহবর্ণের বিচারে চারভাগ করতে গেলে চাররকম দেহবর্ণ লাগে। কিন্ত যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নিই আর্য ব্রাহ্মণরা ফর্সা আর অনার্য শুদ্রেরা কালো, তাহলেও গাত্রবর্ণ দু-রকমই পাওয়া যাচ্ছে। পি ভি কানের লেখা থেকেও আম্বেদকর দেখান যে দাস আর শূদ্রদের প্রসঙ্গেই শুরুর দিকে বর্ণ শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়দের প্রসঙ্গে বর্ণ কথাটির উল্লেখ নেই। এমনকি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্রের উল্লেখ থাকলেও বর্ণের উল্লেখ নেই। অন্য পন্ডিতেরা বৈদিক যজ্ঞে চার দিকে চার রঙের পতাকা—সাদা, কালো, লাল, হলুদের সাথে সেই যজ্ঞবেদির কোন দিকে কোন বর্ণভুক্ত মানুষ বসবে, তার যোগাযোগ দেখাতে চেয়েছেন। বর্ণ শব্দের অনেকগুলি অর্থের মধ্যে একটি অর্থ রং তাই বর্ণ মানেই গাত্রবর্ণ তা ধরে নেওয়ার পেছনে বিশেষ যুক্তি নেই।
আম্বেদকরের মতে বহিরাগত আর্য তত্ত্ব যুক্তির ধোপে না টিকলেও ব্রাহ্মণ আর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রজাতিবাদী (রেসিস্ট) বিশ্বাসের ওপর টিকে আছে, যেখানে গৌরাঙ্গ জাতি অধিক উন্নত এবং শক্তিশালী এবং তারা ঐতিহাসিকভাবে অন্য সব গাত্র বর্ণের মানুষের ওপর প্রভুত্ব করার অধিকারী।
সবশেষে যাচিয়ে দেখা যাক আম্বেদকরের গবেষণা পরবর্তী গবেষকদের হিসাবে কতদূর টেকসই, এটিকে পূর্বোল্লিখিত সাত ভাগে বিচার করে দেখা যাক : ১) আম্বেদকরের হিসাব অনুযায়ী বেদরচয়িতা আর্যরা একটি ভাষাগোষ্ঠী, প্রজাতি (রেস) নয়, এটাই আধুনিক ভারততত্ত্বের অভিমত। আম্বেদকরের গবেষণার এই দূরদৃষ্টি অসাধারণ। ২) আম্বেদকরের মতে আর্যরা যে ভারতে একেবারেই বহিরাগত নন এই তত্ত্ব ঠিক ধোপে টেকে না। কিন্তু ভারতের ‘বাহির’-এর সংজ্ঞাকে বর্তমান ভারতের সীমা দিয়ে বিচার করলে হবে না। যেমন মাইকেল উইটজেলের মতে বর্তমান পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে এসে থাকলেও সে-যুগে সেটাকে ভারতের বাইরে না ভেতরে ধরা হবে তা তর্কসাপেক্ষ। ৩) দাস, দস্যু ও আর্যদের বিভেদ ধর্মচর্চাগত, প্রজাতিগত নয়, আম্বেদকরের এই বিশ্লেষণকে এখনকার পণ্ডিতেরা আংশিক সত্য বলে মানেন, তাঁদের মতে এই বিভেদ খানিকটা হলেও প্রজাতিগত। ৪) দাস, দস্যু, আর্য, শূদ্রদের গাত্রবর্ণ সব আলাদা, এই অতিসরলীকৃত তত্ত্বকে আম্বেদকরের মতোই এখনকার পণ্ডিতেরাও অগ্রাহ্য করেন। ৫ ) এখনকার গবেষণা আর্যদের এলাম-দেখলাম-জয় করলাম তত্ত্বকে মানে না। বহু ধারায় আর্যরা এসেছিল এবং নানাভাবে যুদ্ধ, পরাজয়, বৈবাহিক মিশ্রণ এবং অবদমন ধাপে ধাপে ঘটেছিল, এই তত্ত্বই এখন মান্যতা পায়। ৬) ও ৭) বর্ণ মানে যে গাত্রবর্ণ নয়, শ্রেণী বা গোষ্ঠী, আম্বেদকরের এই অভিমত এফ বি জে কুইপার সহ অনেক পণ্ডিতের সমর্থন পেয়েছে।
অর্থাৎ আম্বেদকরের বিশ্লেষণ যা বর্ণবাদ-জাতিবাদকে একটি প্রজাতিবাদী ব্যবস্থা হিসাবে না দেখে সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক এক ব্যবস্থা হিসাবে দেখে, সে-বিষয়ে আম্বেদকরের অবদান স্বীকৃত না হলেও, তা অন্যান্য বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিবিধ গবেষণার মাধ্যমে এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ।
আরও পড়তে চাইলে:
আম্বেদকরের রচনা বাংলায় -
https://velivada.com/2017/04/22/pdf-in-bengali-dr-b-r-ambedkars-writings-and-speeches/
Vivek Kumar, Situating Dalits in Indian Sociology, Sociological Bulletin, September - December 2005, Vol. 54, No. 3, Special Issue on South Asia: THE STATE OF SOCIOLOGY: ISSUES OF RELEVANCE AND RIGOUR (September - December 2005), pp. 514-532
Y S Alone, Historicism: Confrontation and Enquiries, in Ambedkar in Retrospect: Essys on Economics, Politics, Society, Edited by Sukhdeo Thorat and Aryama, Rawat Publications, 2007, pp. 261-291
B R Ambedkar, India and Communism (Introduction by Anand Teltumbde), LeftWord Books, New Delhi, 2017
Sharad Patil, Should ‘Class’ Be the Basis for Recognising Backwardness? Economic and Political Weekly, Dec. 15, 1990, Vol. 25, No. 50 (Dec. 15, 1990), pp. 2733-2735+2737-2741+2743-2744
Sujata Patel, The nationalist-indigenous and colonial modernity: an assessment of two
sociologists in India, The Journal of Chinese Sociology, December 2021
P.G. Jogdand and Ramesh Kamble, The Sociological Traditions and Their Margins: The Bombay School of Sociology and Dalits, Sociological Bulletin, May-August 2013, Vol. 62, No. 2, Special Issue on The Bombay School of Sociology: The Stalwarts and Their Legacies (May-August 2013), pp. 324-345
Abhijit Guha, Scrutinising the Hindu Method of tribal absorption. Economic & Political Weekly 53, no. 17 (2018): 105
Arvind Sharma, Dr. B. R. Ambedkar on the Aryan Invasion and the Emergence of the Caste System in India, Journal of the American Academy of Religion, Sep., 2005, Vol. 73, No. 3 (Sep., 2005), pp. 843-870
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।