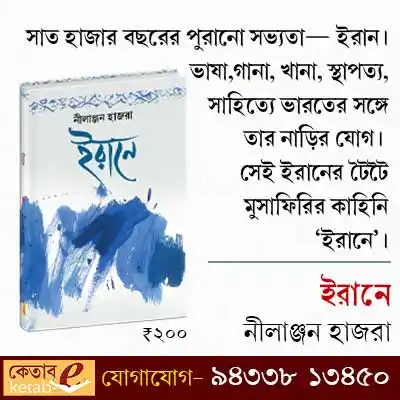উত্তর-পূর্ব ভারতের ছবির মত সুন্দর এক পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয়। মেঘ, বৃষ্টি আর ঝর্ণা রাজ্য— মেঘালয় ভ্রমণের রঙিন অভিজ্ঞতা উঠে এল তন্ময় বিশ্বাসের কলমে। আজ প্রথম পর্ব।
ব্যাম্বুট্রেক
মেঘালয়ের মতো এত সুপারি গাছ আমি অন্য কোনো পাহাড়ে দেখিনি। খুব ঘনভাবে না থাকলেও দেখতে ভারি ভালো লাগে। ওরাই এখানে সবথেকে লম্বা। পাইনগাছগুলো ওদের সাথে না পেরে মনখারাপ করে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তাদের শরীর ছুঁয়ে হাওয়া বয়ে গেলে বাঁশির শব্দ ওঠে, পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এলে মনে হয় মাটিতে কত না সোনার মোহর ছড়িয়ে আছে। আর সাথে সেই গুবরে পোকার গান। অতক্ষণ ধরে কানে বাজে, অথচ একটুও বিরক্ত লাগে না!
আরেকটা যে জিনিস প্রায় রক্তের সাথে মিশে গেছিল সেটা হল বাঁশের নানারকম সব গন্ধ। শুকনো, কাঁচা, আবার আধপাকা সবার আলাদা আলাদা রকম গন্ধ থাকে। শুকনো বাঁশপাতার ওপর দিয়ে কড়মড় করে হেঁটে গেলে পুরোনো বইয়ের মতো গন্ধে মন প্রাণ ভরে যায় একেবারে!
ব্যাম্বুট্রেকে যে গেলাম, তার জন্য মোটেই তৈরি ছিলাম না আমি। ওরাই কোন রিলে না ভ্লগে দেখে এসেছিল। সন্তোষকাকুর সাথে যখন কথা বলছি, তখন সে কী লাফালাফি। আমার আর কী, আমি নতুন জায়গা দেখতে পেলেই তো আর কিছু চাই না। কিন্তু পরে দেখলাম ট্রেকের রাস্তাটা সত্যিই খুব সুন্দর। পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটার থেকে বাঁশের মাচার ওপর দিয়ে চলা ঢের বেশি আরামের। ওরা যে কেন এত ভয় পাচ্ছিল!
অবশ্য কয়েক জায়গার বাঁশ বেশ পুরোনো। উঠলেই বিচ্ছিরি সব ক্যাঁচরম্যাঁচর শব্দ হয়, ভেঙে গেলে কত যে নীচে পড়ব তার হিসাব নেই। তবে পাহাড়ে চড়ার এই বুদ্ধিটা বেশ মনে ধরেছিল। পাহাড় কেটে নষ্টও হল না, কোনো গাছ বাদ পড়ল না, অথচ কেমন সুন্দর রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। আমরা বাংলায় যেটাকে বাঁশের মাচা বলি? এখানে সেটাই একটার পর একটা বাঁশ বেঁধে, তাই দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে। নীচে বাঁশ বা কোনো কোনো জায়গায় লোহার রডের সাপোর্ট। পাহাড়ের গায়ে ফুটো করে সেই সাপোর্টগুলো সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে ফেলা হয়েছে। এভাবেই পাহাড়ের গায়ে গায়ে পাক দিয়ে রাস্তা উঠেছে। যেখানগুলো খুব উঁচু, সেই ঢালে যাতে পা গড়িয়ে না যায়, তার জন্য মই এর মতো আড়াআড়ি সাপোর্ট আছে মাঝে মাঝে। সব মিলিয়ে রাস্তা মোটেই সোজা নয়। দু-পাশে রেলিং আছে বটে। কিন্তু সে আমার প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি, দাঁড়িয়ে থাকলে কোনোভাবেই হাত পৌঁছায় না।
ওঠার সময় আমরা প্রায় একাই উঠেছিলাম। কিন্তু ফেরার সময় যত জনকে ট্রেকিং পোল নিয়ে উঠতে দেখলাম, সবার সাথে প্রথমে হেসে কথা বলি, তারপর ইংরেজি বুঝছে দেখলে জোড়ে জোড়ে মাথা নেড়ে বারণ করি। দুটো বাঁশের ফাঁকে বেকায়দায় পোল আটকে গেলে ও জিনিস আর ফেরত পেতে হবে না। তবে সব জায়গায় মোটেই মাচা নেই, কিছু রাস্তা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে পাথর দিয়ে তৈরি। আবার পাহাড় ফুরিয়ে গেলে দারুণ সব লোহার তৈরি দোলনা ব্রিজ। যদিও সবগুলোতেই বেশ বাজেভাবে মরচে পড়ে গেছে। তবু চলার সময় ব্রিজটা দুলত বলে আমি আরও এঁকেবেকে চলতাম। তাই নিয়ে অনুর সে কী চিৎকার।
ভয় বোধহয় একমাত্র সোমেরই লাগেনি। আমি নাহয় দারুণ বীরপুরুষ। কিন্তু সোমের সেটাই ছিল জীবনের প্রথম ট্রেক। তবু এনার্জি দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমরা ইচ্ছা করেই গাইড নিইনি, সেখানে ওই পারলে আমাদের টানতে টানতে নিয়ে যায়।
আর রাজের একটা বড়ো গুণ হল— জল, উঁচু জায়গা, মাকড়সা প্রায় সব কিছুতেই ভয় পায়। কিন্তু মেল ইগোর জন্য বাঁকা হাসি দিয়ে সেগুলো ঢেকেঢুকে রাখতে পারে।
মেঘালয় জায়গাটা মোটেই নদীমাতৃক নয়, এটা নদীরই দেশ। প্রতিটা নদীই চলতে চলতে দুর্দান্ত সব বাঁক নিয়েছে, আর তার কোলের কাছটাতে একটা করে টুরিস্ট স্পট বানিয়ে মানুষ টিকিট হাতে বসে পড়েছে। এই ট্রেকের একদম শুরুর দিকে যে নদীটা ছিল, তার নাম একদমই ভুলে গেছি। পাথর, বড়ো বড়ো বোল্ডার, আর গাছের ছায়া বুকে নিয়ে বয়ে চলা তিরতিরে জলধারা। খুব একটা স্রোত নেই। এর আগে একটা গাছের ওপর বাঁশ বেঁধে ব্যালকনি মতো করা ছিল। কী গাছ কে জানে! খাদের দিকে ঝুঁকে কিছু একটা দেখতে গিয়ে, সে ব্যাটা ওভাবেই থেকে গেছে। শেকড় সব ইয়া মোটা মোটা। তার ডালের যে ‘ভি’ মতো জায়গা, সেখানে আবার বাঁশের মাচা বানিয়ে ব্যালকনি মতো করা আছে। মই দিয়ে উঠে দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসা যায়। একলা থাকলে, ওখানেই খানিক উদাস হয়ে বসে থাকা যেত। কিন্তু এখানে তো আর একা হওয়ার উপায় নেই, সোমের একগাদা ছবি তুলে দিতে হল। রাজ অবশ্য আমি উঠতেই তাড়াতাড়ি করে নেমে পড়েছিল। আমি একটু ভারী মানুষ কিনা।
ট্রেক যখন একদম শেষের দিকে, তখন দারুণ একটা জায়গায় পৌঁছলাম আমরা। সে এতই সুন্দর যে সবাই ভেবেছিলাম এটাই বুঝি লাস্ট পয়েন্ট। জায়গাটা কেমন বলি একটু। ওপরে ওঠার যে রাস্তা, তার বাঁ-দিকে বিশাল বড়ো একটা পাথর ব্যালকনির মতো ঝুলে আছে খাদের ওপরে। বিছানার ওপর একখানা গীতবিতান উপুড় করে রাখলে যেমন দেখতে হয়? তেমনি। শুধু এখানে প্রচ্ছদ আর ব্যাক কভারের ঢাল অনেকটা। অসাবধান হলেই মানুষ গড়িয়ে পড়ে যাবে। আর তেমনি হু-হু হাওয়া। বহু নীচের নদী-ঝরনা দূরত্বের জন্য কেমন ধোঁয়াটে হয়ে পড়েছে। কতক্ষণ যে আমরা ওখানে বসে থেকে শুধু বাতাসের শব্দ শুনলাম!
একটা বিড়াল আমার কোলের মধ্যে আরাম পেয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর যখন আবার হাঁটা শুরু করলাম, সে খানিক্ষণ আমার কাঁধে উঠে বসে রইল। তারপর আমাদের পাহাড় চড়বার ছিরি দেখে হতাশ হয়ে নেমে গিয়ে ছুটতে লাগল আগে আগে। এর পরের রাস্তাটুকু বোধহয় বিড়ালের হাঁটার জন্যই তৈরি। নইলে এমন সরু রাস্তায় মানুষের পা আঁটে নাকি! আর তেমনি নীচু। অমন ধরধর করে নেমে খানিকটা আড়াল সরে যেতেই আমরা সেই কালো রাজার পাহাড়টা দেখতে পেলাম।
এর আলাদা করে কোনো গল্প নেই। সন্তোষকাকু বলেছিল, আমরা যার মাথায় উঠব সে নাকি সব পাহাড়ের মাঝে একলা রাজার মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। এখন দেখলাম সত্যিই তাই। দাবার বোর্ডের কালো রাজার মতোই ফিগার। শুধু মাথাটা কেক কাটার ছুরির মতো ছুঁচলো। এ পাহাড় থেকে রাজার কোলে গিয়ে ওঠার সিঁড়িটা দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটার সাহস আর হল না আমাদের। হামাগুড়ি দিয়ে উঠলেও বার বার নীচের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে আর বাঁই বাঁই করে মাথা ঘোরে। অর্ধেকটা বোধহয় উঠেছি, তখন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। দেখি কী, একটা সাদা প্রজাপতি তার ডানায় প্রচুর কালো কালো মতো শিরা। সে খাদের ওপর দিয়ে প্রায় গ্লাইড করে উড়ে যাচ্ছে অন্যদিকে! ডানা একটুও নড়ছে না। কিন্তু দিক বদল করার জন্য সে যে শরীরে এদিক-ওদিক খানিক মোচড় দিচ্ছে, সে দিব্যি বোঝা যাচ্ছে। এমন করে চিল ওড়ে, পাহাড়ের কয়েক জায়গায় কাক-পায়রাদেরও এরকম হাওয়ায় ভর করে ভাসতে দেখেছি। কিন্তু প্রজাপতিরাও যে এই কায়দাটা শিখে নিতে পারে সেটা কোনোদিন মাথায় আসেনি। ওই দিনের ট্রেকে এর চেয়ে ভালো জিনিস আমি আর কিছু দেখিনি।
তবু বাকিটা বলি। তখন ছুরির উপমা কিন্তু জোর করে দিইনি। পাহাড়ের মাথাটা একদমই তাই। কোনোরকমে থেবড়ে বসা যায়। দাঁড়াতে হলে বাঁশের রেলিং না ধরে উপায় নেই। আমরা উঠেছিলাম তখন ফাঁকা ছিল জায়গাটা।
তারপর দু-জন মাতাল ডাক্তার এসে জুটল। দেখলাম ওরা সাথে করে অনুকেও নিয়ে এসেছে। অনু ভয়ের চোটে আমাদের সাথে আসেনি। তারপর এরা গিয়ে বলাতে, একটা ছেলের চোখদুটো নাকি ওর খুব পছন্দ হয়ে গেছিল। তাই সেভাবে আর না বলতে পারেনি। পৃথিবীর কত জায়গায় যে ভগাদা ফাঁদ পেতে রেখেছে কে জানে!
তবে ওরা আসার পর আমার আর থাকতে ইচ্ছে হল না। এক তো স্পিকারে প্রচণ্ড জোরে গান চালিয়েছে। আর পরক্ষণেই ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ল বিয়ারের দুটো ঝকঝকে ক্যান। আমি ভালোমতোই নাস্তিক। তবু মনে হয় এইসব মানুষকে প্রকৃতি নিজের হাতেই শাস্তি দেয়। তার স্নায়ুতন্ত্র আমাদের থেকে অনেক বেশি জটিল। তার রসিকতা কল্পনার থেকেও ভয়ানক।
(পরে শুনেছিলাম এটা নাকি ভারতবর্ষের ভয়ানকতম ট্রেকগুলোর মধ্যে একটা। সেখানে আমি কিনা এমন দু-জনকে নিয়ে গেছিলাম যারা এর আগে কোনোদিন ট্রেক করেনি। ভাগ্যিস পরে শুনেছিলাম, নইলে আমার ওখানেই হয়ে যেত।)
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
ডাউকি লেক ও মাউলিং গ্রাম
যেদিন আমরা ডাউকি লেক দেখতে গেলাম, সেদিন আমাদের সে কী ফুলবাবু গোছের মেজাজ। আজ ট্রেক নেই, হাঁটাহাঁটির ব্যাপার নেই। গাড়ি থেকে নামব, জায়গা দেখব, আবার উঠে এসে গদিতে পাছা ঠেকাব। অন্যদের এরকম ভাজুং ভুজুং বুঝিয়েই এনেছিলাম। কিন্তু পাহাড়ে না চাইলেও অনেকটা করে হাঁটা হয়ে যায়।
একবার একটা গ্রাম থেকে খানিকটা উঠে দেখি, বাঁ-দিকে অ্যারো দিয়ে লেখা লিভিং রুট ব্রিজ। আমরা মহানন্দে ডানদিকে উঠে চললাম। একটা লোকও এদিকে আসে না। তেমনিভাবে দেখার কিছু নেইও। তবু তার মধ্যেই ছোটো একটা সাপের খোলস কুড়িয়ে পেলাম, তার গা তখনও খানিক ভেজা ভেজা। আরেকটু সুন্দর হলে ঠিক কুড়িয়ে আনতাম।
তারপর আরও কয়েক পা গেলেই একটা খুদে নদীর বুকের ওপর গিয়ে দাঁড়ানো যায়। একবিন্দুও জল নেই। চারদিকে ঝিম ধরা ঘন জঙ্গল। আর সে কী ঝিঁঝির শব্দ। আমাদের ওখানে এমন পোকা মোটেই পাওয়া যায় না। সৈকতদার একটা উপন্যাসে এদের কথা পড়েছিলাম। হুট করে শুনলে নাকি মনে হয় কেউ পাতালের ঘরে বসে অনন্তকাল ধরে মোহর গুনছে। এখন শুনে বুঝলাম সৈকতদা খানিকটা মায়াকাজল লাগিয়ে নিয়ে লিখেছিল। নইলে আওয়াজটা আসলে খুচরো পয়সার মতো। পকেট ভারী করে এক-দু-টাকার কয়েন নিয়ে দৌড়ালে এরকম শব্দ হয়। তবে মোটেই তেমন এলোমেলো নয়। এই শব্দের ওঠা-নামার খুব কড়া একটা নিয়ম আছে। কোনোমতেই তার বাইরে যায় না। বরং অনেক্ষণ বসে শুনতে পারলে, জঙ্গলের অনেকখানি মনের ভেতর ঢুকে যায়। তখন বুক ভরে নিশ্বাস নিতে কী যে আরাম লাগে!
তারপর ওখান থেকে নেমে সেই লিভিং রুট ব্রিজেও গেছিলাম বটে। সেই আমাদের প্রথম অমন জিনিস দেখা। নীচের জল শ্যাওলা পড়ে ঘন সবুজ। একদম পা ডোবাতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ওই জলেই নিশ্চিন্তে কাপড় কাচছেন কয়েকজন ভদ্রমহিলা। নীচের রিভার বেডে যতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, ততক্ষণ কতজনের যে ছবি তুলে দিতে হল!
এর আগে যখন ডাউকিতে নৌক চেপেছিলাম, তখন ওখান থেকে বাংলাদেশের অনেকখানি অংশ দেখা যাচ্ছিল। সে এক ভারী সুন্দর জায়গা। এমনি এমনি কী আর এত নাম। জলের প্রায় কোনো রংই নেই। নৌকা চললে মনে হয় বাতাসে ভেসে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু ময়লা পড়ে নেই। এসব নৌকায় তিন জনের বেশি লোক নেয় না। তাই আমাদের দুটো নৌকা নিতে হয়েছিল।
আমাদের যে মাঝিভাই, তার বয়স কম হলেও বেজায় গম্ভীর। যদিও টুকটাক গল্প বলছিল। বাংলাদেশের দিক দিয়ে যখন যাচ্ছি, তখন ওপারের একজন ফটোগ্রাফার কত করে রিকোয়েস্ট করল ছবি তুলে দেওয়ার জন্য। মাঝি প্রায় দূর দূর করেই তাড়িয়ে দিল তাদের। ছবি তুললেও তার প্রিন্টটা কী করে দিত কে জানে!
লেকটা কিন্তু আসলে বেশ বড়ো। কিছু জায়গায় তো গভীরও না তেমন। এক জায়গায় দেখলাম দু-জন কাপলা-কাপলি নৌকার মাঝখানে ময়াল সাপের মতো একে অপরকে পেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাদের মাঝি নৌকাটাকে আমাদের চোখের সামনেই নিঁখুত ৩৬০ ডিগ্রি কোনে বাঁই বাঁই করে দু-বার ঘুরিয়ে ফেলল। অথচ নৌকা তার কেন্দ্র থেকে একফোঁটাও সরল না। আমি আর রাজ আমাদের মাঝিভাইয়ের দিকে তাকাতেই হুস করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আজ আমাদের বিয়ে হয়নি বলে এত অবহেলা!
লেকের অন্যদিকে আবার একটা ছোটো মতো দ্বীপ। সেখানে একফোঁটাও সমতল জায়গা নেই। সবই ছোটো ছোটো গোল গোল পাথর। কত যে ব্যালেন্স করে হাঁটতে হয়! তার ওপরই আবার গুচ্ছের খাবারের দোকান, খাসি মহিলারা আনারস কেটে, তার ওপর দিয়ে হাত পা নেড়ে সারাদিন ধরে পোকা তাড়াচ্ছেন।
দ্বীপের অন্য প্রান্তে জলের ভীষণ গর্জন। পা ডুবিয়ে রাখলে, সেকেন্ডের মধ্যে পরিস্কার হয়ে যায় সব। তাও ময়লা যা বাকি ছিল, পরে ডাবল ডেকার ব্রিজে যাওয়ার সময় খুদে খুদে মাছেরা এসে সব চেটেপুটে খেয়ে গেছিল।
দ্বীপে অবশ্য আমাদের বেশিক্ষণ থাকা হল না। দুটো নৌকার মাঝিই সে কী বিরক্ত! ফেরার সময় দেখি জলের ধারে কোন একটা পাহাড় বিচ্ছিরিভাবে কাটা হচ্ছে। অনেক উঁচুতে একটা ক্যাট কোম্পানির ক্রেন পাথরে একটু করে ধাক্কা মারছে, আর ইয়া বড়ো বড়ো সব বোল্ডার গড়াতে গড়াতে এসে পড়ছে জলের ওপর। তার জন্য সে কী ঢেউ। আমাদের নৌকা ভীষণভাবে দুলে উঠছিল। তবু আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম, এর আগে আমারা ধস নামার শব্দ উত্তরাখণ্ডে শুনেছি। এখন ওই ধরণের কিছু শুনলেই বুকটা কেমন ছ্যাঁত করে ওঠে।
ওখান থেকে মাউলিনং গ্রামে যাওয়ার যে রাস্তা, তার বাঁ-দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাংলাদেশ বর্ডার। ওদিকটাই তেমন মানুষ থাকে না, বহুদূর অবধি ছড়ান ঘাসজমি আর জ্বলা। কোথাও কোথাও লাল রঙের গরুরা ঘাস খেতে খেতে মুখ তুলে আমাদের দেখে। সব জায়গায় তো আর বর্ডারও নেই। গরু আর চিনি পাচারের ব্যাপারে নাকি জায়গাটা আজকাল বেশ নাম কিনেছে।
আমার আবদারেই গাড়ি এক জায়গায় থামল। আর কেউ নামল না। সবুজ নেটের একটা দেওয়াল, খুব যে শক্তপোক্ত তাও না। আমাকে নামতে দেখে রাস্তার ওপাশের একটা ছোটো ছাউনি থেকে এক মিলিটারি ভদ্রলোক একবার উঁকি মেরে দেখলেন, তারপর আবার উদাসভাবে চেয়ে রইলেন অন্যদেশের দিকে।
আলাদা করে অবশ্য দেখার কিছু নেই। সাধারণ বাংলার মাঠ। বাদামি, কালো গরু চড়ে চড়ে ঘাস খাচ্ছে। যারা জলের কাছাকাছি ছিল তাদের উলটোনো ছায়া পড়ছে আকাশের গায়ে। আর কোত্থাও কিছু নেই। আমি বর্ডারের তারজালিতে নাক ঠেকিয়ে এইসবই দেখছিলাম। দুটো প্রজাপতি আমার দু-পাশে অনেক্ষণ ধরে উড়াউড়ি করছিল। তারপর একটু হাওয়া দিতেই তাতে খানিকটা ভেসে উঠে দুটো ভারতীয় প্রজাপতি পাচার হয়ে গেল বাংলাদেশের দিকে।
মাঝে মাঝেই উলটো দিক থেকে ফুলঝাড়ু বোঝাই করা ছোটো ছোটো ট্রাক হুসহাস করে বেরিয়ে যায়। এই গাছও এখানে প্রচুর। প্রায় বাঁশজাতেরই গাছ, কিন্তু অনেক বেশি সরু। আমি বেতঝাড় সেভাবে চিনি না, তবে আমার ধারণা সে-গাছও ওখানে দেখেছি।
বাকি জায়গাগুলো ঘুরে যখন মাওলিং-এ পৌঁছালাম তখন বেশ দুপুর। গ্রামটাই যে আলাদা করে দেখবার কিছু আছে এমন নয়। প্ল্যান করে বানানো কাঁচা-পাকা বাড়িগুলো সুন্দর হলেও কেমন যেন মনে হয় এখানে বুঝি তেমন ভালোবাসা নেই। যেজন্য জায়গাটা এত নাম কিনেছে, সেই পরিস্কার পরিচ্ছন্নের জন্য তো নাম্বার দিতেই হবে। মেঘালয়ের একটা গ্রাম নিজেদের পরিচ্ছন্নতাকে ইউএসপি করে এত এত পর্যটকদের টেনে আনছে, অথচ মেঘালয় সরকার এই মডেলখানা বাকি রাজ্যে রেপ্লিকেট করতে পারলেন না কেন কে জানে! এই ক-দিনে আমরা যত জায়গায় গেছি, ট্রেক করেছি, নদী পেরিয়েছি কোত্থাও এমন জায়গা পাইনি যেখানে একটুও প্লাস্টিক পড়ে নেই। ব্যাম্বু ট্রেকের পথে তো কন্ডোমের প্যাকেট অবধি পড়ে থাকতে দেখেছি। শরীরের ভেতর সবাই বাঘ-সিংহ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ পৃথিবীর খানিকটা দায়িত্ব নিতে সবার হাতে ফোসকা পড়ে যায়!
মাউলিনং-এ সবাই মেন রাস্তা দিয়েই হাঁটাচলা করে। আমরা তাও গ্রামের ভেতর সরু রাস্তাগুলো ধরেছিলাম। ছোটো ছোটো সব বাড়ি। দোতলার বেশি কেউই আর ঘর তোলেনি। কতরকম যে গাছ। এখানেই প্রথমবার কলসীপত্র ফুল দেখলাম। সে গাছ যে এত বড়ো হয় আমার ধারণা ছিল না। সব মিলিয়ে প্রায় ২০ ফুট। তার পুরো শরীর জুড়েই অসংখ্য ঢাকনা খোলা কলসি। কয়েকটা শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। বাকিদের সবুজ গায়ের পেটের কাছটা খানিকটা করে হলুদ। কলসির ভেতরে খানিক রোঁয়া, আর একদম তলায় একটা নলের খোলা মুখ। আমরা শুকনো পাতা, টুটপিক বা আরও এটা ওটা ফেলে কত চেষ্টা করলাম, যদি একবার চোখের সামনে গাছটাকে শিকার করতে দেখা যায়। একবার একটা মাছির মতো পোকা এসে কলসির কানায় কিছুক্ষণ বসেও থাকল। কিন্তু কিছুতেই ভেতরে পড়ল না!
আর একটা নিরালা মতো ছোট্ট সাদা রঙের চার্চ ছিল। অত বেলায় বন্ধ হয়ে গেছিল অবশ্য। তবু তার বাগানটা বড়ো সুন্দর। আমরা অনেকখানি সময় ওখানে বসেছিলাম। হাতে সময় ছিল বলে চেষ্টা করছিলাম কটা গুবরে পোকা যদি খুঁজে পাওয়া যায়। একটাও পেলাম না। তাদের গানগুলোয় শুধু বসে বসে রেকর্ড করলাম। পরে কত একলা দুপুর যে আমার এসব শুনেই কাটবে।
ঘুরে ফেরার সময় প্রায়ই দেখতাম পাহাড়ের কোথাও-না-কোথাও আগুন লেগেছে। যেন মা সীতার সতীত্ব পরীক্ষা করতে এসে জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। অতক্ষণ ধরে আগুন জ্বলতে কোথাও দেখিনি আমি। ধোঁয়ার চোটে জায়গাটা ঝাপসা হয়ে যেত। আর আলো কমে গেলে নরকের দরজার মতো হাঁ করে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে। বড়ো বীভৎস, কিন্তু কিছুতেই চোখ ফেরানো যেত না।
গুহা ও কবরখানা
আমি মনে করি ভ্রমণ কাহিনি কলমের বদলে, মন দিয়ে লিখলে তার থেকে কিছুতেই মানুষদের আলাদা করা যায় না। সে যতই পাইন গাছ, প্রজাপতি আর ঘাস ফুলের মধ্যে হারিয়ে থাকি না কেন। পৃথিবীতে এসে মানুষকে এড়িয়ে চলার উপায় নেই।
আমরা যার গাড়িতে চড়ে পাহাড়ে যেতাম তার ভালো নাম ছিল সন্তোষ। পদবি হয় মনে নেই, নয় কাকু বলেইনি কোনোদিন। জাতিতে খাসি হলে কী হবে, তরতরিয়ে বাংলা বলতে পারত। অবশ্য ক্রিয়াপদে একটু গুলিয়ে ফেলত মাঝে মাঝে।
একদিন যেমন বলে বসল, “আজ কিছু টাকা দেব।”
আমি সাথে সাথে হাত পেতে বললাম, “আচ্ছা দাও।”
শুনে সে কী রোদ্দুরের মতো হাসি। জানি কেউ মানবে না, তবু আমার মনে হয় মঙ্গলয়েড চেহারার লোকজনের হাসির মধ্যে আমাদের থেকেও অনেক বেশি চিনি গোলা থাকে। গালে অমন লজ্জার মতো রং আনতে লোকজনকে কত কিছুই না ঘষাঘষি করতে দেখেছি।
ওই ক-দিনে আমাদের সাথে খুব ভাব হয়ে গেছিল কাকুর। এমনিতে বড়ো ভিতু। আমাদের সাথে ট্রেকে যেতে বললেই, স্টিয়ারিং ছেড়ে দু-দিকে হাত নাড়ে। যেদিন গুহাগুলো দেখতে যাচ্ছি, সেদিন একটা চমৎকার ভূতের গল্প বলেছিল। সেটা পরে কোথাও লিখব বলে এখানে আর বলছি না।
শিমুল পলাশ এখানে নেই বড়ো একটা। চেরিফুলের গাছ যা আছে, তারাও বড়ো ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। এখানকার আসল সংখ্যাগরিষ্ঠ হল বাঁশ গাছ। তাদের গোছ মোটেই আমাদের বাংলার মতো অত মোটা নয়, লিকলিক করে বাতাসে নড়ে, আর একটার সাথে আরেকটা লেগে কী অদ্ভুত সব শব্দ হয়। আমি প্রায় গাড়ি থামিয়ে নেমে গিয়ে সেসব শব্দ শুনি। বাকিরা কিছুই বুঝতে পারে না। থমথমে দুপুরে কতরকম যে ছায়া পড়ে আমাদের গায়ে। চারদিকে একটাও মানুষ নেই, শুধু একদল গুবরে পোকা ডেকে ডেকে জায়গাটাকে কানায় ভরে রেখেছে। প্রকৃতির যেসব কারুকার্য ধুলোয় মধ্যে হেলায় পড়ে থাকে, তাদেরই ওপরই যেন যত টান আমার। তার বুকের মধ্যে একটা নিশ্বাসও বাজে খরচ করতে ইচ্ছে করে না।
তবে সব গুহাগুলো আমার মোটেই মনে ধরেনি। ভেতরে আলো-টালো লাগিয়ে বিচ্ছিরি একটা কাণ্ড করেছে। যেন পুজো প্যান্ডেলে ঢুকেছি। অন্যসময় পায়ের নীচ দিয়ে জল বয়ে যায়। এখন শুকনো, কোথাও কোথাও ছাদের থেকে টিপ টিপ করে জল পড়ে। ঢোকার মুখ অনেক জায়গাতেই খুব সরু, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। তারপরে চারদিকে কত যে সুড়ঙ্গ। একটা দিয়ে গেলে আরেকটায় গিয়ে ওঠা যায়, তার পাশে আবার হয়তো অন্য আরেকখান গর্ত। আলো লাগানো জায়গাগুলো ছেড়ে, এগলি ওগলি ধরে অনেকটা ভেতরের দিকে গিয়ে পড়লে, গা শিরশিরানিটা এখনও দিব্যি টের পাওয়া যায়।
একবার তো একটা বাঁক ঘুরেই ভীষণ চমকে গেছিলাম। দেখি কী, কালো ব্লেজার আর সাদা গাউন পরা দু-জন বর বউ একটা বিশাল পাথরের ওপর বসে পা দোলাচ্ছে। তাদের আসলে কেমন দেখতে কে জানে! মেকাপ করে দু-জনকেই দেখাচ্ছে ড্রাকুলারদের মতো। গুহার ভেতর তো আর ফ্ল্যাশ না জ্বেলে উপায় নেই। যে ভদ্রলোক ছবি তুলছিলেন, তিনি সাটারে চাপ দিলেই, তাদের ভয়ানক সব ছায়া ফুটে উঠছে গুহার দেওয়ালে। আমি যা খারাপ নজর দিলাম, বিয়েটা ক-দিন টিকবে কে জানে।
এখান থেকে একটু এগিয়ে মোটামুটি আমার বুকের হাইটে একটা গর্ত পাওয়া গেল। আমরা সবাই হ্যাঁচোরফ্যাঁচোর করে তাতে উঠে পড়ে দেখলাম, দাঁড়ানো তো দূর সেখানে ভালো করে বসারই জায়গা নেই। কিছুটা বুকে হেঁটে গেলে অবশ্য খানিক কুঁজো হয়ে হাঁটা যায়। তারপর ওভাবেই কয়েকটা গলি পেরিয়ে বিশাল একটা ফাঁকা মতো জায়গা। ওখানে পৌঁছিয়েই আমরা আমাদের সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলাম। আর তারপর সে কী অন্ধকার! মনে হয় নিশ্বাস নিলেই বুঝি চোখে-মুখে ঢুকে আসবে।
আমি একটু জোর করেই সবাইকে দশ মিনিটের জন্য চুপ করিয়ে রাখলাম। অনু বার বার ফোন অন করছিল, সেটা কেড়ে নিয়ে নিজের পকেটে ঢোকাতেই কোথাও আর কিচ্ছু রইল না। অন্ধকারের নিজস্ব একটা বিজবিজে শব্দ আছে। আসলে আমাদেরই রক্ত চলাচলের শব্দ, কিন্তু আঁধারে ডুবে থাকলে সেসব লজিক আর তখন কাজ করে না। কিন্তু সে-জিনিসও বেশিক্ষণ টিকল না। কত হবে? এক মিনিট। প্রথমে সারা গুহাটা ধূসর হয়ে এল, তাতে কালো মার্কারে আঁকা মানুষ আর পাথরের সিলুয়েট। তারও খানিক পরে অদ্ভুত একটা সবুজ আলোয় ভরে গেল চারদিক। সে এমনই যে আলাদা করে আলো বলে চেনা যায় না, কিন্তু সামনে বসে থাকা রাজের চুলের সাথে ওর চামড়া, জামাকাপড়ের সাথে হাতের ঘড়িটা দিব্যি আলাদা করা যায়। এ-জিনিস রাতের বেলায় ঘুম ভেঙে গেলেও হয়, কিন্তু তখন ওখানে বসে কী অলৌকিকটাই না লাগছিল। মানুষের চোখ আলো খোঁজার জন্যই তৈরি হয়েছে। তবে মনের মধ্যে সে-আলো জমিয়ে রাখার মতো ক্ষমতা সবার থাকে না।
গুহার কথা আর কী বলব। কত হাজার লক্ষ বছর ধরেই না এসব তৈরি হয়েছে! প্রতিটা দেওয়ালে, ছাদে, মেঝেতে আলাদা আলাদা রকম সব নকশা। একটার সাথে আরেকটার কোনো মিল নেই। এসব না দেখলে বুঝিয়ে বলা মুশকিল। অনেকখানি সময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলে পাথরের গায়েই যে কত রকমের গল্প তৈরি হয়।
জানি খারাপ শোনাবে। কিন্তু ঘুরতে গিয়ে আমার সবথেকে বিরক্ত লাগে বাঙালিদের। অমন ন্যাকা আর অসহ্যকর টুরিস্ট আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। অবশ্যই সবাই নয়।
মৌসুমি কেভ পৌঁছনোর আগে অনেকটায় উঠতে হয়। বলছি না? আমাদের নামেই তিন দিনের ট্রেকিং। আসলে রোজই প্রচুর হাঁটতে হত। যে জায়গা দেখতে যাচ্ছি, গাড়ি যেত তার দেড় কিলোমিটার আগে অবধি। জায়গাটাকে বাঁচানোর এর থেকে ভালো ব্যাবস্থা আর হতে পারে না। কী নিরিবিলি সব রাস্তা। ধাপে ধাপে উঠতে হয়। অনু তো আগে এসেছে, কিন্তু সে অনেক ছোটোবেলায়। ওর প্রায় জাতিস্মরের মতো হঠাৎ হঠাৎ কিছু কিছু ছবি মনে পড়ে যায়। ও-ই বলল রাস্তার ধারে যে নালির মতো গোল গোল গর্তগুলো আছে, সেখান দিয়ে বর্ষার সময় তির তির করে জল যায়। এই গোটা টুরে কত যে শুকিয়ে যাওয়া ঝরনা দেখলাম। এও এক অন্যরকম মজা। ঝরনা না থাকলে কী হবে, কোথাও কোথাও ঠিকই জল জমে থাকে। কিছু পাখি হয় যাদের শুধু ঝরনা বা নদীর আশেপাশেই বেশি দেখা যায়। জলের জায়গা ছোটো হয়ে এলে, তারাও ঘন হয়ে থাকে। একই জায়গায় অনেককে একসাথে দেখা যায়। এও এক মস্ত লাভ।
এইসব নিয়ে যখন গুহার মুখে পৌঁছেছি, দেখি তার সামনে চাতালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একটা বাঙালি পরিবার সবাই মিলে জিভ বার করে হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে। তার মধ্যে ক্যাটক্যাটে হলুদ জামা পরা কর্তা গোছের একটা লোক খানিকটা দম ফিরে প্রায় চিৎকার করে বলে চলেছে, “পয়সা খরচ করে এতদূরে এসে হামাগুড়ি দেব!”
ভদ্রলোকের মেয়ে আর বউ বোধহয় গুহার মধ্যে খানিকটা এগিয়েছিলেন কোনোরকমে। আমরা যখন ঢুকব বলে নীচু হচ্ছি, তখন দু-জনেই গজগজ করতে করতে বেরিয়ে আসছে। কারোর মুখই এখন আর মনে নেই, কিন্তু ব্লেজার পরে অ্যাডভেঞ্চার করতে আসা মানুষ আমি এই প্রথম দেখলাম। কবে যে একটু কেতাদুরস্ত হব!
না বাঙালিদের গাল দেওয়া এখনও শেষ হয়নি। এরা তো তাও গুহার বাইরের অক্সিজেন নষ্ট করছিল। যখন আরও অনেকটা ভিতরে ঢুকে খানিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছি, তখন কোত্থেকে বাবা মা আর পিছনপাকা একটা বাচ্চার পরিবার এসে জুটল আমাদের সঙ্গে। ছেলেটার বয়স ন-দশ বছরের বেশি হওয়ার কথা নয়। সারাক্ষণ একটা ক্যামেরা ধরে কাল্পনিক ‘গাইজ’দের সাথে হিন্দিতে বক বক করে যাচ্ছে। এমনিতে আমি বাচ্চাদের বড়ো একটা পছন্দ করি না। তারপর যখন বুঝলাম এরা আসলে বাঙালি, তখন তো সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। ভালো করে শুনলে বোঝা যায় ছেলেটার হিন্দি জটায়ুর থেকে এমন কিছু উন্নত মানের নয়। কিন্তু তবু এই যে নিজের ভাষা, তারপর যেখানে এসেছে তার প্রকৃতিকে অসম্মান করার গোটা ব্যাপারটাই তার বাবা মায়ের সামনে হচ্ছে দেখে খারাপ লাগল। আমি খানিকটা নীতি পুলিশ একথা ঠিক। কিন্তু তাও বলব সরকার থেকে বাবা-মা হতে চাওয়া ছেলে-মেয়েদের ইন্টারভিউ নেওয়া উচিত। তাতে পাশ করলে, তবে বাচ্চা নেওয়ার পারমিশান দেওয়া হোক। গণ্ডায় গণ্ডায় অমানুষ সৃষ্টির চেয়ে, একটা-দুটো মানুষ তৈরি হলে পৃথিবী খানিক কম দূষিত হবে।
ইচ্ছে করেই দলটাকে এগিয়ে যেতে দিলাম। তখন যেখানে দাঁড়িয়ে, তার চারদিকে অনেক পাথরের থাম বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে ছাদের দিকে উঠে গেছে। তাদের গায়ে দারুণ সব কাজ! কোথাও কোনো সিমিট্রির ব্যাপার নেই, তাও কী যে সুন্দর। দেওয়ালে হাত দিলে, সেটা যেন পিছলে যায় এমন মসৃণ। খুব কাছে চোখ নামিয়ে এনে দেখলে, তার গায়েই আবার কতরকম রঙের প্যাটার্ন। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হাওয়া, জলে, পোকামাকড়ের চলাফেরায় এসব তৈরি হয়েছে। হন হন করে হেঁটে বেরিয়ে গেলে তার কিছুই টের পাওয়া যায় না। ওই নামেই দেখা হয়।
এবার বুদ্ধি করে পকেটে টর্চ এনেছিলাম। কিন্তু তার আলোটা বড়ো বিচ্ছিরি। এই নীল এলিডি আলোগুলো যে-রঙের ওপরই পড়ুক না কেন, জায়গাটা কেমন যেন পুড়িয়ে দেয়। আগেকার হলদে আলোগুলোয় এমন জোর হয়তো ছিল না, কিন্তু রহস্য ছিল বেশ। কোনো জায়গায় থাবা বসালে তার আলো,ছায়া, মিডটোন যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে রাখত। এই টর্চে সেসব নেই। তবু দেখা তো যায়, ওপরের অন্ধকারে কত যে পাথর ছুঁচলোও হয়ে আছে! তাদের গায়েও আবার কতসব নকশা।
আমি শুধু ভাবি, প্রকৃতির সামান্য হাওয়ার স্রোতে, জলের ঝাপটা লেগে বা শুধুমাত্র অভিকর্ষের চোটেই যা সব দৃশ্য তৈরি হয়, তার একফোঁটাও মানুষ শব্দ বা তুলি দিয়ে ধরে রাখতে পারে না। তাদের আবার শিল্প নিয়ে এত বড়াই। এতসব মার মার কাট কাট!
আর এ ছাড়া শুরুতে যে গার্ডেন অফ কেভে গেছিলাম। সে জায়গার বেশিরভাগটাই বড়ো কৃত্রিম। আসলে গুহা না প্রকৃতি জায়গাটাকে ঘন দুধসাদা সব ঝরনা দিয়ে মুড়িয়ে রেখেছে। তাই জল শুকিয়ে গেলে মানুষের আজেবাজে সব কীর্তিগুলো বেশি চোখে পড়ে। তবে এখানে একজায়গায় বেশ সুস্বাদু জল পাওয়া যায়। কী যে মিষ্টি খেতে। এরা বলে এই জলের নাকি ম্যাজিক আছে। একটা দেওয়ালের ফুটোয়, কাঁচা বাঁশের চোঙা লাগানো। তার থেকেই ঝর ঝর করে ম্যাজিক পড়ে নষ্ট হচ্ছে সারাদিন। আমি ছাড়া কারোর কাছেই বোতল ছিল না। তাই ওই জল আদেখলার মতো অনেকখানি খেয়ে, বোতলভরতি করে হোটেলে এনেছিলাম। অনু বার্বিকিউ চিকেন খেয়ে, বোকার মতো সেই জলে হাত ধুতে গিয়ে অনেকখানি নষ্ট করে ফেলে।
গুহা নিয়ে এর বেশি আর কিছু লিখব না। টুর গাইড তো আর লিখতে বসিনি। ট্র্যাভেলগে লেখকের কিছু কিছু জিনিস বাদ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। ওখান থেকে ফেরার সময়কার একটা গল্প বলি বরং। জায়গাটা সোহারার কাছে। যাওয়ার সময়তেই দেখে রেখেছিলাম। ফেরার রাস্তায় প্রায় জোর করেই গাড়ি থামালাম। সামনেই একটা চার্চ। আর তার উলটোদিকে হলদে ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ একটা পাহাড়। খুব যে উঁচু তা নয়। তাই পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তা থেকেই কালো পাথরে বানানো কবরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। কেউই আর আমার সাথে আসতে রাজি হল না। দিনের বেলায় এই ভরা রদ্দুরের মধ্যে কিসের এত ভয় কে জানে। পাহাড়টা কিন্তু ন্যাড়া, একটাও বড়ো গাছ নেই। ঘাস আর ঝোপঝাড় যা ছিল রোদে সেসব শুকিয়ে বুক অবধি উঠে এসেছে।
সারা বছর ধরে আঁকাআঁকি করার সুবিধা হল, মাথার মধ্যে যেকোনো জায়গার রং চট করে বদলে ফেলা যায়। তেমনিভাবেই দেখলাম এ-পাহাড় সবুজে ভরে থাকলে মোটেই এতটা মানায় না। সে হয়তো অন্যরকম সুন্দর। কিন্তু এই মৃত সময়ের বুকের ওপর বসে থাকা কালো পাথরের সমাধি ফলকগুলোর আশেপাশে মরা হলুদ রংটাকেই যেন বেশি মানায়! এক-দুটো সমাধি অনেকটা উঁচু হয়ে আকাশের সাথে নিজের হাত মেলাতে গিয়ে খানিক ব্যার্থ হয়ে, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। এটা যে সময়কার সে-সময়ের শিল্পে শৌখিনতার আশা করা বিলাসিতা। পাহাড়ের এত ওপরে রাজত্ব করতে এসে সাহেবরা তাদের মৃতদেহ সাজানোর মতো শিল্পী পাবেনই-বা কোথায়! তাই এখানকার সব কবরগুলোই হয়েছে খাপছাড়া। কোনরকমের পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে বানানো। তখন এখানকার কেউ পার্কস্ট্রিট সিমেট্রি ঘুরতে গেলে তার নিশ্চয় খুব মন খারাপ করত। কিন্তু তারপর ফিরে এসে, নিজের প্রিয়জনের কবরের পাশে মেঘেদের ঘুমিয়ে থাকতে দেখে, নিজেরায় বোধহয় হেসে ফেলতেন। আমি বারবার বলি, সারাজীবন ধরে বলব— প্রকৃতির থেকে বড়ো শিল্পী এই পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তাকে নকল করেই আমাদের গোটা জাতটা কোনোরকমে টিকে আছে।
এখানে সবথেকে লম্বা যে-কবরটা, তাকে দেখতে অনেকটা লাইট হাউসের মতো। অবশ্যই আসল লাইট হাউসের থেকে অনেক ছোটো আর এবড়োখেবড়ো। পাথরে পাথর জুড়ে বানানো। ওপরে ওঠার কোনো ব্যাবস্থা নেই, উঠতে পারলে অনেকদূর অবধি দেখা যেত নিশ্চয়। হাঁটতে গিয়ে বুঝলাম, এই পাহাড়ের গোটা পিঠটাই আসলে মৃত মানুষদের দখলে। মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা মাটির রাস্তা। তাই দিয়ে পাহাড়টা পেরিয়ে যেতে পারলে সেদিকটা আবার বেশ সাজানো-গোছানো। নতুন মানুষদের ওখানেই কবর দেওয়া হয়। কেমন যেন মেসবাড়ির ঘেঁষাঘেষি বিছানা। পূর্বপুরুষদের মতো শুয়ে থাকার অতটা করে জায়গা এখন আর কেউ পান না। তবে এখান থেকে একটা ছোটো পিচের রাস্তা পেরোলেই খুব সুন্দর একটা উপত্যকা দেখা যায়।
সেটা দেখতে যখন নামছি, দেখি কবরখানার গেটের কাছে দুটো স্কুল ইউনিফর্ম পরা মেয়ে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। গালে সেই লজ্জার মতো রং। মনে হয় স্কুল বাংক মেরে দু-জন মিলে ঘুরতে বেরিয়েছে। আমি তো এসব সময় মুখ গম্ভীর করে, ভুরু কুঁচকে ভীষণ জেন্টেলম্যান হয়ে পড়ি। কিন্তু দেখলাম ওরা সেসব পাত্তাই দিল না। চোখাচোখি হতে খুব স্মার্টভাবে জিজ্ঞেস করল, “ক্যান ইউ টেক আ পিকচার অফ আস”
আমিও আমার সেরা অ্যাকসেন্টের ‘সিওর’ বলে ফোন নিলাম। নতুন কবরখানার ক্যাটক্যাটে লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি। সে আর কত ভালো হবে! কিন্তু তাই দেখেই দু-জনের সে কী আনন্দ। আমি ফোনটা হাতে দিয়েই হাঁটা লাগিয়েছিলাম, পিছনে ‘ইইইই’ চিৎকার শুনে ঘুরে তাকাতেই, একগাদা থ্যাঙ্কিউ এসে আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেল।
ছবি: সৌভিক (রাজ), সোমদত্তা, অণু, তন্ময়
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখিরনিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।