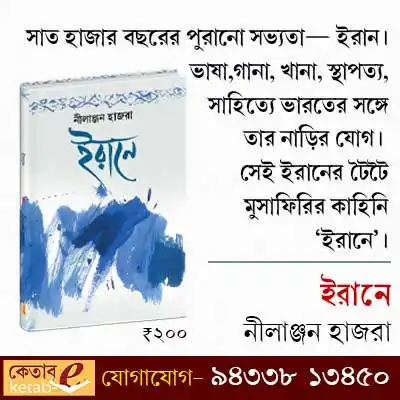উত্তর-পূর্ব ভারতের ছবির মত সুন্দর এক পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয়। মেঘ, বৃষ্টি আর ঝর্ণা রাজ্য— মেঘালয় ভ্রমণের রঙিন অভিজ্ঞতা উঠে এল তন্ময় বিশ্বাসের কলমে। আজ শেষ পর্ব।
ডেভিড স্কট ট্রেক
ডেভিড স্কটের পাহাড়ে রডোডেন্ড্রনের গাছ খুব বেশি নেই। অল্প যে-কটা গাছে ফুল আসে, নাগালের মধ্যে পেলে এখানকার লোকজনই গাছ থেকে পেরে কচড়মচড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে সব। গাইড ছেলেটাকেও ফুল খেতে দেখে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। কী এমন পেট ভরে! অবশ্য আমাদেরও দিয়েছিল একটা করে। ওরা মুখে নিয়েই থু থু করে ফেলে দিল। খুব নাকি কষটা। আমি আর দাঁতে কাটিনি। গাছে তো আর জোড়া লাগাতে পারব না, তাই কানের ওপর যত্ন করে গুঁজে রেখেছিলাম। প্রথমে খেয়াল করেনি কেউ। তারপর চোখের পড়ার পর সোম বলল এতক্ষণে আমি নাকি পারফেক্ট পুকি হয়ে উঠেছি।
রাজ অবশ্য বুলি করার একটা সুযোগ সহজে ছাড়ে না। এটা ওটা ছুতো পেলেই আমাকে মেয়েলি বলে দাগিয়ে দিতে বড়ো ভালোবাসে ও। এসব আমি ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি। তখন ভেউভেউ করে কাঁদতাম। পরে ভেবে দেখেছি জীবনে মায়ের থেকে বেশি তো আর কাউকে ভালোবাসিনি। তাই আমার কিছু কিছু স্বভাব যদি মায়ের মতো হয়, তাতে আমার অন্তত কোনো সমস্যা নেই।
খুঁজে খুঁজে ওদের অনেকগুলো পাইন কোন কুড়িয়ে দিয়েছিলাম। এমনিতে প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু অক্ষত খুঁজে পাওয়ায়ই মুশকিল। পরে ওগুলোর থেকে বেছে বেছে অনু আমাকে একখানা দিয়েছিল। সেটা এতই ছোটো, যে ডাল থেকে আর তাকে আলাদা করা যায়নি। আমার কাছে এসব জিনিস টেকে না। তাই ঠিক করেছি ঋতুপর্ণাকে ওটা বরাবরের জন্য দিয়ে দেব।
সোম জঙ্গল-টঙ্গল ঘেঁটে সবাইকে একটা করে সুন্দর দেখতে ফল এনে দিয়েছিল। এইটুকুনি ওয়াক নাটের মতো ছোটো আর শক্ত। কিন্তু গা-টা একেবারে সাপের চামড়ার মতো। সে-ফল এতদিন পরেও এতটুকুনও নষ্ট হয়নি। বরং শুঁকলে খানিক খানিক বনের গন্ধ পাওয়া যায়।
ডেভিড স্কটের গোটা ট্রেকটাতেই অনেকবার করে নদীর কাছে আসা যায়। নামার সময় হুড়হুড় করে আসছিলাম বলে গোড়ালিতে লাগছিল। ওঠার সময় কিন্তু ঢালগুলো তেমন উঁচু না। নদীর পাশ দিয়ে যে রাস্তাগুলো গেছে, সেখানে অদ্ভুত সব নূপুরের শব্দ কানে আসে। জল আর পাথরের কথা ভালো করেই জানি। তবু আকাশকুসুম কল্পনা করতে কী যে ভালো লাগে। বেশিরভাগ জলেই নীল রং ধরে আছে। নীচের প্রত্যেকটা পাথর ওপর থেকে গোনা যায়। এ কূল ও কূল ছাপিয়ে যাওয়া নদীদের আমার ভালো লাগে না। যার মনের ভেতরটা দেখতে পাব না, বুকের ধুকপুকটুকু ছুঁতে পারব না, তাকে ভালোবাসব কী করে!
সোমের কথা বোধহয় লিখে লিখেও ফোরাবে না। আমার বয়স আরেকটু বেশি হলে মেয়েটাকে দত্তক নিয়ে মনের মতো করে তৈরি করতাম। অন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম, ওর মনের ভেতরকার হিরেকুচিগুলোর কথা ও নিজেও বোধহয় এর আগে জানত না। এখন পাইন গাছ ছুঁয়ে আসা রোদ্দুরে সেগুলো প্রচণ্ড তেজে যেন জ্বলে উঠেছে।
একবার তো রাস্তা ছেড়ে পাথরে পাথরে লাফিয়ে নদীখাতের এমন বিপজ্জনক দিকে গিয়ে দাঁড়াল, যে আমরা সবাই ভয়ে অস্থির। গাইড ভাই ফ্যাকাশে মুখে বলে, “সি হ্যাজ নট ফিয়ার ফ্রম এনিথিং!”
ওর তখন এসবে হুঁশ নেই। আসার সময় শুনেছিল এখানকার কিছু কিছু পাহাড়কে কথা দিলে, পাহাড় আবার সে-কথা ফিরিয়ে দেয়। তাই হাত ছড়িয়ে সে কী চিৎকার! তারপর প্রতিধ্বনি হচ্ছে না দেখে, অনুর ওপর অর্ডার হল ছবি তুলে দেওয়ার জন্য। এবার আমিই বকা দিলাম, “কষ্ট করে গেছিস অতদূর। আশপাশটা দেখ ভালো করে। ছবি নিয়ে কী হবে!”
বললাম না? আমি আসতে আসতে কাকু এরার মধ্যে ঢুকে পড়ছি।
আর কিছু ছিল ফল কুড়ানোর নেশা। ওই সাপের খোলসের মতো ফলটার কথা তো বললামই। আরও কতরকম যে খুঁজে পেল। যাই পায়, গাইডকে জিজ্ঞেস করে, ক্যান উই ইট দিস? গাইড হেসে মাথা নাড়ে। এখন ফল পাকার সময় নয়। পাহাড়ের প্রায় কোনো ফলই কাঁচা খাওয়া যায় না। একবার একটা ফল পাওয়া গেল, যার বাইরেটা সবুজ, কিন্তু ওপরটা ছাড়িয়ে নিলেই হুবহু পেঁয়াজের মতো রং। তখন গাইড এগিয়ে গেছিল, তাই আমিই বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম, এ হল অনিয়ন নাট। পাকলে লোকজন স্যালাড বানিয়ে খায়। গুল মারার সময় আমি কোত্থেকে যেন একটা ব্যারিটোন বের করে আনি। ভদ্রমানুষদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, মাঝে মাঝে আমি নিজেই নিজের গুল বিশ্বাস করে বসে থাকি।
কয়েকটা জায়গা থেকে আবার নদীটার তিন-চারটে বাঁক একসাথে দেখা যায়। আকাশের ছায়া পড়ে কী সুন্দর যে দেখতে লাগে। বেড়ালের চোখের মতো নীল জলে রোদ পড়লে, আঙুলের মতো সেসব গিয়ে বিদ্ধ হয় নীচের পাথরে। তখন জলের নীচের পৃথিবীটাকেই আসল বলে মনে হয়। আর তার সে কী টান! আমার মতো করে তো আর কেউ লেখেনি, তবে জল সবাইকেই অল্পবিস্তর টেনেছিল। সুযোগ পেলেই জুতো খুলে বসে পড়া হচ্ছিল জলের ধারে।
আমাদের গাইড ছেলেটাও বড়ো ভালো ছিল। আমার থেকে ছোটোই হবে হয়তো। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে যখন অপেক্ষা করছিলাম, তখন কেউ এলেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি গাইড। আর তখন অনু দূর থেকেই তাদের নাকচ করে দিচ্ছিল। ওর যুক্তি হল, এইসব স্যান্ডেল পরা লোক কিছুতেই গাইড হতে পারে না। সরকারি গাইডের পায়ে জঙ্গলে হাঁটার মতো একটা জুতো তো অন্তত থাকবেই। শুনে আমি আর রাজ মিটিমিটি হাসছিলাম। তারপর সত্যি সত্যিই যখন গাইড এল— তখন তার পায়ে পাতলা স্ট্রিপের হাওয়ায় চটি। সোলদুটোর নীচের দিকটা এতই মসৃণ যে খানিক ভিজে গেলেই শপশপ করে শব্দ হয়।
ও-ই প্রথম ডেভিড স্কটের গল্প বলে। সাহেব ব্যাবসাপাতি করার জন্য এই রাস্তাখানা বানিয়েছিলেন। এর আবার প্রচুর শাখা পথ আছে। গাইড না আনলে চিনে যাওয়া খুব মুশকিল।
আমরা অনেক তাড়াতাড়ি শুরু করেছিলাম বলে, গোটা রাস্তায় আর একটাও মানুষ পাইনি। শুধু মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে মাথা তুলে তাকাচ্ছে ইয়া বড়ো বড়ো সব গরুর দল। তেড়ে এলে যে সরে দাঁড়াব তারও জায়গা নেই। তিনটে না চারটে পাহাড় বোধহয় পেরিয়েছিলাম। তাদের মাথার ওপর বাতাস এসে আটকে গিয়ে গোঁ-গোঁ করে ভয়ানক সব শব্দ হয়। সবাই নেমে গেলেও, আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই শব্দ শুনি। আমার তো পাহাড় দেখার কোনো গুরু নেই। এসব আমি নিজে নিজেই করি। একলা হয়ে চোখ বন্ধ করে এটা ওটা ভাবতে বড়ো ভালো লাগে!
আধখানা রাস্তা পেরিয়ে যখন নদীটার একেবারে বুকের ওপর উঠে এলাম, তখন বেলা পড়ে গেছে। রোদের কুচিতে চিকচিক করে ভাসছে গোটা নদী। আর কী যে ঠান্ডা জল! একটুখানি বসে থাকলেই পায়ে ভারি আরাম হয়। এখানে ঢাল অত বেশি না। পাহাড় যেন খানিক হেলান দিয়ে নদীকে বয়ে যেতে দিয়েছে। এত নাচগান করে থাকা জলে তো আর মাছ থাকে না। কিন্তু অনেকরকম রঙের পাথর আছে নদীবুক ভরতি করে। সবই প্রায় গোল। জলের ভেতরে কী সহজে তুলে ফেলা যায়, ওপরে আনলেই রাম ভারী। আমি একেকটা তুলে সবার কাছাকাছির জলে আছড়ে ফেলছিলাম, আর সাথে সাথে সেখানকার জল “আর্কিমিডিস মাই কী জয়” বলে ওদের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তাই দেখে গাইড ভাইয়ের সে কী হাসি!
এখানে এসে দেখলাম অনুর বেশ সাহস বেড়েছে। জলের মধ্যে পা ফেলে নিজে নিজেই অনেকটা ওপরে উঠে গেল। সহজ নয় কিন্তু, তলার সব পাথর কাচের মতো পিছল আর হড়হড়ে। কোথাও বেকায়দায় পা ঢুকে গেলে বের করে আনা শিবেরও অসাধ্য। ওখানে গিয়ে কী খুঁজছিল কে জানে, ঘুরতে আসা মানুষের মধ্যে কৌতুহল দেখলে আমার ভালো লাগে। আরেকটু নীচের দিকে আকাশ আর সোমও বসে বসে পাথর কুড়াচ্ছে। আবার সাজাবে বোধহয়।
অনু যেদিকে গেল, তার অনেকটা পিছনে দিগন্তের কাছাকাছি গিয়ে আকাশের সাথে ভীষণ ভাব হয়ে গেছে পাহাড়ের। দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে সমস্ত গাছপালা। মেঘ এসে ঢেকে রাখে তাদের সংসার। তারপর কার যে কী হয়। দূরে সরতে সরতে আকাশ চলে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাহাড় শুধু নদী কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বয়ে যায় পৃথিবীতে।
এখানে বসে থাকতে থাকতেই মেয়েদের একটা বড়ো দল আমাদের ধরে ফেলল। কোন দেশের ঠিক বুঝলাম না। সবার চামড়াই প্রায় গমের মতো, রোদ পরে চারিদিক একেবারে ঝলসে দিয়েছে।
ওরা যে খুব হইচই করছিল তা নয়। তবু এবার সবাইকে তাড়া দিয়ে ওঠালাম। এরা সাথে সাথে চললে আর নিরিবিলিতে নিজেদের মতো হাঁটা যাবে না। গেছোপনা করারও একটা স্পেস দরকার।
এবার রাস্তাতে আর অত খাড়াই নেই। মাঝে মাঝেই বড়ো বড়ো সব ঘাস। এতক্ষণ যেসব গরু, মোষ দেখছিলাম এখানে দেখলাম তাদের মালিকরা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কারোর হাতেই তেমন লাঠি নেই। দরকার হলে বোধহয় ডাল ভেঙে নেয়। আরেকটা অদ্ভুত জিনিস হল কোনো গরুর গলাতেই আমি সেভাবে ঘন্টা দেখলাম না! তাই ব্যাটারা বাঁক ঘুরে একদম সামনে এসে না পড়লে আগে থেকে বোঝাও যায় না তেমন।
এসব জঙ্গলে অবশ্য হিংস্র পশু পাখি নেই সেভাবে। অনেক ওপরে কয়েকটা চিলকে পাক দিতে দেখেছি। তারা আর যা-ই হোক গরু মোষ তো আর উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এ ছাড়া দু-খানা কুচকুচে কালো বেড়ালকে গজগামিনী চালে হেঁটে বেড়াতে দেখেছি। তারা বেজায় গম্ভীর লোক। সত্যিকারের মানুষকে একদম পাত্তা দেয় না। তবে জঙ্গলে না, ওরা থাকে গ্রামে। এই যে পুরো ১৬ কিলোমিটার রাস্তা তার মাঝে এই একটি মাত্র গ্রাম। ঢোকার আগে ভুট্টা খেতের ওপর লাইন দিয়ে চেরি ফুল ফুটে থাকে। আমরা সবাই আলপথ ধরে সেগুলোই দেখতে ছুটলাম।
এ-গ্রামের খুবই ভজখট একখান নাম আছে। কিন্তু কোনো টুরিস্টই সেটা ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারে না বলে, এর নাম হয়ে গেছে ম্যাগি গ্রাম। নেসলের লোকজন জানতে পারলে কালকেই বোধহয় ক্যামেরা নিয়ে হাজির হবে ওখানে।
আমরা অবশ্য ম্যাগির দোকান অবধি আর গেলাম না। গ্রামের পাশের যে ঢাল থেকে গোটা উপতক্যাটা দেখা যায়, ওখানেই চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম সবাই। অনুর ভারি দুঃখ ছিল মেঘালয়ে এসে একফোঁটাও বৃষ্টি ভেজা হল না। ওকে ওখান থেকেই আঙুল উঁচিয়ে একখানা গাছের দিকে দেখালাম। সে উপত্যকার অনেকটা নীচে। পাইনই হবে বোধহয়। বাজ পড়ে একদম ঝামা হয়ে আছে। সেই দেখে এই ঝলমলে রোদের মধ্যেও যেন কেঁপে উঠল একবার।
আমাদের পাশেই গ্রামের এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। গাইডের সাথে এতক্ষণ ইংলিশে কথা বলে কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “ক্যান আই টেক ইওর ফটো?” উনি খুব জোরে জোরে মাথা নাড়লেন দু-দিকে। তারপর হিন্দিতে জিজ্ঞেস করাতে সে কী লজ্জা! ছবি দেখে তো হাঁটুতেই মুখ লুকিয়ে ফেলেন প্রায়। তাও দেখা চাই।
একটু পরেই ধোঁয়া ওঠা ম্যাগি চলে এল। সাথে এক কৌটো চিলিফ্লেক্স, যে-যার দরকারমতো ছিটিয়ে নেবে। সাধারণ এক বাটি ম্যাগি, পরিমাণেও খুব কম। তবু পরিবেশের জন্য, বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়ার আরামে ওটুকুই খাবারই যে কত তৃপ্তির। কী ভাগ্যিস এখনও পৃথিবীতে সব কিছু টাকা দিয়ে কেনা যায় না।
আমরা আসলে বেশ পা চালিয়েই এসেছিলাম। কিন্তু গ্রামে এসে একটু বেশিই শুয়ে-বসে ছিলুম বলে, সেই মেয়েদের দলটা আবার আমাদের ধরে ফেলল। ওদের মধ্যে বোধহয় মিশুকে মানুষ কেউ নেই। তাই অনু চেষ্টা করেও কারোর সাথে তেমন কথা বলতে পারল না । শুধু নীচ থেকে ওদের সঙ্গে আসা একটা সাদা-কালো কুকুর, ওই দলের সাথে বোর হয়ে এবার আমাদের সঙ্গ ধরল। এর পিছন দিকটা আবার খানিকটা বাঁকা, তাই সামনের দিকে হাঁটলেও মনে হয় পাশের দিকে সরে যাচ্ছে। যতই জোরে যাই ওর সাথে তো আর পারা যায় না। তাই ও এগিয়ে গেলেও রাস্তায় কোথাও একটা দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। ফড়িং দেখে, মাছি তাড়ায়, এরিয়া মার্ক করে— তারপর আমাদের কাউকে দেখতে পেলেই আবার দৌড়। এরকম ভবঘুরে গাইড কুকুর আমি অনেক পাহাড়েই দেখেছি। এরা পুরো রাস্তাটাই চেনে। কিন্তু কিছুতেই একা যাবে না। কখনো কাউকে পছন্দ হলে নাচতে নাচতে তার সাথেই ঘুরতে বেরোবে। ট্রেকিং-এর ওই মাথায় গিয়ে যে ফিরে আসবে তাও না। যতদিন ইচ্ছা ওখানেই থেকে যাবে। তারপর আবার কাউকে মনে ধরলে— প্রথমে তার সামনে খুব করে গড়াগড়ি খাওয়া হবে, তখন ঠিকঠাক আদর করতে পারলেই আপনার জ্যাকপট। গোটা রাস্তায় আর এক মুহূর্তেও জন্যও চোখের আড়াল করবে না।
এবার রাস্তা কিন্তু আর অতটা নির্জন রইল না। প্রায় গ্রামের লোকজনকে দেখা যেতে লাগল। হাতে ইয়া বড়ো বড়ো সব পুঁটলি। আজ না কি এদের কাপড় কাচার দিন। সে এক বড়ো বাজে দৃশ্য। যেখানে নদীর জল খানিক স্থির সেখানেই একগাদা সার্ফ ঢেলে প্রচণ্ড আছড়ে-পাছড়ে কাপড় কাচা চলছে একটানা। এদিকার জলও নীলই ছিল, কিন্তু সার্ফের চোটে গদের আঠার মতো বিচ্ছিরি একটা রং ধরেছে এখন। এক জায়গাতে তো আর সবার আঁটেনি। তাই খানিক খানিক গিয়েই একেকটা করে দল জায়গা পেয়ে বসে গেছে। আমাদের লেজওয়ালা গাইড দেখলাম সবাইকেই চেনে প্রায়। দেখা হলেই লাফঝাঁপ করে আহ্লাদ দেখিয়ে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসছে। কাপড় শুকানোর জন্য দড়ির ঝামেলায় আর যায় না কেউ। শুকনো ঝোপঝাড়ের ওপরই টানটান করে সব মেলে দেয়। অনেক ওপর থেকে দেখলে সেগুলোকে দেখায় মাঠে চড়ে বেড়ানো পায়রাদের মতো। জামাকাপড়ে রঙের তেমন বৈচিত্র্য নেই এখানে। আমাদের সাদা-কালো গাইড তাদেরই একটা কম্বলে, নির্দ্বিধায় পেচ্ছাপ করে নিজের বলে দাগিয়ে দিল।
এখানে আকাশ অনেকখানি খোলা। আর কৃষ্ণঠাকুরের গায়ের মতো নীল। নীচে কত যে বড়ো বড়ো ঝরনা এখন জল না পেয়ে ঘুমিয়ে আছে! একবার একটা খুব ছোটো ব্রিজের ওপর অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালাম। দু-দিকের পাহাড়ের একদম মাঝখানে টলমলে নদী। তার ওপরে ছোট্ট একটা ব্রিজ। সেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু কয়েকটা ভেড়া ছাড়া আর কেউই তখন দেখল না। সবাই এগিয়ে গেছে দেখে আমি জোরে একবার চেঁচালাম। পাহাড়ের প্রায় প্রতিটা ভাঁজ থেকেই যেন সেই শব্দ আবার ফিরে এল আমার কাছে। কী অদ্ভুত! পাহাড়-সমুদ্র কেউই দেখছি নিজের কাছে কিছু রাখতে চায় না। এখন বুকের ভেতর এত টলমলে জল নিয়ে আমি যাব কোথায়!
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
ডাবল ডেকার লিভিং রুট ব্রিজ
এখন যেভাবে হাঁটছি আমার বাবা এটাকে বলে লিটিরপিটির করে চলা। এক পা করে ফেলছি তো মনে হচ্ছে সিঁড়ির সাথে ওখানেই সেটা গেঁথে যাচ্ছে একেবারে। ব্যথার কথা তো ছেড়েই দিলাম। তবে আমার সবথেকে কিম্ভুত লাগে গালদুটোর কথা ভাবলে। গোটা ব্যাপারটায় এদের একফোঁটাও কাজ নেই। তবু ট্রেকিং-এর শেষের দিকে কোন আনন্দে যে এত দপদপ করে লাফায় কে জানে! একবার চূড়ায় উঠে, বড়ো আহ্লাদে একজনের গালে গাল ঠেকিয়ে বসেছিলাম খানিকক্ষণ, সে ছিল ডাক্তার। ঘড়ি দেখে আমার হার্টবিট মেপে দিয়েছিল। আমি তো আর দেখতে পাই না, কিন্তু লোকে বলে তখন নাকি ডালিম কুমারের মতো লাল হয়ে যায় গালদুটো। নিজের ফিটনেস দেখে নিজেই ভেতর ভেতর লজ্জা পাই কি না কে জানে।
এখানকার লোকদের গালে নর্থ বেঙ্গলের মতো ওই লজ্জা পাওয়া রংটা নেই। বাচ্চারাও শুধু ফুলো ফুলো গাল নিয়েই ঘুরে বেড়াই। যখন ওরকম অস্বাভাবিক রকমের পাকাল মাছের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছি, তখন একটা বাচ্চা মেয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েই বসেছিল। আমাকে দেখে হুট করে মুখটা দুই হাঁটুর মধ্যে লুকিয়ে ফেলে, প্রচণ্ড মিষ্টি একটা গলায় বলল, “হ্যালো ডু ইউ ওয়ান্ট ওয়াটার মিলন, পাইন অ্যাপেল?”
আমি তো হাবা। কোন তালে ছিলাম কে জানে! প্রথমে বুঝতেই পারিনি। তারপর মেয়েটা আবার বলায় ফিক করে হেসে ফেললাম। বেচারা দোকানদারি করতে বসে কী লজ্জাটাই না পেয়েছে।
পরে ভুলে যাব বলে ওখানেই একটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে পিচ্চিটার কথা লিখে রাখছি, তখনই ঝমঝম করে আমার ফোনটা বেজে উঠল। আর বাচ্চাটা হাঁটুর মধ্যেই তুলোর ফুরকির মতো দূর দূর করে কেঁপে উঠে আমার দিকে তাকাল একবার। আচ্ছা এদের চোখে-মুখে সুগার হয় না?
আরেকটা বাচ্চা তো একদমই চীনা পুতুল। হলুদ জামা পরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে উথালপাথাল কিছু একটা ভাবছিল। আমার সাথে চোখাচোখি হতে টুই করে একবার ভুরুটা নাচিয়েছিলাম শুধু। আর ওমনি হিন্দি সিনেমার নায়িকার মতো চমকে গিয়ে এক-পা পিছলে, হাতদুটো হাওয়ায় ঝাপটে সিঁড়ি থেকে টুপ করে পড়ল আমার কোলে। কী মিষ্টি করেই না একটা থ্যাঙ্কিউ বলল! জীবনটা এত সুন্দর কেন কে জানে।
অবশ্য সিঁড়ি বাইবার সময় অত ভালো ভালো কথা আর মাথায় থাকে না। এমনিতেই ৬০ পা করে হাঁটছি। আর দম নেওয়ার সময় আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি সূর্যটা কেমন রং বদলে দূরের পাহাড়টার ওপর স্থির হয়ে আছে। আর একটু পরে বাউন্ডারি লাইন ছুঁয়ে হারিয়ে গেলেই স্বর্গের আম্পায়ার দুটো হাত তুলে যেখানে যত ঠাণ্ডা বাতাস জমে ছিল সবাইকে ডেকে নেবে পাহাড়ের মধ্যে। তখন আর এত নিশ্চিন্তে হাঁটা চলবে না। ব্যাগে একখান শার্ট আছে বটে, কিন্তু একবার সূর্য ডুবলে পাহাড়ে এমন বখাটে একটা ঠাণ্ডা পড়ে, যে তখন মনটা খালি কম্বল কম্বল করে ওঠে।
অথচ আজ সারাদিন কী রোদটাই না ছিল। ডাবল ডেকার ব্রিজ দেখার বড়ো ভিড়টা আসে বর্ষাকালে। সেটাই আসল বুদ্ধিমানের কাজ। তখন ঝরনা নদী সব ফুলে-ফেঁপে থাকে। গাছের প্রত্যেকটা পাতা এমন সবুজ হয়ে থাকে, যে তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে আমাদের মতো ছিটেলদের খালি মনে হয় একটু অসাবধান হলেই জামাকাপড়ে ক্লোরোফিল লেগে যাবে।
তখন মেঘ-টেঘও থাকে বিস্তর, তার জায়গায় এখন হল প্রায় খরার সময়। নদী বা ঝরনায় যা জল আছে— পরান যায় জ্বলিয়া রে দেখে আমারা তার থেকে অনেক বেশি কেঁদেছিলাম।
গাছপালায়ও আর সেই তেজ নেই। সমস্ত ঘাস এমা ওয়াটসনের চুলের মতো সোনার রং নিয়ে বাতাসে দোল খায়। অনেকে হাসবে। কিন্তু সত্যি কথা হল গ্রীষ্মকালের মৌশিরানেরও একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। ঝাঁকড়া ডালের ন্যাড়া ন্যাড়া গাছের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় নীল আকাশের দিকে তাকালে যে মারকাটারি আলপনাগুলো তৈরি হয় সেসব এই জন্মে এঁকে উঠতে পারব বলে তো মনে হয় না। আর তুলোর গাছ যে এ-রাস্তায় কত সেসব গুনে আর শেষ করা যাবে না। আমি তো জাত চিনি না, তবে শিমুল হয়তো এখানে নেই। তাই কোনো গাছেই সেভাবে আগুন ধরেনি। শুধু যাদের ফল ফেটে গেছে, সেখান থেকে হাওয়া হাওয়ায় তুলোর ফুল ভেসে উঠে সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ছে। বুকে এইটুকুনি একটা করে বীজ। এসব দেখলে তাও ভরসা হয়। প্রকৃতির নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার যতরকম কায়দা আছে, মানুষ হয়তো সবাই মিলে ভেবেও ধ্বংস করার অত রকমের বদবুদ্ধি বের করতে পারবে না।
তবে এখানে বনেরও মোটা সরু আছে। মাঝে মাঝেই এর তার বাড়ির উঠোন এসে পড়ে। আমরা আমাদের বেস্ট হিন্দিতে জিজ্ঞেস করি, “ডাবল ডেকার ব্রিজ ইধারই হে না”। স্প্রিং লাগান পুতুলের মতো মাথা নাড়ে সবাই। অন্য সময় না কি এখানে মেঘ এসে গায়ে ধাক্কা মারে। ছবিতে দেখেই বলে সবাই। আসলে তো আর তা হয় না। মেঘ কাছে এলে কুয়াশার সাথে তার আর ফারাক থাকে না তেমন। গায়ে একটু ভেজা ভেজা ঠেকে, এই যা। এখন খটখটে শুকনো সময়। মেঘ তো পাই না। কিন্তু দেখি হাওয়া দিলেই কী সুন্দর সব হলদে, লাল, গেরুয়া রঙের পাতা বাতাসের গায়ে গড়াতে গড়াতে নীচে নামে। মাটিতে পড়ার আগে খপ করে ধরে ফেলতে পারলে সেই পাতার নাকি অনেকরকম গুণ থাকে। অনু মেয়েটার বোধহয় একটা নিজের দুনিয়া আছে। নিজেও সব সময় বোঝে না, কিন্তু মাঝে মাঝে সেখানে চলে যায়। আমাকে একবার লাল টকটকে একটা পাতা ধরে দিয়েছিল। সে-পাতায় গাছের খানিকটা মন খারাপ লেগেছিল তখনও। আমি কানের পাশের চুলে গুঁজে রেখেছিলাম।
ট্রেকিং-এর মধ্যে কী একটা কারণে অনু আমাদের সবার ওপরেই প্রচণ্ড রেগে গেল। তখন কাউকে কিছু বলতে না পেরে, আমারই কান থেকে পাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে, সামনের নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। কার পৃথিবীতে কখন যে কী হয়ে যায়। এখানে এত প্রজাপতি। তাদের ডানায় না জানি কোথায় ঝড় উঠে আবার থেমেও যায়। অনেকক্ষণ পর আমাকে আবার আরেকটা লাল পাতা কুড়িয়ে দিয়ে সরি বলেছিল। এই পাতাটা দেখতে আরও সুন্দর। কানেই গুঁজে রেখেছিলাম। তারপর সাঁতার কাটতে গিয়ে হারিয়ে গেছিল কোথাও।
তখন তো বুঝিনি। পরে স্যাটেলাইট ম্যাপে দেখেছি, আসলে একটা নদীই অনেকগুলো বাঁক নিয়ে বার বার আমাদের রাস্তায় বাধা দিয়ে বয়ে গেছে। পথের মধ্যে শেষ এত নদী পেয়েছিলাম ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারে। সে ছিল বর্ষার সময়, সব নদী ঝরনা মহা আনন্দে নিজেদের নিয়ে নাচানাচি করছিল। এখানে কান্নার মতো শব্দ হয় জলের। স্রোত নেই বলেই সবখানে টলমলে জল। দেখলেই পা ডুবিয়ে বসতে ইচ্ছে করে।
ফেরার সময় ড্রাইভার কাকু বলেছিলেন, ডাবল ডেকারে যাওয়ার সিঁড়ি আসলে সাড়ে তিন হাজার। মানে আসা-যাওয়া মিলিয়ে সাত হাজারের একটু বেশিই হবে। কারণ আমরা সোজা রাস্তায় তো আর হাঁটিনি। বলছি না গরমকালেরও বেশ অনেক মজা আছে। জল যেমন কম বইছে, তেমনি যেটুকু নূপুরের শব্দ তুলে আসছে, তা একেবারে কাচের বুদ্বুদের মতো স্বচ্ছ। গাছের একটা পাতা ভেসে গেলেও তার দ্বিগুণ বড়ো ছায়া জলের নীচের পাথরের ওপর সরে সরে যায়।
আমরা শ্যাওলা ধরা পুকুর আর হুগলির গঙ্গা দেখা লোকজন। এসব দেখে আদেখলামো করব সেটাই তো নিয়ম। এখন লিখতে গিয়ে খেয়াল হচ্ছে, সেদিন ক্লান্তির অন্তত ১৫% শক্তি আমার খরচ হয়েছিল জুতো খোলা আর শক্ত করে ফিতে বাঁধার জন্য। যেখানে পেরেছি পা ডুবিয়ে বসে পড়েছি। নেমেওছি জলে। পায়ের নীচের প্রায় প্রতিটা পাথরই প্রচণ্ড পেছল, খুব পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। হাঁটু অবধি সবার ভিজে গেছে, তবু স্নান করতে পারছি না বলে আমাদের সে কী আফশোস। সোম সবজায়গাতেই পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে একটা করে কেয়ার্ন বানিয়ে এসেছে। ও তো আর অত নিয়ম জানে না। তাই পাথরের ওপর পাথর সাজানো হয়ে গেলে সেটাকে আবার ছোটো পাথর দিয়ে হাফ সার্কেল বানিয়ে ঘিরে রাখে। তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে কীসব যে বলে! ভগাদার বেশ মজার জীবন। দুনিয়াশুদ্ধু লোকের মনের কথাগুলো আড়ি পেতে শুনে নিয়ে, দিব্যি ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।
তবে ওর প্রার্থনাতেই কি না কে জানে— আমাদের একটা ইচ্ছে বেশ সাথেসাথেই পূরণ হয়ে গেল।
এক জায়গায় মেন রাস্তা থেকে সাইনবোর্ড দেখিয়ে আমাদের অনেকটা নীচে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সাঁতারের জামাকাপড় পাওয়া যায়, তাই দেখে কী যে আনন্দ হল। ওখানকার ভাইয়াকে কত করে রিকোয়েস্ট করলাম— যদি লাইভ জ্যাকেট ছাড়াই জলে নামা যায়। কিছুতেই সে রাজি হল না। তার না কি নিয়ম নেই।
আমার মতো ভুলভাল কনফিডেন্স ওয়ালা লোকের জন্যই বোধহয় এইসব নিয়ম তৈরি হয়েছে। জলে নেমেই খুব খানিক জল খেয়ে ফেললাম। সেই পাঁচ বছর আগে শেষ সাঁতার কেটেছি। এতদিন পর মনে থাকে নাকি! দম ধরে রেখে কী করে ধীরে ধীরে তা ছাড়তে হয় সেই টেকনিকটাই গোটাটা ভুলে মেরে দিয়েছি। চিতসাঁতারটা তাও আয়ত্তে আছে দেখলাম। তাতে সুন্দর আকাশ, পাখি, প্রজাপতি দেখতে দেখতে ভেসে থাকা যায়। শুধু কোনদিকে যাচ্ছি সে দেখার উপায় থাকে না। দুমদাম ধাক্কা লেগে যায়। সত্যিকারের সুইমিং পুল তো আর নয়। এখানে-ওখানে পাথর উঠে থাকে। কতবার যে হাঁটু ছড়ে গেল। যখন জল কেটে এগিয়ে যাই, নীচের প্রতিটা পাথরে আমার ছায়া ইয়া বড়ো হয়ে পড়ে। সেখানে কোথাও একফোঁটা আগাছা নেই। আর কী যে নীল জল! দূর থেকে স্থির মনে হলেও, আসলে কিন্তু জলে স্রোত আছে। বিশাল বড়ো একখানা জামবাটির মতো জায়গা। একদিকে ঝরনা, আর অন্যদিকে জল উপচে পড়ে নদী হয়ে নীচের দিকে বয়ে যায়। ওদিকটা যাওয়া বারণ। আর এখানে ঝরনা দিকে এগোতে গেলেই বুকে একটা ঠেলা লাগে। অভ্যাস তো আর নেই, অতটা গিয়ে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ঝরনার দিকের পাথর এমনই খাড়া, যে ধরে দাঁড়াবার জায়গা অবধি নেই। কোনোরকমে একটা ফাটলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছিলাম।
আমি একটু উঁচুদরের সাহিত্যিক হলে এইখানটার একটা সুন্দর বর্ণনা দেওয়া যেত। কিন্তু ভগাদা আমাকে সুন্দর সুন্দর সব জিনিস দেখান বটে, কিন্তু সেসব যে আঁকা বা লেখায় ধরে রাখব সে ক্ষমতা কোনোদিন দেননি। এখানে জলের এমন ঢেউ, যে তার চোটেই মাঝে মাঝে খাবি খেতে হচ্ছে। সে-অবস্থাতেই দেখলাম ওপর থেকে নেমে আসা জলের মধ্যে থেকে রঙের একটা স্রোত এসে মিশেছে সামনের নীল জলে। চোখের এত কাছ থেকে এমন স্পষ্ট রামধনু আমি কোনোদিন দেখিনি। খানিকটা এগিয়ে গেলেই সে আবার মিলিয়ে যায়, আবার দু-পা পিছিয়ে এলেই প্রায় চোখের সামনেই তৈরি হয় রঙের খেলা। কতক্ষণ যে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম সেসব। এই জায়গাটার অনেকটা ওপর দিয়ে একটা লোহার ব্রিজ দিয়ে নদীটা পেরিয়ে অন্যদিকে যাওয়া যায়। সব ছেড়ে যখন জাস্ট জলের ওপর চুপচাপ ভেসে যাচ্ছিলাম, তখন ব্রিজটা দেখলেই মনে হচ্ছিল ইস ওখান থেকে যদি কেউ একটা ছবি তুলে দিত!
তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমরা জলের মধ্যে কত কী যে করলাম! একবার করে নিজেদের মধ্যে দেখা হচ্ছে, আর হাসতে হাসতে বলাবলি করছি আজ আর ডাবল ডেকার ব্রিজ অবধি যাওয়া হবে না। বলেই আরও হাসছি। কারোর মধ্যে কোনো আফশোস নেই। অমন সেতু পরেও দেখা যাবে, তাই বলে এতখানি আনন্দ হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে চলে যাব নাকি! জলের ভেতর যখন প্যাডেল করে সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলাম, তখন নিজের পাগুলো কী যে ফরসা লাগছিল। খুব ইচ্ছা করছিল ডুবে গিয়ে নীচের পাথরের ওপর একবার দাঁড়াই, লাইফ জ্যাকেটের জন্য সে উপায় তো আর নেই। তবে অনেক হাত পা ছুড়ে ঝরনা অবধি পৌঁছিয়েছিলাম শেষমেষ। এবার ডানদিক দিয়ে গেছিলাম। ওদিকেও দেখি ইয়া বড়ো একটা রামধনু। খুব কাছে এগিয়ে গেলেই হুস করে মিলিয়ে যায়। আবার ওখানে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা খানিক পিছনে আনলে প্রায় আমার নাক ছুঁয়েই তৈরি হয় সেটা। যে বিশাল পাথরটার ওপর জল এসে আছড়ে পড়ছিল, সেটাতেই উঠে থেবড়ে বসলাম খানিকক্ষণ। খুব বেশি বসার উপায় নেই, পিঠে প্রায় কিল ঘুষির মতো জল এসে আছড়ে পড়ে। আরেকটু বসে থাকলেই বোধহয় কাঁধে, পিঠে কালশিটে ফেলে দিত। বাকিদের মধ্যে সোমই দেখলাম একমাত্র সাঁতার জানে। আমার চেয়েও ভালো জানে আসলে। ঝরনার তলায় গিয়ে তার সে কী আনন্দ, হু-হু করে চিৎকার করছে। রাজ জলে ভয় পেলেও আমাদের ভরসায় গোটাটাই গেছিল ও। তবে অনুকে কিছুতেই আনা যায়নি। খানিক নেমেই উঠে গেছিল। তারপর গবদা লাইফ জ্যাকেটটা পরেই পাথরের ওপর বাকি মেয়েদের সাথেই বসে থাকল সারাক্ষণ।
মেয়েদের মধ্যে দেখলাম শুধু আমাদের দলের দু-জনই নেমেছে। বাকিদের বর জলে নেমে হাবুডুবু খেলেও তারা দিব্যি পাড়ে বসে ছবি তুলে যাচ্ছে।
একজনের বয়ফ্রেন্ডকে তো আমিই হাতে ধরে ঝরনা অবধি নিয়ে গেছিলাম, নইলে সে বেচারা পাড় থেকে একটু এগিয়েই একপেট জল খেয়ে আবার ফিরে আসছিল। পরে ট্রেকের সময় আমার হাত-ঠাত জড়িয়ে অনেক থ্যাঙ্কিউ বলেছিল, তখনই জেনেছিলাম ওরা দু-জনেই মুম্বাইতে চাকরি করে, থাকেও ওখানে। শুনে বেশ হেসেছিলাম।
বাংলার মেয়েরা গেছোপনায় বাকিদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে।
ফাইনালি আমরা যখন জল ছেড়ে উঠলাম, সূর্য তখন একদিকে হেলে পড়েছে। রোদের আর সেই ‘তোমরা আমায় রক্ত দাও’ গোছের তেজটা বেঁচে নেই।
আমরাও এবার বেশ পা চালিয়েই হাঁটছিলাম। পথে এবার আরেকটা গ্রাম পড়ল। কী যে শান্ত সব ঘরবাড়ি, নিঝুম দোকানপাট। দোকান যা আছে টুরিস্টদের জন্য, নিজেদের জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে জীবন কাটায় ওরা। খুব বেশি মানুষকে বাইরে দেখিনি, যারা ছিলেন গায়ে নরম রোদ পড়ে কী যে সুন্দর দেখাচ্ছিল তাদের। পথে কিছু থাক বা না-থাক, আমি সবসময় খুব সতর্ক হয়ে হাঁটি। তাই গাছের খুব সরু একটা ডালকে সিঁড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। ওটা আসলে একটা পোকা, এত চমৎকার ক্যামোফ্লাজ করে নিজের শরীরটাকে কাঠির মতো বানিয়ে নিয়েছে, যে নড়াচড়া না করলে ওকে শুকনো ডালপালার স্তূপের থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব।
ডাবল ডেকার ব্রিজের কথা একটু তাড়াহুড়ো করেই বলব। কারণ জায়গাটা মোটেই আমাদের তেমন পছন্দ হয়নি। তার আগে এরচেয়েও সুন্দর একটা জায়গায় আমরা সারা সকালটা কাটিয়েছিলাম। তবু সেটা বলার আগে, এদিকটা একেবারে শেষ করেনি।
ছবিতে যেমন জংলি ভাব দেখাই সবাই, জায়গাটা আদৌ অমন না। পাহাড়দুটো অনেকখানি এগিয়ে এসে এমনিতেই নদী খাতটা অনেকটা সরু করে ফেলেছে। তার ওপর আবার একটা বিচ্ছিরি দেখতে ম্যাগির দোকান আর একগাদা টুরিস্ট মিলে জায়গাটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে।
নীচে জল যাবার যে জায়গা, কেন কে জানে সেটাকেও খুব ঘটা করে সিঁড়ির মতো করে বাঁধানো হয়েছে। যেখানে জল একটু স্থির, সেখানে সব ইয়া বড়ো বড়ো মাছ। এও যে নীচ থেকে এনে ছাড়া হয়েছে, বোঝা যায়। দোতলা সেতুদুটোও ঠিক একজ্যাক্ট একটার মাথায় আরেকটা না। কাছে গেলে বোঝা যায় বেশ খানিকটা গ্যাপ আছে। শক্তপোক্ত পা হলে অনায়াসে দোতলারটা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচেরটায় নেমে আসা যায়।
আমরা যখন পৌঁছলাম জায়গাটায় বেশ ভালো ছায়া পড়ে গেছিল। প্রায় সবাই রওনা দেওয়ার জন্য একে একে উঠে পড়ছে। আমাদের মাথায় তখনও ধান্দা ঘুরছে, সবাই একটু এগিয়ে গেলে তারপর নিরিবিলিতে হেঁটে ফিরব। সে খানিক অন্ধকার হলে হবে।
কলেজের বড়ো দলের সাথে এসে একটা মেয়ে কীভাবে যেন সবার থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল। তার শরীর খানিক ভারী। তাই বোধহয় বেচারি বাকিদের সাথে তাল রাখতে পারেনি। আজকালকার ব্রোকোডগুলো কেমন জানি একটা হয়ে গেছে! মনমরা দেখে অণুই বোধহয় নিজে থেকে গিয়ে কথা বলেছিল। আমাদের সাথে ফেরার জন্য নেমন্তন্নও করেছিল। কিন্তু সে বন্ধুদের জন্য একটু অপেক্ষা না করে কিছুতেই নামবে না। আর ওদিকে বাঁদরগুলো নাকি একে ফেলেই চলে গেছে!
আমরা আর খুব বেশিক্ষণ ওখানে থাকিনি। ফেরার রাস্তাও তো আর কম না। রেনবো ফলস অবধি আর যাওয়া হল না। তবু সবার মন তো কানায় কানায় ভরে আছে। সোমই প্রথম বলল, সিঙ্গেল লিভিং রুট ব্রিজটার মতো সুন্দর জায়গা এখানে আর একটাও নেই। তাতে আমরা সবাই চিৎকার করে ডিটো দিলাম।
নীচের ওই নদী খাতটা পেরোনোরও অনেকটা আগে জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিলাম আমরা। সেটা নাকি পৃথিবীর সব থেকে লম্বা লিভিং রুট ব্রিজ। বাইরের কথা জানি না, কিন্তু মেঘালয়তে বহু জায়গায় এরকম মানুষ আর প্রকৃতির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বানানো ব্রিজ আছে। সেসব ভারী শক্তপোক্ত হলেও, হাঁটলে প্রচণ্ড দোল খায়। দাঁড়িয়ে বারান্দা বিলাস করার উপায় নেই কোথাও। এরকম বুদ্ধি মানুষ কোথা থেকে পেয়েছিল কে জানে। এখন কেটে ফেললেও আমার মনে হয়, তখন নদীর দুই পারেই লাইন দিয়ে প্রচুর রবার গাছ ছিল। তাদের মধ্যে থেকেই সমান্তরাল দুইখানা বেছে নিয়ে তাদের মধ্যেখানে বাঁশ রেখে তার ওপর গাছদুটোর শেকড় খানিকটা করে জড়িয়ে দেওয়া হয়। সময়ের সাথে দু-দিকের শেকড় বেড়ে যখন কাছাকাছি আসে, তখন একটার সাথে আরেকটা জড়িয়ে দিয়ে ব্রিজের ভিত তৈরি হয়। তারপর যত দিন যায়, সেইসব শেকড়, আরও বড়ো ব্রিজটাকে একেবারে মানুষের হাঁটার মতো করে পোক্ত করে গড়ে তোলে।
আমরা যেখানে পৌঁছলাম সেখানে একটা ব্রিজ এখনও তৈরি হচ্ছে। আরেকটায় উঠলে, মানুষের গোটা পৃথিবীতেই কেমন জানি একটা বদল আসে।
ভালোবেসে সুখে থাকা মানুষের মতো একটা নদী, পায়ের কাছ দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বয়ে যায়। অণুর এত খাড়াই বেয়ে নামতে ভয় লাগে। তাই আমরা বাকিরাই নদী পেরিয়ে পাথরের গায়ে পা ঝুলিয়ে বসলাম। ওপরে কেষ্ট ঠাকুরের গায়ের মতো নীচ আকাশ। নীচে রবার গাছের ছাউনি। যে-চারটে গাছের শেকড় দিয়ে ব্রিজদুটো তৈরি হয়েছে, তাদের মাথাগুলো গোল হয়ে এগিয়ে এসে ছেদবিন্দুর খানিকটা আগে কী ভেবে যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। সেখানকার আকাশ দীঘির মতো স্বচ্ছ। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই একটা সাদা মেঘের ছানা এসে থমকে দাঁড়াল সেখানে। এসবের তো আর ছবি হয় না। মাথার মধ্যেই-বা কতদিন থাকবে কে জানে!
প্রজাপতির কথা আলাদা করে আর কী বলি! কত যে তাদের রং, মানুষকে একটুও ভয় পায় না। তবে দেখতে ভালো হলে কী হবে, যত লোভ নোংরা জিনিসের ওপর। একটু দূরে যেখানে জুতো মোজা ছেড়ে এসেছিলাম, সেখানে দেখতে দেখতে প্রজাপতি আর মথের মেলা বসে গেল। নকশা দেখে তো আর ছেলে-মেয়ে আলাদা করতে পারি না। কিন্তু যখনই একইরকম দেখতে দু-জন সামনাসামনি হয়, তখনই দু-জন দু-জনকে ঘিরে খুব একপ্রস্থ নেচে নেয়। তারপর আবার যে-যার রাস্তায়।
এরা তো তাও ডাঙার ওপরে। নীচের ওইটুকু জলেও কতরকম মাছ যে ঘর বানিয়ে আছে! হাতের আঙুলের মতো সাইজ। তারা সবাই মস্ত বীরপুরুষ। জলের মধ্যে পা ডোবালেই ঝাঁকে এসে ময়লা খায়। দাঁত তো নেই কারোর, তাই কামড়ালে ভীষণ কাতুকুতু লাগে। শুনেছি কোনো কোনো স্পা পার্লারে না কি এরকম মাছের অ্যাকোয়ারিয়ামে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে হয়। তার গলাকাটা দামও হয় নিশ্চয়।
আমি খুব আরাম পেলে বেশিক্ষণ আর বসে থাকতে পারি না। তা ছাড়া এখানে পিঠের দিকের পাথরটা ঢালু হয়ে এসে এমন চমৎকার ডেকচেয়ারের মতো আকার নিয়েছে, যে খানিক শুয়ে না নিলে নিজেরই পরে মনখারাপ করবে। সঙ্গে ঝিঁঝি আর গুবরে পোকাদের বাজনা তো রইলই। স্বর্গে এরচেয়ে বেশি আর কী থাকে কে জানে!
জায়গাটা নিয়ে এত যে লিখছি, তার কারণ এর অনেকখানি আমি মনের মধ্যে চুরি করে এনেছি। তার স্থানমাহাত্ম বলে আলাদা করে কিছুই নেই। তবু এবার থেকে ময়ূরাক্ষী পড়লে এই নদীটাকেই দেখতে পাব বারবার। তার কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যাবে। আমাদের জামরুল গাছের মাথায় বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে থাকবে একটুকরো সাদা মেঘ। হায়রে জীবন। বড়ো ভালোবাসি তোমায়।
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।