একটি চেয়ার যাকে ঘিরে আবর্তিত হয় ছবির বয়ান, পুরুষ ও নারীবিশ্ব আর সেই বিশ্বের অনেক জটিল আর্থ-সামাজিক স্তর।
“O Prince, O Chief of many throned Powers, that led the Embattled Seraphim to War” —Paradise Lost, John Milton
সম্প্রতি নারীবিশ্বের একটা ভরকেন্দ্র তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ভারতীয় সিনেমায়। এমন নয়, যে ভারতে নারীকেন্দ্রিক সিনেমা অতীতে হয়নি। মূল ধারার বাংলা ছবি উত্তরফাল্গুনী, সাত পাকে বাঁধার সাথে উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে তালিকায় উঠে আসবে চারুলতা, মহানগর বা শ্যাম বেনেগালের ভূমিকার নাম। হয়তো মনি কাউলের উসকি রোটিও আসবে। আসবে ১৯৫৭ সালে নির্মিত মেহবুব খানের মাদার ইন্ডিয়া। এই উদাহরণগুলো উল্লেখ করার সময় আমরা খেয়াল রাখব, নারীকেন্দ্রিক আর নারীবৈশ্বিক ছবির মধ্যেকার পার্থক্যটুকু। অতীতের নারীকেন্দ্রিক যে সিনেমার তালিকা এখানে দেওয়া হল, সেগুলোতে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রকে বোনা হচ্ছিল প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে রেখে। পুরুষ দর্শনের স্পেসটিকে বিনির্মান করে নারীর নিজস্ব ভুবন রচনা হয়নি তখন। এই প্রসঙ্গে আমরা ফিরে যেতে পারি, সম্প্রতি হলবার্গ পুরষ্কার প্রাপ্ত মানববিদ্যার ভাবুক, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের একটি উক্তির কাছে। এই উক্তি তার বই, “Feminism and Critical theory“ সম্পর্কে তিনি করেছিলেন ১৯৭৮ সালে।
“My own definition as a woman is very simple: it rests on the word man as used in the texts that provide the foundation for the corner of the literary critical establishment that I inhabit. You might say at this point, defining the word woman as resting on the word man is a reactionary position. Should I not carve out an independent definition for myself as a woman?”
এই প্রশ্নের সাথে কীভাবে জড়িয়ে থাকে এক দ্বান্দ্বিকতা, ‘Man’ শব্দের এক ঐতিহাসিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে, কীভাবে জড়িয়ে থাকে Power Domination, এই শব্দের semantics-কে একই সাথে মান্যতা দিয়ে এবং চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, তার বিস্তারে আমরা যাব না। কিন্তু, সাম্প্রতিক সিনেমার নারীভুবন আর নারীর দৃষ্টিকোণের কথা উল্লেখ করা থাক, যা অতীতের নারীকেন্দ্রিক সিনেমার থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখে। এর বীজ অবশ্য ছিল ষাটের দশকে তৈরি চারুলতাতেও। অপেরা গ্লাস ছিল চারুর দৃষ্টিকোণের দ্যোতক। আমরা লক্ষ করেছি, কীভাবে চারুর অপেরাগ্লাস এক দূরের প্রেক্ষণী রচনা করেছে দুটি পুরুষের জন্যে। দুটি আলাদা মুহূর্তে ভুপতি আর অমল, দুজনেরই জন্যে। ট্রাজেডির মতো এই দুই পুরুষই হয়ে ওঠে তার ‘অপর বিশ্ব’। একটি বিশ্ব দূরায়ত এবং অপরটি কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু দুটি বিশ্বই তার নিজের নারী বিশ্বে বাহিরি হয়ে থেকে যায়। মেলে না। উল্লেখ থাক, মৃণাল সেনের পদাতিক ছবির কথাও। যেখানে মৃণাল বামপন্থকে প্রশ্ন করেন, এবং সমান্তরালে রাখেন এক জায়মান নারীবিশ্বকে। এতটাই, যে একটি আলাদা দৃশ্য রচনা করেন, প্রায় ডকুমেন্টেশনের মতো করে, যেখানে সুচিত্রা মিত্র, গীতা মুখার্জি প্রমুখ ব্যাক্তিত্ব তাদের নিজেদের নারীবিশ্বকে বক্তব্যে ধরে রাখেন। অধিকার, ক্ষমতা আর বিপ্লবের স্পেসে তৈরি করতে চান নারীর ভুবন।
অপেরা গ্লাসে চারুর দূরায়ত অপরবিশ্ব ভূপতি
অপেরা গ্লাসে চারুর কাঙ্ক্ষিত অপরবিশ্ব অমল
পদাতিক ছবিতে সুচিত্রা মিত্র আর গীতা মুখার্জির কথনে অধিকার, ক্ষমতা ও নারীবিশ্ব
উপরের কথাগুলো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল, সম্প্রতি বাংলা চলচ্চিত্র মনপতঙ্গ দেখার পর।
এই ছবির শুরুতেই থাকে পর্দা জোড়া দুটি জড়িয়ে থাকা হাত। পুরুষ ও নারীর। বিগ ক্লোজ আপ! বন্ধুত্বের, পারস্পরিক নির্ভরতার, অনিশ্চয়তা আর ভালোবাসার দুটি হাত। দুটি ছেলে ও মেয়েকে একই অবস্থানে রাখা হল। দুজনে মিলে একই স্পেস করে নিচ্ছে। জড়িয়ে থাকা দুই হাতের ওপারে, যানবাহন গর্জিত নগর কোলকাতা। গাড়ির যাওয়া আসা। সিগনাল নেই। কেটে গেল প্রায় এক মিনিট। এইরকম কম্পোজিশনের একটি শুরু, যার মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উৎকণ্ঠা, অপেক্ষা আর অনিশ্চয়তা। যার মধ্যে ধরা থাকছে, এক নারীর স্পেস, পুরুষের ঠিক পাশাপাশি। এই শুরুটুকু, গায়ত্রী স্পিভাক কথিত ‘women’-এর সংজ্ঞাকে মনে পড়িয়ে দিতে পারে। একটু পরেই দৃষ্টিকোণ বদলে গেল। মিড ক্লোজআপ, লং ডিস্ট্যান্স শট আর একেবারে উপর থেকে দেখা জেব্রা ক্রসিং। ব্যাস্ত শহরের, ব্যস্ত রাস্তার ধারে দাঁড়ানো দুটি অকিঞ্চিৎকর মানুষ! বুঝে ফেলা গেল, ওই দুটো হাত আসলে গ্রামের মাটির গন্ধ মাখা, প্রথম শহরের বুকে পা রাখা একটি ছেলে ও মেয়ের। আরও একটু পর জানা হয়ে যায়, ছেলেটির নাম হাসান আর মেয়েটি, লক্ষ্মী। দুজনেই গ্রাম থেকে প্রথম শহরে পা রাখছে।
রাজদীপ পাল আর শর্মিষ্ঠা মাইতির যৌথ নির্দেশনার দ্বিতীয় ছবি মনপতঙ্গ প্রথমেই নজর কেড়ে নেয় তার ক্যামেরা-চোখের অবস্থান দিয়ে। দুটি জড়িয়ে থাকা হাতের প্রতিমা, আমাদের স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে পারে দুটি সিনেমার কাছে। একটি অবশ্যই অপু-দুর্গার হাত। অন্যটি গ্রিক পরিচালক থিওডোর এঞ্জেলোপৌলোসের “land scape in the mist”-ছবির Voula আর Alexandros এর হাতের কাছে। কিন্তু ওই দুটি ছবিতেই জড়িয়ে থাকা হাত ছিল ভাই বোনের। মনপতঙ্গ ছবির হাত সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত দুটি ছেলে-মেয়ের, যারা একে অপরের কাছে ভিন্ন ধর্মের, কিন্তু গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে বাধ্য হয়েছে ঘর বাঁধবে বলে। কিন্তু তাদের গ্রাম কোথাকার? এপার বাংলা, না ওপার বাংলার? এই সন্দেহকে উসকে দিয়ে, শুরু থেকে শেষ অবধি, ছবিটা একটা টানটান গল্পই বলে। কিন্তু ক্যামেরার যে চোখ গল্পের ন্যারেটিভ তৈরি করে, সেটি রাখা থাকে ফুটপাথবাসী কিছু প্রান্তিক মানুষের ঘর সংসারের দিকে। মনপতঙ্গ পথের মানুষদের গল্প বলে। কিন্তু ফর্মের দিক থেকে এটি পথ ভাঙার ছবি হয়ে ওঠে মূলত ক্যামেরার অবস্থানের বদল দিয়ে। অথচ এই বয়ানভঙ্গীর মধ্যে অনিবার্য একটা দ্বন্দ্ব আছে। যেহেতু মনপতঙ্গ হল এইরকম একটি সিনেমা, যার আবেদন কাজ করে যায় অনেকগুলো স্তরে, বুদ্ধি আর বোধের স্তরেও, এটির টার্গেট দর্শক হয় মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। ফলত, ক্যামেরার দৃষ্টির বদল ঘটালেও, ছবিটির ন্যারেটিভে প্রচ্ছন্ন রাখতেই হয় “Civility”। পরিচালক দ্বয়, এই দুই প্রান্তকে মেলানোর দুরূহ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছেন, এটা বলতেই হয়। এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় মৃণাল সেনের উক্তি, যা তিনি পথের পাঁচালী সম্পর্কে একাধিক বার করেছিলেন। পথের পাঁচালী আদ্যন্ত গ্রামের ছবি। কিন্তু যে-চোখ সেই গ্রাম কে দেখেছে, তার স্পেস রচনা করেছে, সেই চোখ Civil. তাই পথের পাঁচালী গ্রামের ছবি হয়েও 'গ্রাম্য’ নয়। পথের পাঁচালীর Civility প্রকাশ পেয়েছিল, শুধুমাত্র বিন্যাস, চিত্রপ্রতিমা আর অভিনয় স্টাইলেই নয়। রায় পরিবারের মুখের ভাষাতেও। একটা দ্বান্দ্বিক প্রতর্ক তৈরি হয়েছিল এই প্রশ্ন দিয়ে, যে ওদের মুখের ভাষা ঠিক কোন অঞ্চলের? একটি রিয়ালিস্ট সিনেমার মুখের ভাষা কি রিয়াল? বিভূতিভূষণের বর্ণনা অনুসারে হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষ বীরু রায় যশড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মানুষ। শ্রীপুর, টাকির উল্লেখও আছে। কিন্তু হরিহর পরিবারের কথ্য ভাষায় ওই অঞ্চলের ভাষার মিল সামান্যই। ওদের ভাষায় শহর কোলকাতার কথ্য বাংলার মিল স্পষ্ট। এটা থেকে বোঝা যায়, পথের পাঁচালীর সংলাপের ভাষায়, পরিচালক ভৌগোলিক যাথার্থ্যের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁর শিল্পের সংবহনের দিকে। এই ভাষা সচেতনে নির্মাণ করা হয়েছিল, অথচ দর্শকের কানে তা কৃত্রিম মনে হয়নি। শিল্পের বাস্তব তাই যাপন বাস্তবের হুবহু অনুকরণ হয়নি। এটা উল্লেখ করা হল, কারণ, মনপতঙ্গ ছবির ফুটপাথবাসী চরিত্ররা যে ভাষায় কথা বলে, সেটিও এক নির্মাণ করা ভাষা।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
হাসান আর লক্ষ্মী কোলকাতায় পা রাখার একটু পরেই মুখোমুখি হয় একটা ফার্নিচারের দোকানে রাখা লাল রঙের একটা সোফার সাথে। ওদের বিস্ময় আর স্বপ্ন শুরু হয় এখান থেকেই। আর ঠিক এখান থেকেই, গোটা ছবিতে চেয়ার, তার ভিন্ন ভিন্ন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ফিরে ফিরে আসে মেটাফরের মতো। চেয়ার হয়ে ওঠে স্বপ্ন, শক্তি আর ক্ষমতার প্রতিমা। কখনো সেই চেয়ার হাসান আর লক্ষ্মীর যৌথ স্বপ্ন। কখনো তা লক্ষ্মী অথবা রুমির একক নারী কামনার দাবি। কখনো সেটি একজন পেইন্টার অমিতাভর (অভিনয়ে জয় সেনগুপ্ত) ক্যানভাসে এক শক্তির প্রতীক। যে-শক্তি আসলে এক সুবিধেপ্রাপ্ত শ্রেণীর। ওই শক্তির আসনে বসে নগ্ন নারী মডেল রুমি (তন্বিষ্ঠা বিশ্বাস)। অমিতাভর শক্তির ওই একই চেয়ার হাতছানি দেয় লক্ষ্মীকেও। চেয়ার হয়ে ওঠে সীমা বিশ্বাস অভিনীত জ্যোছনা নামক মেয়েটির চায়ের দোকানের কুর্সি, যেখানে বসে, সে এপার বাংলা-ওপার বাঙলার টাকা দেওয়া নেওয়ার হাওয়ালা ব্যাবসা চালায়। এই চেয়ারই হয়ে ওঠে মনপতঙ্গ ছবির এক কেন্দ্রীয় চরিত্র, যাকে ঘিরে আবর্তিত হয় ছবির বয়ান, পুরুষ ও নারীবিশ্ব আর সেই বিশ্বের অনেক জটিল আর্থ-সামাজিক স্তর।
হাসান-লক্ষ্মীর যুগল বিশ্বের বিপ্রতীপে চেয়ারের হাতছানি। পাশে চেয়ার রক্ষক— চৌকিদার চরণদাস
লক্ষ্মী এবং জ্যোৎস্না— নারীবিশ্বে অর্থনীতির স্বপ্ন ও ক্ষমতার দুটি বিপরীত ছায়া
শহরে পা রেখে, হাসান আর লক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছিল তাদের গ্রামের বাপন দা (অমিত সাহা) আর পিংকির (অনিন্দিতা ঘোষ) ফুটপাথের সংসারে। ফার্নিচারের দোকানের লাগোয়া ফুটপাথেই তাদের ঘরসংসার।
সিনেমার বয়ান বা গল্পটা বলার দিকে এই লেখাটিকে নিয়ে যাব না। তার জন্যে সিনেমাটি দেখা দরকার। তার বদলে, আরও কিছু বিশিষ্টতার উল্লেখ করি।
মনপতঙ্গ ছবিতে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে গেছে, ফুটপাথবাসী মানুষদের প্রান্তিক জীবনের ছবি, বাংলাদেশ থেকে চলে আসা উদ্বাস্তু মন, তাদের দৈনিক যাপনে জড়িয়ে থাকা existential crisis আর পুলিশের সাথে সমঝোতা করে চলতে থাকা প্রান্তিক জীবন। লক্ষ করতে হয়, প্রান্তিক মানুষ কীভাবে প্রলুদ্ধ হয় আর যুক্ত হয়ে পড়ে সুবিধেপ্রাপ্ত শ্রেণীর দুর্নীতিচক্রে। হাসান আর লক্ষ্মীর একটি চেয়ারে বসার নিষ্কলুষ স্বপ্ন, যা উড়ানের স্বপ্নে প্রতীকি হয়ে যায়, প্রলুব্ধ করে রাস্তার কীট জীবন থেকে পতঙ্গের মতো ডানা মেলে ওড়ার দিকে, একটা metamorphosis-এর দিকে। কাফকার গল্পের একটা বিপ্রতীপ ছবি তৈরি হয় দুজনের জীবনে আর সেটির প্রায় নির্মেদ বয়ান তৈরি হয়। হাসান আর লক্ষ্মীর গল্পের সরল অথচ জটিল ন্যারেটিভের সমান্তরালে ভরে দেওয়া থাকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সাব প্লট। সেই তিনটি উপাদান হল, কীভাবে একজন আপাত লিবেরাল আর মানবিক শিল্পী, উদারতার মুখোশের আড়ালে exploit করে প্রান্তিক নারীকে। লক্ষ্মী যেমন একদিকে হয়ে ওঠে স্বাধীন, নিজের শরীরের অধিকার সে নিজেই বুঝে নেয়, অন্যদিকে সে হয়ে পড়ে শিক্ষিত শিল্পী অমিতাভর একজন Victim. না, সেই victimisation, চলতি পদ্ধতির ধর্ষণ নয়। আরও চতুর আর জটিল! সে লক্ষ্মীর ‘স্বপ্ন’ আর স্বাধীন নারীবিশ্বকে ব্যবহার করে। অমিতাভর victim শুধুমাত্র লক্ষ্মী নয়। তার শিক্ষিত আর আলোকপ্রাপ্ত মডেল উর্মিও হয়ে যায় victim। আর এইখানেই উল্লেখ করতে হয়, কীভাবে জাগ্রত নারীবিশ্বও হয়ে ওঠে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির commodity। উর্মি আর লক্ষ্মী, দুজনে দুটি আলাদা শ্রেণীর মেয়ে, অথচ কী অনিবার্যতায় তারা জুড়ে গেল একই সামাজিক ল্যাণ্ডস্কেপের পুরুষতন্ত্রে! উর্মী যখন জার্মানি যাচ্ছে, তার মধ্যে পাঠ করা যাচ্ছে লক্ষ্মীর গ্রাম থেকে শহরে আসা স্বপ্নের মানচিত্র! কিছুদিন আগে দেখা কান ফেস্টিভালে পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি All we imagine as light-এর কথা মনে পড়বে আমাদের। ওই ছবিটার পরে, মনপতঙ্গ হল দ্বিতীয় ছবি, যেখানে পুরুষের বদলে আমরা একজন নারীকে দেখি যৌনতায় লিড করতে। শায়িত পুরুষের উপরে দেখি নারীকে। যেমন সমাজ ও সমকালীন সাহিত্যে, ঠিক তেমনি সিনেমায় ক্রমশ প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে মেয়েদের অধিকার বোধের কথা। মেয়েদের নিজের শরীরের উপর তাদের নিজের অধিকারের কথা। খুব Irony মনে হয়, যখন অমিতাভ-র সংলাপে উঠে আসে মেয়েদের এই শারীরিক অধিকারের কথা।
হাসানের উপর লক্ষ্মী, নারীর আপন শরীর চেতনা ও যৌন অধিকার
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের কথা বলতেই হয়। তাকে আপাত বিচারে গৌন চরিত্র মনে হলেও, তার উপস্থিতি একটা গুরুত্বপুর্ণ বয়ান তৈরি করে। এই চরিত্রটি হল ফার্নিচারের দোকানের চৌকিদার চরনদাস (জনার্দন ঘোষ)। এই চরিত্রটি এমন এক চরিত্র, যে ক্যাটালিস্ট হয়ে ওঠে, হাসান আর লক্ষ্মীর জুড়ে থাকা হাত যার জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগিয়ে যায় একটা প্রায় ম্যাকবেথ তুল্য ট্রাজেডির দিকে। অন্যদিকে, আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি, সে সাধারণ এক চৌকিদার মাত্র নয়, সে এককালের বামপন্থী বিপ্লবী। রাতে তার গলায় ভেসে আসে মুক্তির গান। আর শেষে লেখা থাকে একটি শব্দ-‘ইনকিলাব’। অথচ এই চরণদাস একদিকে যেমন ক্ষমতার রক্ষক, নিজে একজন ক্ষমতার দাস হয়েও সে ব্যাবহার করে ওই দুটি প্রান্তিক মানুষ, হাসান আর লক্ষ্মীকে। অন্যদিকে সে নিজেও ক্ষমতার একজন victim. যাকে দেখে রাগের বদলে করুণা হয়। যার ‘ক্ষুধা’ শুধু পেটের নয়, অতৃপ্ত যৌনতারও। চরিত্রটি মনে পড়িয়ে দেবে গুপীগাইন ছবির সেই ক্ষুধার্ত কারারক্ষীটিকে, যার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নৃপতি চ্যাটার্জী।
মনপতঙ্গ ছবিটি বিশিষ্ট বলেই, একটি প্রশ্নও মনে জাগে। এই ছবির দুটি গানের মধ্যে, দ্বিতীয় গানের প্রয়োগ চলচ্চত্রীয় হলেও, প্রথম গানটি কী অনিবার্য ছিল?
অভিনয়, এই ছবির ন্যারেটিভে জড়িয়ে মিশে আছে। হাসান চরিত্রে শুভংকর মহান্ত আর লক্ষ্মী চরিত্রে বৈশাখী রায় অকৃত্রিম আর তরতাজা। একই কথা বাপন চরিত্রের অমিত সাহা আর তার বউ পিংকির চরিত্রে অনিন্দিতা ঘোষ সম্পর্কেও। জনার্দন ঘোষ আর সীমা বিশ্বাস অভিজ্ঞ অভিনেতা হিসেবেই অনবদ্য!
এই ছবির সুরকার অভিজিৎ কুণ্ড বেহালা বাদনকে বেশ কটি ভূমিকা একসাথে পালন করিয়ে নিলেন। একজন বেহালা বাদককে রোজ দেখা যায় ফার্নিচারের দোকানের সামনে একটি সোনাটা বাজাতে। বাদক যখন নেই, তখনও বেহালার এই সুরের মূর্ছনা, ফিরে ফিরে আসে, সিনেমার প্লাস্টিক ধর্মকে ব্যবহার করে ছড়িয়ে যায়, টুকরো টুকরো মুহূর্তকে জুড়ে দেয়, স্বপ্নের আবহ তৈরি করে। একইসাথে, এই বেহালা সংগীত, মনপতঙ্গ ছবিকে তার দেশজ পটভূমি পার করিয়ে ছুঁয়ে ফেলে বৈশ্বিক চিত্রভাষা। বেহালা সোনাটার এই ভাষার হাত ধরে শেষ দৃশ্যের মোচড়টিও আসে। আবারও আসে চেয়ার। আবারও আসে প্রান্তিক দুই নারী ও পুরুষের একই পেডেস্টালে দাঁড়ানো প্রতিমা। একটা জটিল ও সমকালীন আর্থসামাজিক ট্রাজেডি প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়, সমর্পিত হয় ফ্রেমবদ্ধ ক্যানভাসে।
এক গুচ্ছ ভারতীয় ছবির উড়ান লক্ষ করা যাচ্ছে, যেখানে উঠে আসছে নারীবিশ্বের বয়ান, তাদেরই দৃষ্টিকোণ থেকে। অতীতের নারীকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র পার করে যাচ্ছে তার পরিধি, হয়ে উঠছে নারীবৈশ্বিক। এই তালিকায়, মেইন্সট্রিম ছবি থাপ্পড়, পিংক বা সাম্প্রতিক OTT সিনেমা MRS-এর সাথে Alll we imagine as light, shameless, মায়ানগরের মতো অনুসন্ধানী ছবির মিছিলে জুড়ে গেল মনপতঙ্গ ছবির নাম।
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই, ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
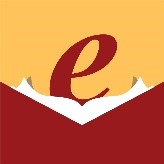

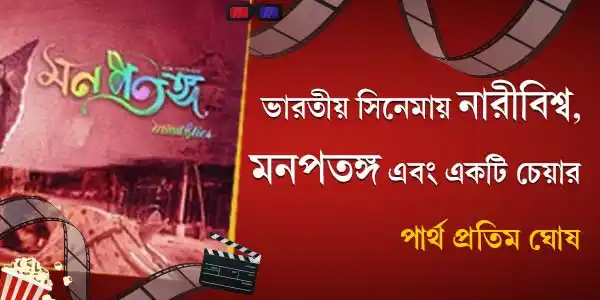
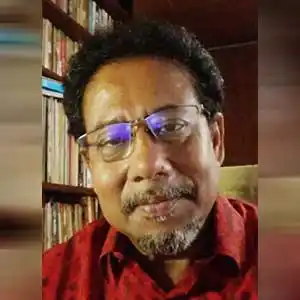









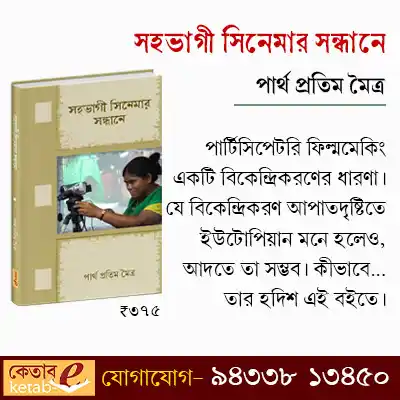
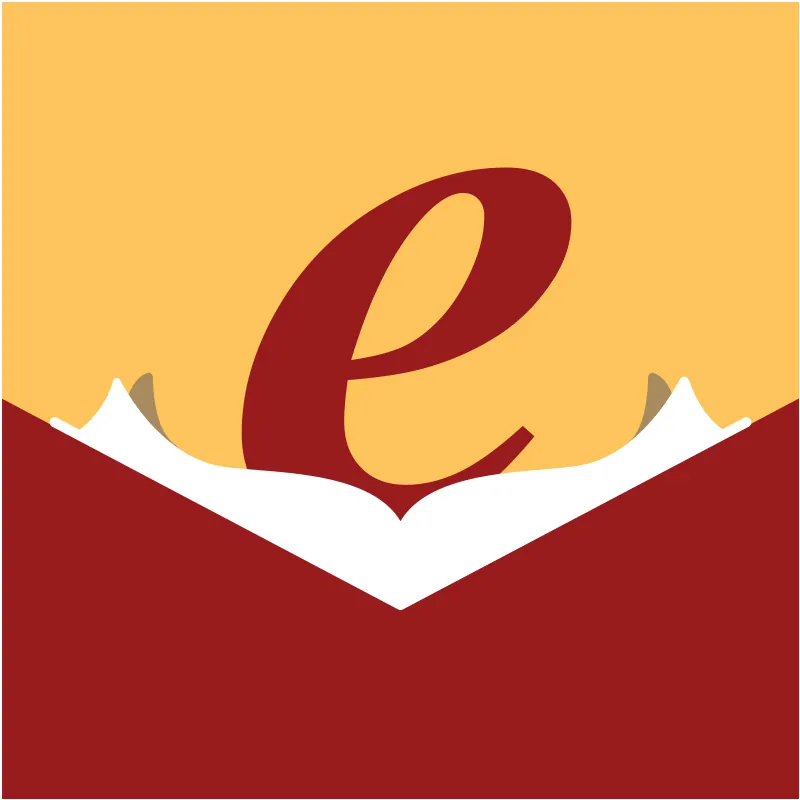
Madhumita mukhopadhyay
10 মাস আগেKhub bhalo laglo Monprotongo"chhobi r explanation korte giye ki sundar bhabe Nari sorta ke bujhiea diechhe bes kichhu past chhobir tulona kore,amader past niee porasona korte gele,Nari sorta protimuhurto uthe ase.Apner lekha pore ekebare dhonnyo.Really wonderful writing skills.
শামীম নওরোজ
10 মাস আগেখুব ভালো লাগলো