ছুটে চলেছে চন্দ্রপুরাগামী শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। স্মৃতিচারণে স্বপ্ননীল।
যে মন্থন থেকে বেরিয়ে আসবে কেন খুন হলেন বিশ্বামিত্র। এই অবকাশে, একবার বিশ্বামিত্রের চোখ দিয়ে দেখে নেওয়া যাক চৈতন্য মহাপ্রভুর বংশের কিছু ইতিহাস। যে ইতিহাস সাহায্য করবে স্বয়ং মহাপ্রভুর রহস্যাবৃত অন্তর্ধানের আবরণ উন্মোচনের ক্ষেত্রেও। যা এই উপাখ্যানের মূল প্রতিপাদ্য...
আটচল্লিশ
স্মৃতিচারণে স্বপ্ননীল।
যে মন্থন থেকে বেরিয়ে আসবে কেন খুন হলেন বিশ্বামিত্র।
ছুটে চলেছে চন্দ্রপুরাগামী শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। নিজের ভিতর এখনও মগ্ন স্বপ্ননীল।
নীল সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল বিশ্বামিত্র বাবুকে, যে উনি কী ভাবে এতটা সবিস্তারে জানলেন, তাদের পরিচয়?
প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে, মহাপ্রভু সম্পর্কে বলতে শুরু করেছিলেন মিস্টার সেন, “উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র হলেন জগন্নাথ। তাঁর আবার দুই ছেলে। বিশ্বম্ভর আর বিশ্বরূপ। বিশ্বম্ভরই পরবর্তীকালে বিশ্বের দরবারে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে খ্যাতি লাভ করেন। মহাপ্রভু বিবাহ করেছিলেন। তবে, সংসারে আবদ্ধ হননি কোনোদিন; কিন্তু...”
রত্নাকর বাবু ধরতে পারেন না ঠিক কী বলতে চাইছেন বিশ্বামিত্র।
“কিন্তু!”
“কিন্তু বিশ্বরূপ প্রথম জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও, পরবর্তী জীবনে তাঁর কী হয়েছিল, সেকথা ইতিহাসে কোথাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা নেই। কেউ কেউ বলেন তিনি সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর সল্পায়ু কাটিয়ে দিয়েছিলেন, কেউ কেউ বা আবার বলেন তিনি সংসারমুখী হয়েছিলেন।”
বিশ্বামিত্র তড়িঘড়ি করে বলে ওঠেন, “কে বলেছিলেন যে তিনি সংসারমুখী হয়েছিলেন!”
এইবার মুচকি হাসেন বিশ্বামিত্র। খুব ধীরে ধীরে বলেন, “আমি যদি এই প্রশ্ন করি, কীভাবে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি আর সংসারে ফিরে আসেননি?”
“ইতিহাস তো তাই বলছে।”
এইবার হাসি আরও চওড়া হয় বিশ্বামিত্রের, “ইতিহাস! কোথায় ইতিহাস? যা বলা হয়, সবই অনুমানের উপর ভিত্তি করে। আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন, কেউ এই কথা একশো ভাগ নিশ্চিত করে বলতে পেরেছেন, বিশ্বরূপ আবার সংসারে ফিরে আসেননি? বেশির ভাগ মানুষ বলেন উনি খুব অল্প বয়েসে দেহ রেখেছেন। সেটা... হ্যাঁ সেটা হতেই পারে,আবার নাও হতে পারে। আসলে আমরা এমন একটি অবস্থানে কখনই নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে কোনও কথা নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায়।”
একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন বিশ্বামিত্র, “কে ছিলেন এই বিশ্বরূপ? না একজন দরিদ্র পিতার সন্তান। কোনও রাজা রাজরা নন। সুতরাং এমন মানুষ কোথায়, যে লিখবেন বিশ্বরূপের ইতিহাস! নেহাত তিনি মহাপ্রভুর বড় ভাই। সেই কারণে... হ্যাঁ একমাত্র সেই কারণেই, তাঁর নাম আজকে আমরা জানি, না হলে সেই নামও আমাদের জানার কথা নয়। আর, তিনি সন্ন্যাস ভেঙে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন কি হননি, তা জানা তো অনেক দূরের প্রশ্ন। আরও একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে...”
“কী?”
“তিনি যখন সংসার ত্যাগ করেন তখনও বিশ্বম্ভর কিন্তু ‘চৈতন্য মহাপ্রভু’ হননি। অতয়েব তাঁর ভাই সংসার ত্যাগ করলেন, এবং পুনরায় সংসারমুখী হলেন কি হলেন না, এই নিয়ে কারও মাথা ব্যথার কারণ তখন একেবারেই ছিল না... হ্যাঁ তবে এটা ঠিক যে তিনি আর স্বগৃহে ফিরে আসেননি।”
রত্নাকর ধৈর্যশীল মানুষ। কিন্তু তাও এখন কেমন যেন স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই বিশ্বামিত্রের কথার মাঝখানে কথা ঢুকিয়ে দেন, “আচ্ছা বিশ্বামিত্রবাবু আপনিই বা এটা জোর দিয়ে বলছেন কী করে, যে তিনি আবার সংসারে ফিরে এসেছিলেন!”
“না, রত্নাকর বাবু জোর দিয়ে আমি কিছুই বলছি না। একবারেই নয়। কিন্তু বিশ্বরূপের সংসারে ফিরে আসার ব্যাপারটাকে আমি অস্বীকারও করছি না। যতটুকু কথিত আছে তাতে এটা জানা যায় যে, ঐ সময়ে যারা গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্বরূপ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। মাত্র ষোলো বছর বয়েসে তিনি সংসার ত্যাগ করেন...”
সম্মুখে খোলা আকাশ। প্রকাণ্ড এক নীল মেঘ দেখা যাচ্ছিল দুই রোধবতীর সঙ্গমস্থলে। ভাগীরথী-জলঙ্গীর মিলনক্ষেত্র ছেড়ে সেই মেঘ যেন এগিয়ে আসতে শুরু করেছে, একটু একটু করে। নদীর বুক ঘেঁষে তখন উঠে আসতে শুরু করেছিল পাক খাওয়া বাতাস, যা ঘুরে বেড়াচ্ছিল ছাদের আনাচে কানাচে। হাওয়ার ঘূর্ণি পেরিয়ে ভেসে এসেছিল রত্নাকরের কিছু শব্দ, “তাতে কী বিশ্বামিত্রবাবু?”
“আজ্ঞে!”
“বলছি যে ষোলো বছর বয়েসে সংসার ত্যাগ করার সাথে, সংসারে ফিরে আসার কী সম্পর্ক...!”
“না আপাত দৃষ্টিতে কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমরা যদি একটু তলিয়ে ভাবি তাহলে কিছু কিছু বিষয় উপলব্ধি করতে পারি বৈকি। তবে উপলব্ধিই মাত্র, যা দিয়ে একটা ‘সম্ভাবনা’-র পথ প্রশস্ত হয় কিন্তু কোনও কিছু প্রমাণ করা যায় না। “মহাপ্রভু খুন হয়েছেন কিম্বা গুম হয়েছেন”, এই তথ্যই যেখানে কোনোভাবে এক অকাট্য সত্যের বেদীতে স্থাপন করা যায় না, তখন তাঁর ভ্রাতা বিশ্বরূপ, সংসারে ফিরে এসেছিলেন কি আসেননি , এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করা তো অনেক দূরের ব্যাপার।”
“মাফ করবেন বিশ্বামিত্রবাবু, এটা আমার কথার উত্তর হল না। আমি জানতে চেয়েছিলাম, ষোলো বছর বয়েসে সংসার ত্যাগ করার সাথে...”
“আসছি রত্নাকরবাবু সেই প্রসঙ্গেই আসছি। ষোলো বছর বয়েসের একজন মানুষকে কোনোভাবেই সাবালক বলা যায় না। ঐ বয়েসে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে আবেগ বড় বেশি থাকে। অধিকাংশক্ষেত্রেই ঐ সময়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এবং সেটাই স্বাভাবিক।”
“বিশ্বামিত্রবাবু তাহলে আপনি বলতে চাইছেন যে বিশ্বরূপ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন তখন আবার সংসারে ফিরে এলেন, জৈবিক কোনও তাড়না থেকে?”
“জৈবিক কোনও তাড়না থেকে ফিরে এলেন, এইরকম কথা আমি একবারও বলিনি। যে কোনও কারণেই ফিরে আসতে পারেন। আর ‘প্রাপ্তবয়স্ক’ শব্দটার থেকে ‘প্রাপ্তমনস্ক’ শব্দটার উপর আমি বেশি জোর দিতে চাইছি। আর উনি যে ফিরে এসেছিলেন এরকম কোনও নিশ্চয়তাও আমি দিচ্ছি না। আমি একটা সম্ভাবনার কথা বলছি মাত্র, আর সেই সম্ভাবনাটাকে খতিয়ে দেখতে চাইছি।”
স্বপ্ননীল বহুক্ষণ কোনও কথা বলেনি। অবাক হয়ে শুনছিল দু’জন বয়োজ্যেষ্ঠর কথোপকথন। এইবার বলে, “বিশ্বরূপ যে সংসারে ফিরে আসতে পারেন, এইরকম সন্দেহ আপনার মনে এল কী ভাবে?”
এইখানে স্বপ্ননীলের উপস্থিতির কথা বিশ্বামিত্র ভুলেই গিয়েছিলেন। চকিতে ফিরে তাকান স্বপ্ননীলের দিকে। স্নেহমিশ্রিত একটা হাসি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলেন, “খুব ভালো প্রশ্ন। না, সন্দেহ ঠিক হয়নি। আসলে, একটি জায়গা থেকে এক দেহাবশেষ পাওয়ার পরই আমি প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলাম যে, ঐ দেহাবশেষ চৈতন্য মহাপ্রভুর। কিন্তু সেটা প্রমাণ করার জন্য সঠিক এবং পর্যাপ্ত ইতিহাস আমার হাতে ছিল না। তখন আমি আঁতিপাঁতি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম এমন কোনও তথ্য, যার সাহায্যে বিজ্ঞান দিয়ে সেটা প্রমাণ করা যাবে। কিম্বা প্রমাণ না করা গেলেও অন্তত একটা প্রশ্ন তোলা যাবে...।”
বিশ্বামিত্রের কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না স্বপ্ননীল। সেইটা আন্দাজ করতে পেরে বিশ্বামিত্র বলেন, “পরিষ্কার হয়ে যাবে। সবটা শুনলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা সেই তথ্যের খোঁজ করতে করতেই বরেণ্য বিশ্বরূপ মিশ্রের কথা আমার মাথায় আসে । হানা দেই সেইসব জায়গায়, যেখানে যেখানে বিশ্বরূপ মিশ্র ভ্রমণ করেছিলেন গৃহত্যাগী হওয়ার পর । এর ফলে এমন কিছু ইনফর্মেশান আমার হাতে আসে, যাতে এটা ধারণা হতে পারে যে, তিনি পুনরায় সংসারমুখী হয়েছিলেন। তবে আবারও বলছি, ধারণাই মাত্র।” এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে, ‘ধারণাই মাত্র’।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
যাই হোক, এতখানি বলে পকেট থেকে ছোটো একটা নোটবুক বার করে রত্নাকরকে দেখান বিশ্বামিত্র সেন। অনেকগুলো নাম ড্যাস দিয়ে পর পর লেখা। বিশ্বরূপ-শ্রীরূপ-অরূপ-রূপ… এরপর আরও বেশ কয়েকটা নামের পর শেষের তিনটে নাম পিলে চমকে দেবার মত। সন্ধ্যাকর-রত্নাকর-রুদ্রনীল-স্বপ্ননীল।
তালিকাটা দেখার পর রত্নাকরের গলা দিয়ে একটা কাঁপা আওয়াজ বার হয়। “আপনি কোথায় পেলেন এই তালিকা!”
বিশ্বামিত্র বাবু নোটবুকটা বন্ধ করে পকেটে ঢোকান। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলেন, “অনেক ইতিহাস, অনেক নথি ঘেঁটে আমাকে এই তালিকাটি প্রস্তুত করতে হয়েছে। শেষ কয়েক জনের নাম অবশ্য ইতিহাসে নেই, থাকার কথাও নয়। ওইগুলি আমি অনেক দেখেশুনে, বেশ কিছু কাগজপত্র ঘেঁটে তবে জোগাড় করেছি। আমি কি ভুল করেছি রত্নাকর বাবু?”
স্বভাব বিরুদ্ধভাবে বেশ উচ্চস্বরে চিৎকার করে ওঠেন রত্নাকর মিশ্র,
“আমি তো এটাই বুঝতে পারছি না, বিশ্বরূপ যে বিবাহ করেছিলেন এইরূপ ভ্রান্ত তথ্য আপনি কোথায় পেলেন! তারপর তো বংশতালিকা নিয়ে ভাবব!”
স্মিত হাসেন বিশ্বামিত্র সেন। বলেন, “মহাত্মা শিশির কান্তি ঘোষের ‘অমিয় নিমাই চরিত’ আপনি নিশ্চয়ই পাঠ করেছেন...? ”
এই কথা শুনে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন রত্নাকর মিশ্র, “আপনি কী বলতে চাইছেন মিস্টার সেন? মহাত্মা শিশির কান্তি ঘোষ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে বিশ্বরূপ বিবাহ করেছিলেন!”
“না বলেননি। একবারও বলেননি। আসলে তাঁর লেখা থেকে ইচ্ছেমত পঙক্তি তুলে নিয়ে আজকাল বিশ্বরূপকে নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তিনি সেগুলোও বলেন নি। সেই জন্যই মহাত্মার বিষয়টা আমি উল্লেখ করলাম। দাঁড়ান আমি দেখাচ্ছি।” কথাটা বলে নিজের ঝোলা থেকে বেশ মোটা একটা বই বার করলেন। মহাত্মা শিশির কান্তি ঘোষের ‘অমিয় নিমাই চরিত’। মুখের প্রসন্ন ভাবটি দিব্য বজায় রেখে বলতে শুরু করলেন, “তৃতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪২৬। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪৯, ৫০। কী বলা হয়েছে একবার দেখা যাক— অতি সুন্দর, সুবোধ পিতৃ-মাতৃ-অনুগত, ভাতৃবৎসল, পরম জ্ঞানী ও ভক্ত, অল্পবয়স্ক বালক বৃক্ষতলবাসী হইল, এই কথা ভাবিয়া নদীয়ায় লোকে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, শচী আর জগন্নাথের তো কথাই নাই। জগন্নাথের কর্তব্য শচীকে প্রবোধ দেওয়া। কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না। বন্ধু বান্ধব বুঝাইতে লাগিলেন যে তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের পুত্র ধন্য, তাহাদের পুত্র হইতে কূল উজ্জ্বল হইল। ইহা শুনিয়া তাঁহারা শান্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা পুত্রকে বাড়ি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন? সে বাসনা বিন্দুমাত্র তাঁহাদের মনে ছিল না। ষোল বৎসরের পুত্র না বুঝিয়া সন্ন্যাস করিয়াছে। তুমি আমি হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া, তাহাকে বুঝাইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ করাইতাম। আর ভগবানের নিকট ইহাই বলিয়া কাঁদিতাম যে, হে নাথ! এই বালক-চাপল্যে সন্ন্যাস লইয়া, ধর্ম ত্যাগ করিয়া আবার সংসারী হইয়া যে ঘোর অপরাধ করিয়াছে তাহা তুমি ক্ষমা কর।”
বিশ্বামিত্র এতখানি বলে আবার মুখ তুলে তাকান রত্নাকরের দিকে। তারপর আবার অমিয় নিমাই চরিতে মননিবেশ করেন। “দেখুন এই পৃষ্ঠাতেই পরবর্তীতে আবার কী বলা হয়েছে— বিশ্বরূপ ষোড়শ বৎসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এবং অষ্টাদশ বর্ষ বয়েসে, পুনে নগরের নিকট পাণ্ডুপুর নগরে অতি অলৌকিক ভাবে অদর্শন হয়েন।”
একথা বলে আবার একবার চোখে চোখ রাখেন রত্নাকরের। তারপর আবার পাঠ করতে থাকেন, “কর্ণপুরকৃত ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’ গ্রন্থে এই কথাকে সমর্থন করা হয়েছে। এবং ভক্তমালগ্রন্থে আরও কি বলা হয়েছে,
শ্রীগৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ মতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল, হৈলা যতি।।
শ্রীমান ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি।।
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি সঞ্চারিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজঃপুঞ্জ রূপ হৈলা।
সহস্র সূর্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা।।”
বই থেকে চোখ তুলে মুহূর্তটাক সময় নিয়ে বলেন, “এই পঙক্তিগুলির পরেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের একদম শেষে, কী বলা হয়েছে একবার দেখা যাক- ইহার ষোল বৎসর পরে নিমাই তাঁহার জ্যেষ্ঠের অদর্শন স্থান দেখিতে গিয়াছিলেন।
মহাত্মা শিশির কান্তি ঘোষ রচিত— অমিয় নিমাই চরিতের এই কথাগুলো থেকে তিনটি বিষয় খুব পরিষ্কার।”
রত্নাকর মিশ্র আবার ফিরে গেছেন স্বভাবসিদ্ধ ধীরস্থির ভঙ্গিমায়। তাঁর কণ্ঠস্বর এখন আবার নির্দিষ্ট তারে বাঁধা, “কী তিনটি বিষয় যদি একটি বুঝিয়ে বলেন...”
“অবশ্যই। এক, বিশ্বরূপ যেই বয়েসে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, বয়সের সেই সন্ধিক্ষণ, জীবনের চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে একবারেই উপযুক্ত নয়। যদিও বিশ্বরূপের পিতা মাতা বিশ্বরূপকে সংসারে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেননি। কিন্তু তাঁর পক্ষে সংসারে ফিরে আসা একেবারেই অসম্ভব ছিল না বরং স্বাভাবিক।
দুই, আঠারো বছর বয়েসে বিশ্বরূপের যে অন্তর্ধানের কথা বলা হয় তা একেবারেই অলৌকিক। অতয়েব তা গ্রহণযোগ্য নয়। এবং,
তিন, চৈতন্য মহাপ্রভু যখন পাণ্ডুপুর নগরে যান তখন তাঁর সাথে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের সাক্ষাৎ হয়নি, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ‘অদর্শন স্থানটিই’ দেখতে পেয়েছিলেন মাত্র। অনেকেই এই নিয়ে নানা রকম গল্প বানান। কিন্তু এক্ষেত্রে, ‘অমিয় নিমাই চরিত’ একেবারে ভিন্ন কথা বলছে।”
রত্নাকর মিশ্রের জলদ-গম্ভীর স্বর পাক খায়, গাভীর মত চড়ে বেড়ানো হাওয়ায়, “বিশ্বরূপের অন্তর্ধান যে অলৌকিক সেই বিষয়ে যদি আরও একটু বিশদে বলেন তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়...”
“অবশ্যই।” বইয়ের পাতা উল্টে চলে যান, পিছনের দিকে । “ষষ্ঠ খণ্ড। তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭৮৮ তে কী বলা হয়েছে একবার দেখা যাক— মহাপ্রভু ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় দেশে প্রবেশ করিলেন। যেখানে তিনি অনেকগুলি অদ্ভুত লীলা করিলেন। ইহার পর প্রভু গুর্জরীনগর ছাড়িয়া পুনা যাইবেন মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া বিজাপুর গেলেন। সেখান হইতে পান্ডুপুর অর্থাৎ পাণ্ডারপুরে গমন করিলেন। যেই স্থানে, তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্য্যরূপে নিত্যধামে চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তখন সেখানে ছিলেন। তিনিই দেখিয়াছিলেন বিশ্বরূপের আত্মা দেহ ছাড়িয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায় চলিয়া গেল।...”
এক নিঃশ্বাসে লাইনগুলো পড়া হয়ে গেলে মাথা তুলে তাকান মিঃ সেন। বলেন, “আগের কথারই প্রায় পুনরাবৃত্তি এখানে ঘটেছে। মানে মহাত্মা শিশির কান্তি ঘোষ একাধিক বার তার বক্তব্যকে একই দিশায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আমার মনে হয় তিনি এইভাবেই একটি অদ্ভুত বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করতে চেয়েছেন।”
“কী বিষয়?”
“যে মহাপ্রভুর মতই তাঁর অগ্রজ বিশ্বরূপের অন্তর্ধানও সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। একজন রক্তমাংসের মানুষের এই রূপ অন্তর্ধান হতে পারে না। ‘আত্মা দেহ ছাড়িয়া সহস্র সূর্য্যের ন্যায়’ চলে যেতে পারে না।”
স্বপ্ননীল নেহাতই কিশোর তখন। তাও কেন যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল পিতামহ এবং দেবসুলভ চেহারার অধিকারী বিশ্বামিত্র সেনের আলোচনা। পিতামহ রত্নাকরের কণ্ঠস্বর এরপর আছড়ে পড়ে স্বপ্ননীলের কানে, “আপনার কি মনে হয় বিশ্বামিত্রবাবু, যে মহাত্মা শিশির কান্তি ঘোষ মিথ্যা কথা লিখে গিয়েছেন পাতায় পাতায়!”
মৃদু হাসেন বিশ্বামিত্র। এই প্রশ্নের উত্তর যেন তৈরিই ছিল, “না। বরঞ্চ বিপরীতটাই সত্য। তিনি পাতায় পাতায় সত্যিটাই লিখে গেছেন। একটু অন্যভাবে। এখানে একটা জিনিস কিন্তু আমাদের খেয়াল করা দরকার। সেটি হল, মহাত্মা তার নিজের চোখ দিয়ে কিছু দেখছেন না। দেখছেন শিবানন্দ সেনের চোখ দিয়ে। এবং আমার মনে হয় তিনি ইচ্ছে করেই বিষয়টিকে এই ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। যাতে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে।”
রত্নাকর মিশ্র বুঝতে পারেন যে এই মানুষটিকে যুক্তিতর্কে হারানো সহজসাধ্য নয়। তিনি এইবার আসল তিরটি বার করেন তূণীর থেকে, “আচ্ছা বিশ্বামিত্রবাবু আপনি আমার একটি কথার উত্তর দিন তো...।”
“দয়া করে বলুন।”
“আপনিই বা এই কথা নিশ্চিত করে কী করে বলছেন যে বিশ্বরূপ বিবাহ করেছিলেন, সংসারে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেই থেকে মিশ্র বংশের ধারাকে বহমান করেছিলেন !”
“এই ক্ষেত্রে প্রথমেই যা বলেছি সেটাই আবার বলব। বারংবার বলব। তা হল আমি কোনও কিছুই নিশ্চিত করে বলছি না। একটা সম্ভাবনার কথা বলছি মাত্র। সে যাই হোক, চূড়ঙ্গগড়ের কাছে সিদ্ধেশ্বর মন্দির। মন্দির পার্শ্বস্থ জঙ্গলে আমার কাঙ্ক্ষিত দেহাবশেষটি পাওয়ার পর যে অনুসন্ধান আমার শুরু হয়েছিল, তার সূত্র ধরেই আমি একদিন পৌঁছে যাই চৈতন্য ভ্রাতা বিশ্বরূপের ‘অদর্শন’ হওয়ার স্থানটিতে। কিন্তু আমি সেখানকার ইতিহাসে এমন কিছু খুঁজে পাইনি, যাতে এটা প্রমাণ করা যায় যে, বিশ্বরূপ সত্যি সত্যি অষ্টাদশ বর্ষ বয়েসে ‘অপ্রকট’ হয়েছিলেন। এইবার আমাকে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে অমিয় নিমাই চরিতে। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪৯ এ। কী লেখা হয়েছে সেখানে— বিশ্বরূপ এবং লোকনাথ যদিও সমবয়স্ক, সমাধ্যায়ী ও পরস্পর ভাতৃসম্পর্কীয় তত্রাচ বিশ্বরূপকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন লোকনাথ। ইহা বিচিত্র নহে, যেহেতু রূপে গুণে বিশ্বরূপ দেবতার ন্যায় ছিলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিবেন লোকনাথকে বলিলেন। লোকনাথও তদ্দণ্ডে বলিলেন, বিশ্বরূপ যেখানে যাইবেন, তিনি তাহার পশ্চাৎ ছাড়িবেন না। বিশ্বরূপ কাজেই লোকনাথকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন।”
রত্নাকর মিশ্র বললেন, “সে তো বুঝলাম। কিন্তু এর থেকে কী বলা যায় মি. সেন!”
“আসছি আমি সেখানেই আসছি। আমি পাণ্ডারপুরে যাই। সেখানে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। আমার অনুসন্ধিৎসু মন তার কাজ চালাতে চালাতেই খুঁজে পায় এমন একজন মানুষকে, যিনি নিজেকে দাবি করেন বিশ্বরূপ ঘনিষ্ঠ লোকনাথের বংশধর রূপে। প্রমাণ স্বরূপ আমাকে এমন একটি জিনিস দেখান যাতে আমি তার কথায় কিছুটা হলেও ভরসা করতে সাহস পাই।”
স্বপ্ননীল মজে গিয়েছিল গল্পে। কয়েকটি শব্দ তার মুখ থেকে ছিটকে বার হয়, “কী দেখিয়েছিলেন তিনি?”
“বিশ্বরূপের একখানি পুঁথি। আরও বলার আগে, অমিয় নিমাই চরিতের প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৪৯ থেকে আরও কয়েকটি লাইন উধৃত করতে হবে আমাকে-বিশ্বরূপের বয়ঃক্রম তখন ষোল বৎসর মাত্র। বালক বলিলেই হয়, লোকনাথ তাহার ছোট। এই দুই জনে রজনীতে জগন্নাথের বাড়িতে শয়ন করিয়া রহিলেন। শীতকাল। রজনী আন্দাজ এক প্রহর থাকিতে দুই জনে উঠিলেন। সম্বলের মধ্যে একখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। আঙিনায় আসিয়া নিদ্রিত মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন আর নিমাইকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে চলিলেন...।”
বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হবার আগেই রত্নাকর মিশ্র বলে উঠলেন, “আমি যে অন্য কথা জানি মি. সেন।”
“কী কথা?”
“বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করার আগে মা শচীদেবীর হাতে একখানি পুঁথি ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সেটা নাকি নিমাইয়ের জন্য। নিমাই বড় হলে তাঁকে দিতে। এই কথা কি তবে ভুল মি. সেন!”
“না। একটুও ভুল নয়। সেটাও লেখা আছে এই পৃষ্ঠা-৪৯ এই। ঠিক, মাতৃদেবীকে একখানি পুঁথি ভাইকে দেবার জন্য উনি দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পুঁথির সাথে, যেই পুঁথি নিয়ে উনি গৃহত্যাগ করেছিলেন তার বিরোধ কোথায়? দু'খানি আলাদা গ্রন্থ, এটা বুঝতে পারলেই তো আর কোনও সমস্যা থাকে না।”
এতখানি বলার পর বিশ্বামিত্র সেন ‘শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত’ বন্ধ করে পূর্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকালেন রত্নাকর মিশ্রের দিকে,বললেন, “হ্যাঁ যা বলছিলাম..., এইখানে যে পুঁথি একমাত্র সম্বল করে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, পাণ্ডারপুরের মানুষটি সেই পুঁথিটির একটি প্রতিলিপি আমাকে দেখিয়েছিলেন। আরও একটু বিস্তারে বললে, যে কথাটা বলা যায় তা হল, উনি আমাকে একখানি পুঁথি দেখিয়ে দাবি করেছিলেন যে, এটি সেই বিশ্বরূপের পুঁথির প্রতিলিপি যা তাঁর বংশপিতা লোকনাথের নিজের হাতে করা। আমি সেই প্রতিলিপি থেকে আরও একটি প্রতিলিপি করাই এবং আসার সময় সাথে করে নিয়ে আসি। সে যাই হোক, যেটি বলবার তা হল, সেই পুঁথিটির প্রতিলিপি আমার ভিতরে এই বিশ্বাস দৃঢ় করে যে ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই লোকনাথের বংশপুরুষ এবং তিনি যা বলছেন তা সত্য বলছেন।”
এতটা বলে একটু থামেন বিশ্বামিত্রবাবু কিন্তু রত্নাকর তখন রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন, “তারপর বিশ্বামিত্রবাবু?”
“ হ্যাঁ...আমি সেই ভদ্রলোকের থেকে লোকনাথের বংশ এবং মিশ্রবংশের একখানি করে তালিকা পাই। যে দু’খানি তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে তিনি পেয়েছেন। মিশ্রবংশের তালিকাটিরও আমি একটি প্রতিলিপি বানাই। তবে ঐ খানে শেষ চারজনের নাম ছিল না। আজ থেকে প্রায় শ'খানেক বছর আগেই সেই বংশপঞ্জী শেষ হয়ে গেছে।”
“তারপর?”
“তারপর আমি বারংবার অনুরোধ করাতে মিশ্র বংশের শেষ চারজনের নাম সম্বলিত আলাদা একটি তালিকা তিনি আমাকে দেন। অতঃপর, আমি আমার মত করে সেই তালিকার শেষ চারটি নাম নিয়ে অনুসন্ধান চালাই। সেই জন্য আমাকে নবদ্বীপেও আসতে হয়। এখন বলতে দ্বিধা নেই যে আমি আপনাদের এই বাড়ি আগের থেকেই চিনতাম। আপনার প্রতিবেশীর থেকে আমি আপনাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করি। সেই তথ্য থেকে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি প্রথম তালিকা যেখানে শেষ হচ্ছে পরের তালিকা সেখান থেকেই শুরু হচ্ছে। এবং বহমান সেই বংশধারা গিয়ে শেষ হচ্ছে স্বপ্ননীলে।”
বিশ্বামিত্র সেনের এই কথায় হতবাক হয়ে যায় স্বপ্ননীল। সে বলে, “তাহলে আপনি যে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, রত্নাকর মিশ্রের বাড়ি কোথায়!”
“হা হা হা সেটি নিছকই মজা করার জন্য। যাই হোক, আমি নবদ্বীপে অনুসন্ধান চালিয়ে এটি একরকম নিশ্চিত হয়ে যাই যে, দ্বিতীয় তালিকায় থাকা শেষ চারজনের নাম নিয়ে কোনও সংশয় নেই।”
রত্নাকর বলে ওঠেন, “আপনি যে পাণ্ডুপুরবাসির কথা উল্লেখ করলেন, তার নামটা জানতে পারি কি, যে মিশ্রবংশ সম্পর্কে এতখানি উৎসাহী!”
“আজ্ঞে আমাকে ক্ষমা করবেন রত্নাকর বাবু। সেই ভদ্রলোক আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে, আমি কখনই যাতে কাউকে ওঁর নাম না বলি। একটা কথাই বলতে পারি উনি বহুদূরে থাকলেও, মহাপ্রভুর বংশ পরম্পরা সম্পর্কে আর পাঁচ জনের মতই আগ্রহী। এবং সেটাই স্বাভাবিক। সেই কারণেই তাঁর সংগ্রহে রয়েছে যাবতীয় তথ্য।”
রত্নাকর স্তব্ধ হয়ে থাকেন। বিশ্বামিত্র বাবু বলেন, “আচ্ছা এইবার আপনি দয়া করে বলুন রত্নাকরবাবু, আমার কাছে যে তালিকা আছে তা কি একেবারেই আজগুবি? আমার বিশ্বাস কিছু অসাধু মানুষ এই তালিকাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও, আপনি অন্তত এইটিকে একবার বিচার করে দেখবেন। বলুন রত্নাকরবাবু...”
“কী বলব?”
“আমার এতদিনের যে অনুসন্ধান, তাঁর অভিমুখ সঠিক কিনা?”
অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফিরে এসেছিল রত্নাকরের চেহারায়। বলেন, “কী অনুসন্ধান বিশ্বামিত্রবাবু ?”
নীলের এই কথোপকথন শোনার নেশা ক্রমশ বাড়ছে। সে তখনও দাঁড়িয়ে, বিকেলের আড্ডা ছেড়ে।
ঐ দিকে মি. সেন বলে যান, “আমার এই অনুসন্ধানের বিষয়, দু’এক কথায় বলা সম্ভব নয়। সে বিষয়ে বলার আগে কিছু অত্যাবশ্যক ভূমিকার প্রয়োজন।”
আসুদা দুজনের জন্য আবার এক রাউন্ড চা নিয়ে আসে। নামিয়ে রাখে সামনের গোল টেবিলে। নীলকে বলে, “খোকাবাবু তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ যে। তোমার জন্য একখানা মোড়া এনে দিই না হয়...।”
“না না আসুদা লাগবে না। আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।”
জলঙ্গী আর ভাগীরথীর সীমানায় যে প্রকাণ্ড নীল মেঘখানা ছিল, তার থেকে বৃষ্টির গন্ধ ছড়াতে শুরু করেছিল ততক্ষণে। রত্নাকর বলেন, “চা টা নিন বিশ্বামিত্র বাবু।”
কাপটা তুলে নিয়ে একটা লম্বা চুমুক দেন বিশ্বামিত্র। চিলেকোঠার কার্নিশে কিছু পায়রার বাক্স। নীলের সখ। অন্ধকার নামার আগে ঘরে ফিরে আসছিল পাখিরা। পালক আর হলুদ কলতান ছিল বাতাসে। এরই মধ্যে, বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে ফের কথা শুরু করেন বিশ্বামিত্র। ওঁর কথা অনুযায়ী যা ‘অত্যাবশ্যক ভূমিকা’।
“দেখুন রত্নাকর বাবু, নবদ্বীপ যে সে জায়গা নয়। এই পুণ্যস্থান হল মহামানবের মিলন ক্ষেত্র। প্রভুর জন্মের আগে থেকেই, আবির্ভাব ঘটেছে একের পর এক মহাধনুর্ধর পণ্ডিতের। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তী এবং পূর্ববতী সময়কালটাকে বলেছেন বাঙালির রেনেসাঁ।”
রত্নাকর আরাম কেদারার ঠেসান ছেড়ে সোজা হয়ে বসেন। বিশ্বামিত্র অনাড়ম্বর কিন্তু সাবলীল ভাবে বলে যান বাংলার সেই গৌরবান্বিত ইতিহাস, “মহামানবের এই মিলন ক্ষেত্রেই একদিন আনন্দচন্দ্রোদয় হল। শুধু নবদ্বীপের মানুষ নন, সমগ্র একটা জাতি যেন সিক্ত হল স্নিগ্ধ আলোয়। পেল এক নতুন পথের সন্ধান। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির যে ভাব ধারা ছিল আগের থেকেই বহমান, তাতে জাগল প্লাবন। আসলে আবির্ভূত হলেন কে, না, আনন্দ জাগরণের প্রধান কাণ্ডারি। প্রধান ধর্মবেত্তা, প্রধান শাস্ত্রবেত্তা, প্রধান দর্শনবেত্তা ও প্রধান ন্যায়বত্তা। তবে... , ঐ সময়টাতে, মশাল বাহক একা মহাপ্রভু নন। আরও যাদের কথা না বললে অবিচার করা হবে তারা হলেন...”
একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করেন, “দর্শনে-রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ। স্মৃতিতে রঘুনন্দন। বাংলা কাব্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস...।”
অপূর্ব বিশ্বামিত্রর বাচন ভঙ্গি। শব্দ প্রক্ষেপণের ভঙ্গিমায় এমন একটা কিছু আছে, যা চিত্তাকর্ষক। এতখানি বলে , বাকি চা টুকু এক চুমুকে শেষ করেন। কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে আসল কথাটা বলেন এবার, “আমার বহুদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল এই নবদ্বীপ সম্পর্কে জানবার এবং আনন্দ জাগরণের প্রধান কাণ্ডারি মহাপ্রভুর সম্পর্কে জানবার। শুরু এবং শেএএষ। সবটা...।
এখনও মনে আছে স্বপ্ননীলের ‘শেএএষ’ শব্দটা এতখানি জোর দিয়েই বলেছিলেন বিশ্বামিত্র।
যাই হোক, বলে চলেছিলেন তিনি, “সেই চেষ্টার ফলস্বরূপই শুরু হয় আমার অনুসন্ধান এবং সেই অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই, ওড়িশার দুর্ভেদ্য চূড়ঙ্গগড়ের কাছে যে সিদ্ধেশ্বর মন্দির, তার পার্শ্বস্ত জঙ্গল থেকে উদ্ধার করি এক দেহাবশেষ। বহুকাঙ্খিত সেই দেহাবশেষ অনুসন্ধান করতে করতেই, যে ভাবনাটা আমার মনে উঁকিঝুঁকি মারছিল, তাও যেন একটা রূপ পরিগ্রহ করে। অনুসন্ধান করতে করতেই আমার অনুমান ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে যে..., হ্যাঁ ‘অনুমান’ শব্দটিই এখানে ঠিক...”
রত্নাকর, প্রসঙ্গে থাকতে চান। তিনি বিশ্বামিত্র কথা শেষ হবার আগেই বলেন, “হ্যাঁ কী অনুমান করেছিলেন আপনি?”
“যে সেই মহাপুরুষের বংশধর আপনারা...। হ্যাঁ প্রায় সরাসরিই তাঁর উত্তরপুরুষ আপনারা।”
এই বাক্যের পর, দু’এক মুহূর্ত কেউ কোনও কথা বলে না। বিশ্ববাবুকেই নীরবতা ভঙ্গ করার দায়িত্ব নিতে হয়, “আমি কি ভুল জানি মি. মিশ্র? বলুন... আপনিই বলুন ...আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।”
“ভুল অথবা ঠিক আমি বলতে পারব না বিশ্বামিত্র বাবু। তবে, আমার কাছে যে বংশ পঞ্জী আছে, তাতে আমার থেকে যদি পিছিয়ে যাওয়া যায় তবে নবম পুরুষ অব্দি নাম পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সেই নামগুলির সাথে এই তালিকা মিলে গেছে বটে।”
শিশুসুলভ চিৎকার করে ওঠেন মি. সেন, “আমার এই বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হল যে আমি ঠিক পথেই এগোচ্ছি।”
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই, ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
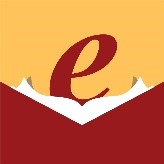

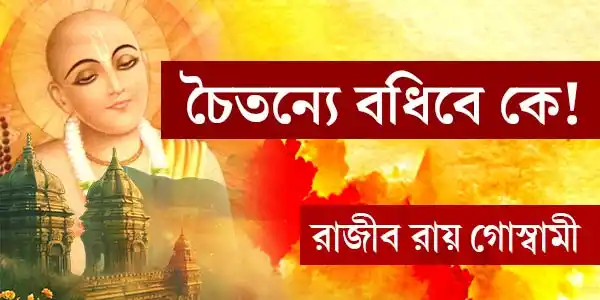




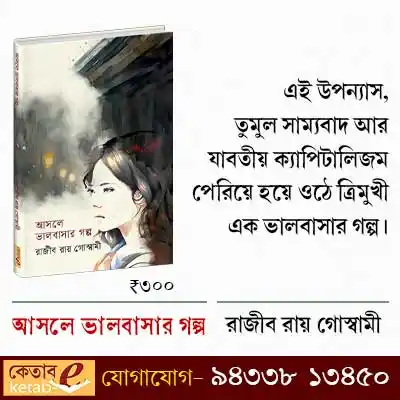
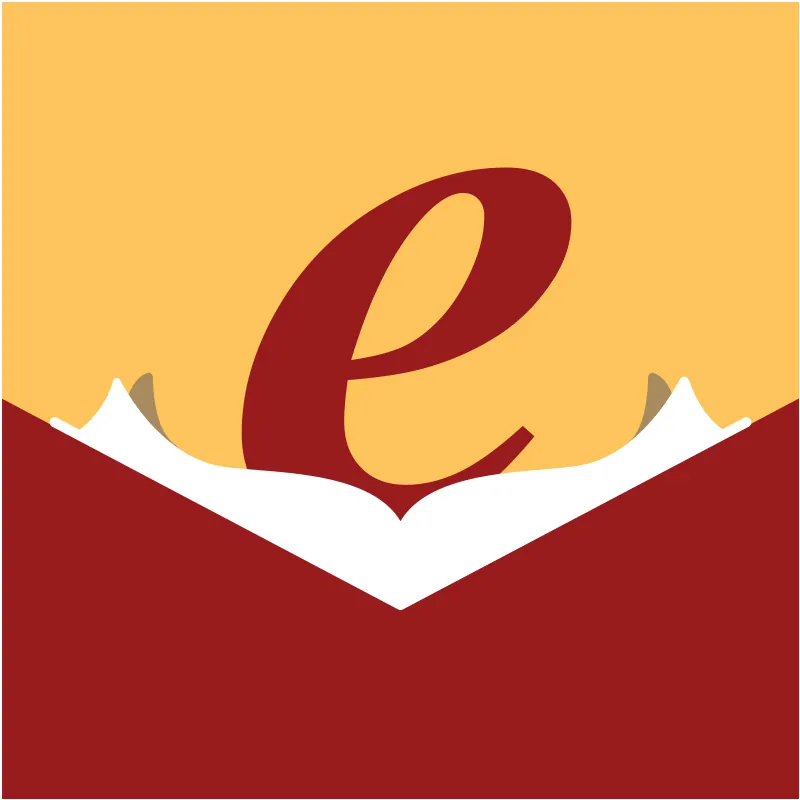
Partha Mukherjee
8 মাস আগেশিশির কান্তি ঘোষ, না-কি শিশির কুমার ঘোষ? এইটা নিয়ে একটু বিভ্রান্তি হলো। লেখা বেশ ভালো, সুন্দর যাচ্ছে।