চলচ্চিত্রের জন্ম, বিবর্তন, রাজনীতি আর শিল্পের সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধে সায়ন দত্ত দেখিয়েছেন চলমান চিত্রের শিল্পভাষার ইতিহাস, গ্রিফিথ থেকে অনুপর্ণা রায় পর্যন্ত এক মুগ্ধকর যাত্রাপথ। সিনেমাপ্রেমী, পাঠক ও চিন্তাশীল মানুষ—সকলের জন্যই এটি এক অপরিহার্য পাঠ।
“Every child deserves peace, freedom, liberation and Palestinians are no exception... It's a responsibility at the moment to stand by Palestine... I might upset my country, but it doesn't matter to me anymore…”
প্রথম গান কে গেয়েছিলেন? বা প্রথম লেখা কবে শুরু হয়েছিল? এই বিষয় নিয়ে আমাদের কাছে সঠিক কোনো তথ্য নেই। কিন্তু শিল্পের প্রায় কনিষ্ঠতম সন্তানটির সঠিক জন্ম তারিখ আমরা জানি। (প্রায় বলছি কারণ, চলমান চিত্র তার মাধ্যম পরিবর্তন করেছে। বিবর্তন করেছেও বলা চলে। যদি, ওয়েব সিরিজকে প্রাচীনপন্থী চলচ্চিত্রের বিবর্তিত রূপ ধরি, তাহলে সে তো আজ আধুনিকতম মুকুটের দাবিদার) আজ থেকে প্রায় ১৩০ বছর আগে পথ চলা শুরু ‘Motion picture’-এর। সময়টা ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫, সিনেমার ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম দিন। প্যারিসের গ্র্যান্ড ক্যাফেতে প্রদর্শিত হল প্রথম কমার্শিয়াল সিনেমা। এই দিনটির ঠিক কতটা মাহাত্ম্য, তা হয়তো সেদিন ল্যুমিয়ের ব্রাদার্সরাও বুঝতে পারেননি। হয়তো সেদিন প্যারিসের দর্শকরাও এর ভবিষ্যৎ পরিধি আন্দাজ করতে অক্ষম ছিলেন।
শিল্পের নবাগত মাধ্যমটির ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই, তার পরিচয় হয় শিল্প (Industry)-র সঙ্গে। ভালোভাবে বলা যায় পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির একটি মাধ্যম হিসেবেই চলচ্চিত্রের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু এই ঘটনাই বপন করে ভবিষ্যতে দ্বন্দ্বের বীজ। পুঁজিপতিরা মুনাফা বোঝেন, কিন্তু চলচ্চিত্র তো নির্মাণ হওয়া উচিত শিল্পগুণ-এর উপর, ফলে সংঘাত বাঁধাই স্বাভাবিক। আর এই সংঘাতের বলি হিসেবে চলচ্চিত্রের প্রথম প্রতিভা, আধুনিক সিনেমার জনক ডেভিড ওয়াক গ্রিফিথকে জীবনের শেষ সময় কাটাতে হয় পানশালায় তীব্র দুর্দশার মধ্যে দিয়ে, চ্যাপলিনকে দেশ ত্যাগ করতে হয়, আইজেনস্টাইনের মেক্সিকোতে সাত মাস ধরে করা শুটিং বন্ধ করে দিতে হয়। আর ভারতে! পুঁজির ফাঁদে পড়ে বলিউডের সঙ্গে মহানায়কের হয় না ‘chhoti si mulaqat’।
মানুষ চলমানতা পছন্দ করে। গুহার গায়ে আঁকা প্রথম ‘ছয় পা-ওয়ালা বাইসন’ থেকেই বোঝা যায় গুহামানবও চিত্রের চলমানতা তার গুহাচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এবার আসা যাক চলচ্চিত্রের বিবর্তনের প্রসঙ্গে। ল্যামিয়ের ভাইরা ১৮৯৫ থেকে ১৯০৬-এর মধ্যে বানিয়ে ফেলেছেন হাজারখানেক চলমান চিত্র, যা নেহাতই ‘Moving shorts’ ছাড়া কিছু নয়। আধুনিক চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ আসলে যে ব্যক্তির নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তিনি ডেভিড ওয়াক গ্রিফিথ। তাঁর প্রথম শিল্পকর্ম হিসেবে বলা যায় ‘THE BIRTH OF NATION’ (1915) চলচ্চিত্রটিকে। এটি ছিল পৃথিবীর প্রথম উল্লেখযোগ্য ফ্যাসিবাদী ছবি। ছবির গল্প তিনি ধার করেন, কুখ্যাত বর্ণবিদ্বেষী লেখক টমাস ডিকসনের উপন্যাস থেকে। এই চলচ্চিত্রে স্পষ্টতই দেখনো হয় কালো চামড়ার মানুষ সাদা চামড়ার দাস হিসেবে থাকলেই সমাজে শৃঙ্খলা থাকে। এবং চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে দেখানো হয়, দক্ষিণের ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী ‘ক্লু ক্লাক্স ক্লান’ সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে কালো চামড়ার মানুষদের পুনরায় দাসে পরিণত করছে। বিশুদ্ধ প্রোপাগান্ডা এই সিনেমার বিষয়। তবুও এটা সিনেমা, এর শিল্পগুণ আছে। নয়কে ছয়ের মতো না করে, নয়কে নয়ের মতো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা। আজকাল প্রোপাগান্ডা শব্দের ব্যবহার করে যে যা খুশি বানাচ্ছে। শিল্পগুণ না থাকলে, সিনেমার কথা কেউ মনে রাখে না, রাখবেও না। তাই, প্রোপাগান্ডা প্রধান হলেও ‘BIRTH OF NATION’ সিনেমা, আর অনেক কাজ প্রোপাগান্ডা ছড়াতে গিয়ে D বা E গ্রেডের সিনেমা হবার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। ‘BIRTH OF NATION’-এর ঠিক এক বছর পরে গ্রিফিথের কাছ থেকে আমরা পাই ‘INTOLERANCE’ (1916), যারা আবেদন ‘BIRTH OF NATION’ এর ঠিক উলটো। ছবিটি ছিল ১২ ঘন্টার দীর্ঘ ছবি। আপাত বিচ্ছিন্ন চারটি আলাদা আলাদা কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই চলচ্চিত্রটি। যদিও প্রত্যেকটি কাহিনির দাবি ছিল একটি। মানুষের, মানুষের উপর আগ্রাসন। গ্রিফিথই চলচ্চিত্রকে উপহার দিয়েছেন বাস্তববাদ, যা সেই সময় কল্পনা করাই ছিল অসম্ভব। তিনিই প্রথম লং, মিড লং এবং ক্লোজ আপ-এর ধারণা দেন। আধুনিককালে ব্যবহৃত হওয়া ফ্ল্যাশব্যাক প্রথাও তাঁরই সৃষ্টি। “বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজের ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি”-(শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ঠিক এই কারণেই ধীরে ধীরে হলিউডে পড়তে থাকে গ্রিফিথের বাজার। যে হলিউডের পুঁজিপতিরা একসময় তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তাঁরাই গ্রিফিথকে সিংহাসনচ্যুত করেন। কারণ ততদিনে পৌনঃপুনিকতা গ্ৰিফিথকে গ্রাস করেছে। আর আগেই বলেছি, তৎকালীন সময়ে মার্কিন পুঁজিপতিদের কাছে চলচ্চিত্র ছিল একটি ব্যাবসার মাধ্যম। আর তাই গ্রিফিথের শেষ জীবন কাটে চরম দূর্দশায়। চলচ্চিত্রের প্রাতঃকালে হলিউডে আরও কিছু স্মরণীয় নাম এস. পিটার, জন ফোর্ড, ওয়েলস, চ্যাপলিন-এর মতো ব্যক্তিত্বরা। চ্যাপলিনের চলচ্চিত্র জগৎ-এর সাহসিকতা অবশ্যই কুর্নিশযোগ্য। চার্লি বারবার ব্যঙ্গ করেছেন সমাজের তথাকথিত ভদ্র সমাজকে। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রে বারবার বুঝিয়েছেন, তিনি নিচুতলার মানুষের প্রতিনিধি। তাঁর ব্যঙ্গের নিদর্শন হিসেবে বলা যায় ১৯২১ সালে মুক্তি পাওয়া ‘THE KID’ সিনেমার কথা। সিনেমাটি শুরু হওয়ার পূর্বেই লেখা থাকে ‘A picture with smile-perhaps a drop of tear’। মনে পড়ে ১৯২৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘GOLD RUSH’ সিনেমায় তীব্র ক্ষুধায় জুতো সেদ্ধ করে খাবার দৃশ্যটির কথাও। চ্যাপলিনের তৈরি ‘THE GREAT DICTATOR’ (1940) নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ সাহসিকতার প্রমাণ রেখে যায়।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
ভি.আই.লেনিন বলেছিলেন: ‘আমাদের জন্য চলচ্চিত্র হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম’। খালি মুখের কথা নয়, সোভিয়েত বিশ্ব চলচ্চিত্রকে উপহার দিয়েছে আইজেনস্টাইন, পুডভকিন, ডবঝনকো, জিগা ভার্তবের মতো চিত্রপরিচালক। এক অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা। যখন গ্রিফিথকে মার্কিন শিল্পপতিরা প্রত্যাখ্যান করলেন, তখন আইজেনস্টাইন ‘গ্রিফিথ ও আজকের চলচ্চিত্র’ শীর্ষক নিবন্ধে গ্রিফিথকে চলচ্চিত্রের প্রথম প্রাণপুরুষ বলে সম্মানিত করলেন। আর গ্ৰিফিথও তাঁর দেখা সর্বশেষ্ঠ সিনেমা হিসেবে দাবি করলেন ‘BATTLESHIP POTEMKIN’ (1925) কে। যেখানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে সেন্সর বোর্ড নিয়ে এত লাফালাফি, সেখানে প্রায় ১০০ বছর আগে নবাগত আইজেনস্টাইনকে কোনো প্রকার বাধার মধ্যে না রেখেই তৈরি করতে দেয়া হয় ‘BATTLESHIP POTEMKIN’। এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব আজও আমাদের মুগ্ধ করে। তা ছাড়াও তাঁর তৈরি ‘OCTOBER’(1928), ‘GENERAL LINE’(1929) এক-একটি অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি তাঁর চলচ্চিত্রে মান্তাজের সফল প্রয়োগ করেন। ক্যামেরা ব্যবহার ও তার জ্যামিতিক কোণ থেকে দৃশ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসামান্য। যার প্রমাণ তাঁর একাধিক চলচ্চিত্র। এ ছাড়াও ডবঝনকোকের ‘EARTH’ , পুডভকিনের ‘MOTHER’ সোভিয়েতের এক-একটি অসাধারণ সৃষ্টি। আর যদি সেন্সরবোর্ডের কথাই হয়, তবে বলতে হয় কিউবার কথা। খোলামেলা করে বলা যায়, কিউবার সিনেমায় সরকারি নজরদারি সে অর্থে নেই। ফলে শিল্পীর হাতে রয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কিউবার একটি কাহিনিচিত্র ‘THE THIRD BRIGADE’-এর কথা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ আসলে পূর্ব ইউরোপের মেসজরাস-এর কথা বলতেই হয়। তাঁর তৈরি ‘NINE MONTHS’ একটি অসামান্য সৃষ্টি। চলচ্চিত্রটিতে নায়িকা লিলি মোলার প্রকৃতই গর্ভবতী ছিলেন, এবং সিনেমাটির শেষদৃশ্যে ছিল তাঁর প্রকৃতই প্রসবের দৃশ্য। যা ছিল বাস্তবতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন। চরিত্রকে বাস্তবসম্মত করতে আধুনিক কালে হিথ লেজারের কথা বলতেই হয়। তিনি ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত সুপারহিরো চলচ্চিত্র ‘দ্য ডার্ক নাইট’ চলচ্চিত্রে কিংবদন্তী চরিত্র ‘দ্য জোকার’ চরিত্রে অভিনয় করেন। এটি ২০০৮ সালে তাঁর মৃত্যুর ছয় মাস পর মুক্তি পায়। এই ছবিতে তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি মরণোত্তর শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন, যা তাঁর পরিবার গ্রহণ করে এবং সেরা পার্শ্ব অভিনেতার জন্য গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার লাভ করেন, যা তাঁর পক্ষ থেকে পরিচালক নোলান গ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি সেরা পার্শ্ব অভিনেতার জন্য বাফটা পুরস্কার, লস অ্যাঞ্জেলেস ফিল্ম ক্রিটিকস অ্যাসোসিয়েশন পুরস্কার ও অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে সেরা আন্তর্জাতিক অভিনেতার খ্যাতি অর্জন করেন। শোনা যায়, চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য করতে তিনি দীর্ঘদিন ‘Self isolation’-এ ছিলেন। যা পরবর্তীতে তাঁর গভীর মানসিক অবসাদের কারণ হয়ে ওঠে।
বিশ্বমানের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে আমরাও পিছিয়ে নেই। আমাদের ঝুলিতেও আছে ‘পথের পাঁচালী’ (১৯৫৫), ‘পদাতিক’ (১৯৭৩), ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬০), ‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১), ‘প্রতিদ্বন্দী’ (১৯৭২)-র মতো চলচ্চিত্র। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’(১৯৭০) তে আমরা পালামৌ শুনতে-শুনতে হারিয়ে যাই মহুয়ার মাদকতায় এক লজ্জাহীন মাতলামিতে আবার ‘নায়ক’(১৯৬৬)-এ দেখতে পাই এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক রেলযাত্রা। মৃণাল সেনের ‘কোরাস’(১৯৭৪), ‘কলকাতা -৭১’(১৯৭১) আমাদের দেয় নিউ রিয়ালিজম-এর ধারণা। আবার ঋত্বিক ঘটক ‘তিতাস একটি নদীর নাম’(১৯৭৩), ‘সুবর্ণরেখা’ (১৯৬৫)-য় দেখান দেশভাগের যন্ত্রণা। প্রতিটিরই চলচ্চিত্রগত মূল্য অপরিসীম। এবং চলচ্চিত্রগত ব্যাখ্যা অনেক গভীর। আমরা একই সময়ে দেখছি ‘পদাতিক’ (১৯৭৩), ‘প্রতিদ্বন্দী’ (১৯৭২) -র মতো রাজনৈতিক সিনেমা, যা তৎকালীন তিলোত্তমার অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে সক্ষম। তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের আয়োজনে পেয়েছি ‘টুমোরো ইজ টু লেট’, ‘কবিতার অনন্ত যাত্রা’। যা বিশেষ প্রশংসিত।
আজকে আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি... হলিউডে পেয়েছি একাধিক অস্কারজয়ী সিনেমা। বাংলাও প্রচুর বক্সঅফিস মাতানো চলচ্চিত্র তৈরি করেছে। অনেক আধুনিক হয়েছে অভিনয় কৌশল, ক্যামেরা ধরার পদ্ধতি। রিয়ালিজমের বিশেষ প্রয়োগ এখন চলচ্চিত্রে দেখা যাচ্ছে। চলমান চিত্রকে চলতে হবে আরও অনেকটা পথ... হবে আরও নানা নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট। উপরের যে সংলাপ দিয়ে লেখা শুরু করলাম সেটি, ভেনিসের মঞ্চে থেকে Best Director Award হাতে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে ওঠেন বাংলার মেয়ে অনুপর্ণা রায়। তাঁর এই অবস্থান দেখে গর্ব হয়েছে, বিস্মিত হইনি। বাঙালি তার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আগাগোড়াই স্পষ্ট। আর তাই রাজনীতির ছোঁয়া দেখা যায় বাঙালির দীর্ঘকালের সিনেমার ভাষায় (পূর্বে বেশ কিছু উদাহরণ দেয়া আছে)। মাঝে বেশ দীর্ঘ সময় জুড়ে কিছু বাঙালি পরিচালক সিনেমা ও রাজনৈতিক অবস্থানকে অনেকটা ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ গোছের রাখতে চেয়েছিলেন। এক বাংলার মেয়ের এই পুরষ্কার প্রাপ্তি, এবং বিশ্ব মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁর দীপ্ত গলায় বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে রাখা এই বক্তব্য যে-কোনো সিনেপ্রেমীর কাছে আশার আলো। শিল্পের এই কনিষ্ঠতম সন্তানটির মুকুটে আরও নতুন নতুন পালক যুক্ত হোক, এই আশায় থাকবে সিনেমাপ্রেমীর।
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
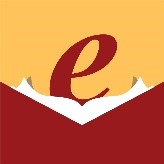

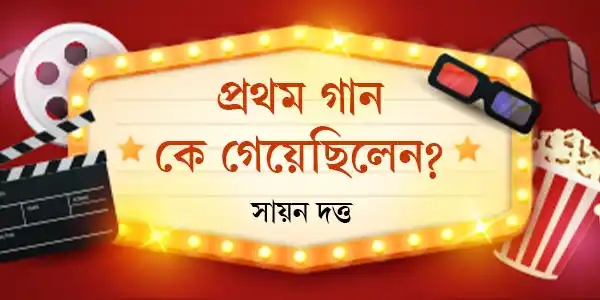




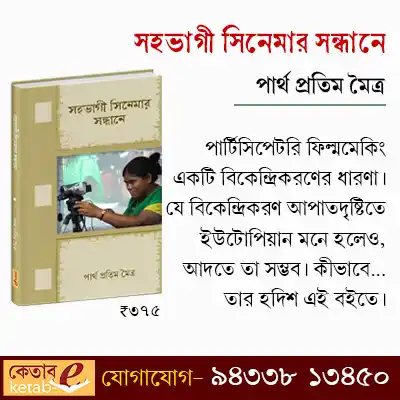
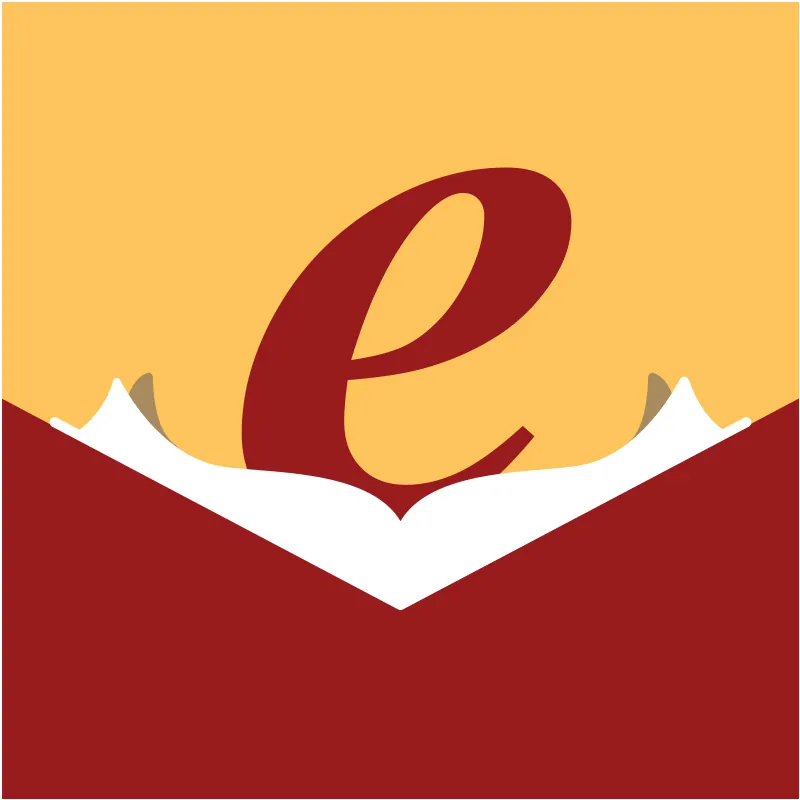
Jigeesha Biswas
4 মাস আগেবিভিন্ন সাইটে লেখা পড়লেও আমি সচরাচর মন্তব্য করিনা। কিন্তু এক্ষেত্রে বলছি, কারণ লেখকটি নবীন। লেখাটি পড়লাম। ভালো লাগলো। লেখার বাঁধুনি সুন্দর, লেখক যে যথেষ্ট গবেষণা করে লেখাটি লিখেছে তা স্পষ্ট। পাশাপাশি বিষয় নির্বাচনেও অভিনবত্ব আছে। নবীন এই লেখকটির আরো অনেক লেখা আশা করি পরর্বতীতেও এই পেজ থেকে পড়তে পারব। কেতাবি যে এইভাবে নতুন লেখকদের লেখার সুযোগ করে দিচ্ছে তা দেখে ভালো লাগলো।
Jigeesha Biswas
4 মাস আগেবিভিন্ন সাইটে লেখা পড়লেও আমি সচরাচর মন্তব্য করিনা। কিন্তু এক্ষেত্রে বলছি, কারণ লেখকটি নবীন। লেখাটি পড়লাম। ভালো লাগলো। লেখার বাঁধুনি সুন্দর, লেখক যে যথেষ্ট গবেষণা করে লেখাটি লিখেছে তা স্পষ্ট। পাশাপাশি বিষয় নির্বাচনেও অভিনবত্ব আছে। নবীন এই লেখকটির আরো অনেক লেখা আশা করি পরর্বতীতেও এই পেজ থেকে পড়তে পারব। কেতাবি যে এইভাবে নতুন লেখকদের লেখার সুযোগ করে দিচ্ছে তা দেখে ভালো লাগলো।
Pritom Das
4 মাস আগেসিনেমা নিয়ে এরকম তথ্য ভিত্তিক লেখা সচরাচর তেমন চোখে পরে না। ভালো লাগলো। অনেক কিছু জানা থাকলেও আরো অনেক কিছু নতুন জানলাম।
Pritom Das
4 মাস আগেসিনেমা নিয়ে এরকম তথ্য ভিত্তিক লেখা সচরাচর তেমন চোখে পরে না। ভালো লাগলো। অনেক কিছু জানা থাকলেও আরো অনেক কিছু নতুন জানলাম।
Pritom Das
4 মাস আগেসিনেমা নিয়ে এরকম তথ্য ভিত্তিক লেখা সচরাচর তেমন চোখে পরে না। ভালো লাগলো। অনেক কিছু জানা থাকলেও আরো অনেক কিছু নতুন জানলাম।
Pritom Das
4 মাস আগেসিনেমা নিয়ে এরকম তথ্য ভিত্তিক লেখা সচরাচর তেমন চোখে পরে না। ভালো লাগলো। অনেক কিছু জানা থাকলেও আরো অনেক কিছু নতুন জানলাম।
Pritom Das
4 মাস আগেসিনেমা নিয়ে এরকম তথ্য ভিত্তিক লেখা সচরাচর তেমন চোখে পরে না। ভালো লাগলো। অনেক কিছু জানা থাকলেও আরো অনেক কিছু নতুন জানলাম।
Pritam Das
4 মাস আগেসিনেমা নিয়ে এরকম তথ্য ভিত্তিক লেখা সচরাচর তেমন চোখে পরে না। ভালো লাগলো। অনেক কিছু জানা থাকলেও আরো অনেক কিছু নতুন জানলাম।