তিনটি নারীতে কিছুক্ষণ গল্প চলার পর উপস্থিত হলেন শবরপাদ। সঙ্গে গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী এক সুপুরুষ। শবর, সুশীলাকে উদ্দেশ করে সঙ্গী মানুষটির পরিচয় দিলেন—“এ হচ্ছে আমার শিষ্য লুই। নবগঠিত বাঙ্গালা ভাষায় অসাধারণ গান লেখে।”
সুশীলা শিহরিত হলেন। ইনিই লুইপা! এঁর গানই তো আজ সহজযানীদের মুখে মুখে ফিরছে—‘কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।/ চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।/ দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ...’ এঁকে দেখেই তো তিনিও পদ লিখেছেন, তবে তা প্রকাশ্যে আনেননি। নারীর পদরচনা মানুষ কেমনভাবে গ্রহণ করবে কে জানে! মানুষ জানে নারীরা বাল্য অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করলেই তাদের বিবাহ দেওয়া উচিত। নয়তো তারা নাকি বিপথগামিনী হতে পারে! সংসারের জোয়াল টানতে-টানতে পুত্রোৎপাদনই তাদের একমাত্র কর্তব্য। শাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। বয়সকালে তারা তাই রোগভোগ করতে-করতে কায়ক্লেশে জীবন কাটিয়ে মারা যায়।
১
শীতটা বড়ো জব্বর পড়েছে। দোলাইটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন সুশীলা। মাঘের শীতে নাকি বাঘও কাবু হয়ে পড়ে বলে দামোদর নদের তীরবর্তী এই লাঢ় অঞ্চলে প্রবাদ আছে। বঙ্গদেশে আসা ইস্তক একথা শুনছেন তিনি। তবে নারীদের দেহে মেদাধিক্য থাকায় শীতবোধ তাঁদের একটু কমই হয়। সুশীলা স্থূলাঙ্গিনী না হলেও এখন চল্লিশোর্ধা, তাই বয়সোচিত মেদলাবণ্যে তিনি আত্মবিশ্বাসী ও উজ্জ্বল। তাঁর কুটির থেকে অর্ধ যোজন দূরে শবরপা-র কুটির। যেতে যেতে সুশীলা দেখলেন, অপরাহ্নের মরণোন্মুখ সূর্য থেকে নির্গত পরাজিত বিষণ্ণ রশ্মিজাল মানভূম উপত্যকার ভয়ংকর শৈত্যকে প্রতিরোধ করতে পারছে না। চারিদিকে চূর্ণ শিলাময় বন্ধ্যা প্রান্তর। উপলব্যথিত সেই পথে এগিয়ে চললেন তিনি। কুটিরদ্বার উন্মুক্ত ছিল। সুশীলা কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেই দুই সুন্দরী নারী কলস্বরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “সিদ্ধাচার্য শবরপা কোথায়?” শবরপা-র জ্যেষ্ঠা পত্নী লোকি কপট উষ্মা দেখিয়ে বললেন, “কেন দিদি, আমাদের কি তোমার ভালো লাগছে না? আমাদের স্বামীই বুঝি শুধু তোমার আপন?”
সুশীলা সহাস্যে উত্তর দিলেন, “আরে, তোমরা আমার ভগিনী। তবে জানো তো শ্যালিকারা বোনের বাড়ি এলে জামাইয়ের সান্নিধ্যই বেশি প্রত্যাশা করে।”
তিনটি নারীতে কিছুক্ষণ গল্প চলার পর উপস্থিত হলেন শবরপাদ। সঙ্গে গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী এক সুপুরুষ। শবর, সুশীলাকে উদ্দেশ করে সঙ্গী মানুষটির পরিচয় দিলেন—“এ হচ্ছে আমার শিষ্য লুই। নবগঠিত বাঙ্গালা ভাষায় অসাধারণ গান লেখে।”
সুশীলা শিহরিত হলেন। ইনিই লুইপা! এঁর গানই তো আজ সহজযানীদের মুখে মুখে ফিরছে—‘কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।/ চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।/ দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ...’ এঁকে দেখেই তো তিনিও পদ লিখেছেন, তবে তা প্রকাশ্যে আনেননি। নারীর পদরচনা মানুষ কেমনভাবে গ্রহণ করবে কে জানে! মানুষ জানে নারীরা বাল্য অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করলেই তাদের বিবাহ দেওয়া উচিত। নয়তো তারা নাকি বিপথগামিনী হতে পারে! সংসারের জোয়াল টানতে-টানতে পুত্রোৎপাদনই তাদের একমাত্র কর্তব্য। শাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। বয়সকালে তারা তাই রোগভোগ করতে-করতে কায়ক্লেশে জীবন কাটিয়ে মারা যায়।
তাঁর সংবিৎ ফেরে লুইপা-র মধুর গম্ভীর কণ্ঠে—“প্রণাম গ্রহণ করুন ভদ্রে। সর্বত্র কুশল তো?”
সুশীলা ঈষৎ অপ্রস্তুত হাস্যে বললেন, “হ্যাঁ সিদ্ধাচার্য। আপনি কতদিন এ দেশে এসেছেন?”
লুইপা-র মুখের কথা প্রায় কেড়ে নিয়ে শবরপা বললেন, “এই তো কিছুদিন।” তারপর লুই-এর প্রতি দৃকপাত করে বলে উঠলেন, “জানো লুই, সৌরাষ্ট্রের রাজকুমার শান্তি, তাঁর মায়ের অনুরোধে রাজত্ব ত্যাগ করে মঞ্জুবজ্রসমাধির শিষ্যত্ব নিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। এখন তিনি মগধে বাস করছেন। দেখো, রাজার পুত্র যদি আমাদের এই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন তাহলে বৌদ্ধধর্মের অধুনা যে জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে তা থাকবে না। বরং বৌদ্ধধর্ম আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে।”
লুই বললেন, “একদমই ঠিক। শান্তিদেবের মতো উচ্চবংশীয় মানুষ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পথে এলে মানুষেরই উপকার। আর মহানির্বাণের পথে এগোতে গেলে সহজযান ছাড়া পথ নেই।”
“তুমি কি মনে করো যে সহজযান মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া উচিত? কেন-না আমাদের এ সাধনা গুহ্য থেকে গুহ্যতর। প্রকৃতি অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মিলনের মহাসুখই এই মার্গে মানুষকে নির্বাণের পথে নিয়ে যায়। একে হাটে মাঠে বাটে ছড়িয়ে দিলে...”
সুশীলা তাঁদের কথার মাঝে প্রবেশ করলেন—“যা মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে তাকে কুক্ষিগত করে রাখা কি খুব প্রয়োজন?”
তাঁর কথার কেউই উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। বরং নিজেদের মধ্যে তত্ত্বালোচনা প্রগাঢ় করার পথে অগ্রসরমান হলেন। লুই বললেন, “গুরুদেব, আপনিই ঠিক বলেছেন। নির্বাণপথ সকলের উপযুক্ত নয়। আমরা যদি...”
গৃহে প্রবেশ করলেন ভুসুকপা। শবর তাঁকেও যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন।
শবরের কনিষ্ঠা পত্নী গুনি ঈষৎ বিরক্তভাবে সুশীলাকে ডাকল—“দিদি পাশের ঘরে চলো। থাক ওরা ওদের তত্ত্ব নিয়ে।”
পাশের ঘরে গুনি জিজ্ঞাসা করল, “দিদি, আজ বলো না, তুমি কেন এই রুক্ষ দেশে পড়ে আছ নিজের ভাগীরথী তীরের সবুজ শ্যামল দেশ ছেড়ে? তুমি বোধহয় শবরপা-র আকর্ষণ এড়াতে পারছ না!” কথাগুলি বলেই গুনি খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।
সুশীলা কপট উষ্মা দেখিয়ে বললেন, “অসভ্য কোথাকার! নিজের স্বামীকে নিয়ে ওরকম বলে না। আসলে ওঁকে আমি মনে মনে গুরুপদে বরণ করেছি। এই যে ভাষাটিতে এখন ওঁরা কয়েকজন পদ রচনা করছেন, আমারও ভারি ইচ্ছে ওই বাঙ্গালা ভাষায় আমিও পদ রচনা করি। এই বাঙ্গালা ভাষা অত্যন্ত সুমিষ্ট। অনেকদিন আগে থেকেই এ ভাষা প্রাকৃতের খোলস ছেড়ে আপন রূপ ধারণ করতে চাইছিল। এবার কয়েকজন শক্তিশালী কবির হাতে তার যথাযথ স্ফূরণ ঘটল। আমিও চাই কবিখ্যাতি। কিন্তু সাধনার তত্ত্বাধিকারী না হলে আমার তো পদ লিখবার অধিকার জন্মাবে না। অথচ আমি নারী বলে শবরপা আমাকে শিষ্যত্ব না দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।”
“তুমি কাব্য লিখবে! মেয়েমানুষ কি কাব্য লিখতে পারে! তবে যে বলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়।”
“কেন, অসুবিধা কোথায়? নারী দেবীকে যদি পুরুষরা পূজা করতে পারেন তাহলে রক্ত-মাংসের নারীকে দীক্ষা বা শিক্ষা দিতে কিসের বাধা? আমি স্বচেষ্টায় এবং আমার পিতার উৎসাহে শিক্ষালাভ করেছি। আমার ইচ্ছা আরও নারীকে শিক্ষার আলো দেখাব। একজন নারী ছাড়া নারীকে কে বুঝবে, দেখবে বলো? পুরুষ? তারা তো সর্বদাই উচ্চমার্গের আলোচনায় ব্যাপৃত নয়তো কলহে লিপ্ত। আমাদের নারীদের উচিত নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব না করে সব...” কথা অসমাপ্ত রেখেই নিস্তব্ধ হলেন সুশীলা।
গুনি সাজতে বসল। আজ সে আর একটু পরে নাচবে। সুশীলা দেখছেন। তিনি নিজে স্বামী পরিত্যক্তা, কারণ তিনি তাঁকে পুত্রসন্তান উপহার দিতে পারেননি। সুশীলা অবশ্য জানেন না প্রকৃতই তিনি বন্ধ্যা না তাঁর স্বামী অনুর্বর। কিন্তু সমাজ এ প্রশ্ন তুলতে দেয় না। দোষী করা হয় নারীকেই।
স্বামীর ছায়ায় থাকতে পারেন না বলে তিনি কঠোর জীবন যাপন করেন। কেন-না প্রলোভন আর অত্যাচারের ভয় চতুষ্পার্শে। কিন্তু তিনি তো আসলে নারী। মুগ্ধনয়নে দেখছেন গুনির কেশবিন্যাস, হাত ও পায়ের অলক্তকের রঞ্জনী, অধরোষ্ঠে কুঙ্কুম লেপন...
লোকি ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙে, “তুমি পুথিও পড়েছ?”
“হ্যাঁ। কিন্তু সে-সবই সংস্কৃতে। এবার নিজের ভাষায়, আপনার প্রাণের এই বঙ্গভাষায় লিখতে চাই। লিখেওছি দুটি পদ।”
পাশের ঘর থেকে ডাক এল। এবার একটু নাচ-গান হবে। তার পূর্বে শবরের জ্যেষ্ঠা পত্নী লোকি সকলকে সামান্য খর্জুরতাড়ি আর শূল্যপক্ব বরাহ মাংস পরিবেশন করলেন, কেন-না সকলেই এখন ক্ষুধার্ত। খেতে-খেতে আবার আলোচনা জমে উঠল।
ভুসুকপা বললেন, “মাৎস্যন্যায় থেকে বঙ্গদেশ রক্ষা পেয়েছিল গোপালের নেতৃত্বে। কিন্তু আবার মনে হচ্ছে...” শবর দ্রুত তাঁর কথার পাদপূরণ করলেন, “হ্যাঁ, পাল সাম্রাজ্য এখন অস্তায়মান। পাল রাজা মহীপালদেব যথেষ্ট সাহসী বা শক্তিশালী নন। তিনি সিন্ধুরাজ মাহমুদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় রাজাদের হয়ে সংগ্রাম করেননি। অবশ্য এজন্য তিনি মাহমুদের আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।” ভুসুকপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ওদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ, গুর্জররাজের ভয়ে অবমাননামূলক শর্ত মেনে নিয়ে সিন্ধুরাজের সঙ্গে সন্ধি করছেন।”
লুইপা মৃদুস্বরে জানালেন, “রাষ্ট্রকূটরাজ! অথচ একদা রাষ্ট্রকূটরাজ ছিলেন ধ্রুবের মতো মহা পরাক্রান্ত শাসক। আর এখন!”
“যতদিন-না ভারতবর্ষের রাজারা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ত্যাগ করছেন ততদিন দেশের উন্নতি হওয়া সমস্যার। জানো, গান্ধারে যবনরা বহু বৌদ্ধ কীর্তি ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে! একটাই আশার কথা যে অতীশ দীপঙ্করের মতো মহাপণ্ডিত তিব্বতে গেছেন বৌদ্ধধর্মের প্রচারে।”
শবরপা জিজ্ঞাসা করলেন, “তাহলে তিনি নিশ্চয় তাঁর অমূল্য পুথিগুলিও সঙ্গে নিয়ে গেছেন? মনে হয় এই অব্যবস্থিত বঙ্গদেশে পুথিগুলি নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচল বুঝি।”
লোকি এইবার ঝংকার দিয়ে উঠলেন, “বলি, হল তোমাদের পান-ভোজন? ছোটো মেয়েটা কখন থেকে সেজেগুজে অপেক্ষা করছে নাচবে বলে!”
সত্যিই সুসজ্জিতা গুনিকে অপূর্ব লাগছে। পুরুষদের পাশাপাশি সুশীলাও মুগ্ধ নয়নে তাকে দেখছেন।
শবরপা বললেন, “ভুসুক, আপনার নতুন বাঁধা পদটিতে সুর যোজনা করেছেন তো? সেইটিই গান করুন। সঙ্গে গুনি নাচবে।”
ভুসুকের গম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠল—“ভবনঈ গহন গম্ভীর বেগে বাহীঁ/ দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী/ ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই...” এরই মধ্যে লুই হাতে তুলে নিয়েছেন সর্বক্ষণের সঙ্গী আড়বাঁশিটি, মর্দলে ঘা দিচ্ছেন শবর।
সদ্যযুবতি গুনি নাচছে। অপূর্ব সে-নাচ। এগিয়ে-পিছিয়ে, শরীরকে সাপের ন্যায় দোলায়িত করে, তার শরীরের বক্র রেখাগুলি সে ব্যবহার করছে মাধুর্য মেশানো চতুরতায়। পুরুষ কণ্ঠের গানে সাযুজ্য রেখে নাচকে সে করে তুলেছে দীপ্র। সুমিষ্ট অথচ ওজস্বিনী ভাষার সঙ্গে সমতা রেখে সে নৃত্য পরিবেশন করছে। সুশীলা বহুকাল পরে, কতকাল তাঁর নিজেরই মনে নেই, রোমাঞ্চ অনুভব করছেন। পুরুষ স্বভাবতই নারীর নাচে খোঁজে লাস্য। আর এক নারীই পারে অন্য নারীর দেহবল্লরীর ভঙ্গিমায় একাত্ম বোধ করতে। নারীই কেবল বোঝে নারীকে, তাই অনায়াসে সে স্বল্পালাপেও অন্য নারীর সামনে মেলে ধরতে পারে নিজস্ব গোপন কথার ডালি কিংবা দ্বিধা না করে তাকে সখ্যতার আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করতে পারে।
গান আর নাচ শেষ হল। কখন যে শীতসন্ধ্যা পা বাড়িয়েছে রাত্রির অভিমুখে, এতক্ষণ বুঝতে পারেননি কেউ। চারিদিকে বিপুল নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কেবল ঝিঁঝির ডাক।
সহসা নিস্তব্ধতা ভেঙে লুই বলে উঠলেন, “সাধু সাধু।”
শবর একটু ইতস্তত করে ভুসুককে উদ্দেশ করে বললেন, “কিন্তু এই গানটি তো...”
“ঠিকই ধরেছেন। এ গান আমার রচনা নয়। এটি চাটিল্লপা-র লেখা। উনিও এক সিদ্ধাচার্য। গানটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে বলেই এটি আজ গাইলাম। সম্প্রতি এই গানের এক নকল পুথি আমার হস্তগত হয়েছে। আমার গান আবার একদিন হবে।”
“কী সুন্দর কথাগুলি! গভীর ভবনদী গম্ভীরভাবে বইছে। তার দুই তীর কর্দমাক্ত, মাঝখানটির থই পাওয়া যায় না। এই ভবনদীর উপর পারাপারের জন্য চাটিল্ল সেতু গড়ার কাজে ব্যস্ত... সত্যি; এ যেন মানবজীবনেরই কথা। অপূর্ব লিখেছেন ওই কবি।”
লোকি গৃহাভ্যন্তরে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন তৈলদীপ। যেন রহস্যঘন আলো-আঁধারি পরিবেশ। উত্তুরে বাতাস কুটিরের ঝিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে কম্পিত করে তুলেছে আগুনশিখা। সুশীলা, লুইপাকে গোপনে চোখের কোণে দেখছেন। অকস্মাৎ লুইপা এদিকে ঘুরতেই চোখাচোখি হল আর যেন নিষিদ্ধ কাজ করে ধরা পড়েছেন এভাবে তাঁর উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন লজ্জারুণ সুশীলা।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
২
লুই আর সুশীলা মুখোমুখি বসে। উভয়ের মাঝে কুপির মৃদু আলো। শীতকাল ক্রমে অপস্রিয়মান, তবে বসন্তের আবির্ভাব এখনও ঘটেনি। এমনিতেই মানভূম উপত্যকা সজল শ্যামল নয়, তার উপর দীর্ঘ শীতের অবসানকল্পে প্রকৃতি এখন নিষ্করুণ, আভরণহীনা, অনেকটা স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা সুশীলার মতো।
সুশীলা নিজেই লুইকে আমন্ত্রণ করে এনেছেন তাঁর কুটিরে। এই মাসখানেকে তাঁদের পরিচয় প্রগাঢ় হয়েছে। সুশীলা-র উদ্দেশ্য তাঁর রচিত দুটি পদ লুইকে শোনাবেন। যদি লুই তাঁর লেখনীকে স্বীকৃতি দেন তবেই তিনি আপন পদগুলিকে প্রকাশ্যে এনে লিপিকরদের হাতে তুলে দেবেন।
রাত গভীরতার দিকে এগোচ্ছে। উভয়ের তত্ত্বালোচনার ফাঁকে সুশীলা বললেন, “আমি দুটি পদ রচনা করেছি নবগঠিত বাঙ্গালা ভাষায়। শুনবেন?”
“পদ রচনা করেছেন! আপনি! তবে আপনিই ভারতবর্ষে প্রথম মহিলা কবি। পড়ুন।”
সুশীলা নম্রভাবে প্রতিবাদ করলেন, “না, আমি প্রথম নই। আপনি নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষার কবি শীলাভট্টারিকার নাম বা পদের সঙ্গে পরিচিত?”
“ওহো, হ্যাঁ হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে ওঁর পদ বড়ো ব্যক্তিগত গন্ধ মাখা। আপনি নিশ্চয় সাধন ভজনের কথাই লিখেছেন?”
“তা লিখেছি। তবে শীলাভট্টারিকাও তো কত সুন্দর করে লিখেছিলেন—‘এই সেই তরুতল যেখানে তুমি আমার কৌমার্য হরণ করেছিলে, দেখো আজও সেই বৃক্ষ আর নদীতীর একই আছে, তুমি আর আমিও সেরকমই আছি, তবু আজকের মিলনে আমার কেন সেদিনের মতো আনন্দ বোধ হচ্ছে না!’
“হুম! পড়ুন।”
সুশীলা স্বরচিত একটি পদ পাঠ করতে শুরু করলেন—“নাড়িলে পুচ্ছই হরিণা বিমনা।/ দোঁহা...”
তাঁর পাঠের মাঝেই প্রশ্ন করলেন লুই—“দাঁড়ান, দাঁড়ান। এখানটায় কী লিখেছেন! ‘মাঁসে ধারণ মহাসুখ সংগম/ বিবশ করিলা পুরুঅ দৃঢ়তা’! এসব কী? মেয়েদের শরীরসুখ, পুরুষের উদাসীনতা, তার শরীরের দার্ঢ্য... এগুলির মধ্যে মহত্ব কোথায়? সাধন ভজন কই? আমাদের এই পদসমূহের ভাষাকে আমরা সন্ধ্যাভাষা রূপে অভিহিত করেছি। কারণ এতে লগ্ন হয়ে থাকবে সাধনার গুহ্য প্রকরণগুলি। সাধারণ জীবনের কী দাম?”
স্মিত হেসে সুশীলা উত্তর দিলেন, “মেয়েরা তো এমনিই লিখবে। তাদের যাপন, তাদের দেখা জীবন... ছোটো ছোটো তুচ্ছ বিষয় থেকে আনন্দ খুঁজে পাওয়া—এ তো নারীর নিজস্বতা। সেটাকেই আমি কাব্যে রূপ দিয়েছি। তা ছাড়া নারী অনেকাংশে বিব্রত আবার গর্বিতও থাকে তার দেহ নিয়ে। সে যদি কাব্যে তার নারীত্ব উপভোগ করতে চায় তাতে ক্ষতি কী? আর নতুন গড়ে ওঠা লেখ্য একটি ভাষাকে সকলের কাছে গ্রহণীয় করতে হলে সেটি বোধগম্য করেই তো লেখা উচিত। আমরা লিখতে বসেছি মানে ভাষাটির প্রতিও আমাদের দুর্বলতা আছে। প্রাকৃত-অপভ্রংশের খোলস ত্যাগ করে আমাদের নিজস্ব ভাষা এখন রূপ পরিগ্রহ করছে। আমরা তাকে গুরুত্ব দেব না? শুধুই কি গুহ্য তত্ত্বে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখব?”
“ক্ষতি বা ভাষার কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে কাব্যের এবং সাধনার উচ্চতার কথা। মোক্ষ, নির্বাণ—এসবের উদ্দেশ্য আর উপায় রেখে-ঢেকে বলাটাই দস্তুর। নাঃ, এভাবে বিষয়টাকে খেলো করে দিলে...”
“আসুন, কিছু শুষ্ক মহুয়া ফলের স্বাদ নিন। মনকে উচ্চমার্গ থেকে বাস্তবে আনুন।”
মহুয়া ফুল খেতে-খেতে চোখ রক্তাভ হয়ে উঠল লুই এর। তাঁর মত্ত মুখাবয়বের উপর কটাক্ষপাতে সুশীলা বুঝলেন লুই এখন তাঁর আসঙ্গলিপ্সার জন্য আকুল। কিন্তু তাঁর মন বিরূপ হয়ে আছে। ভেবেছিলেন, তাঁর রচিত পদগুলি শুনে মুগ্ধ হবেন লুই, দু-জনের একত্র আনন্দসন্ধ্যা যাপনে তিনি কাব্যরচনায় আরও উজ্জীবিত হবেন। আজ লুই তাঁর লেখার ক্ষমতা স্বীকার করে নিলে তিনি হয়তো লিপিকরদের হাতে তাঁর সৃষ্টি তুলে দিতেন। লিপিকররা নকল করে ছড়িয়ে না দিলে তাঁর লেখা দেশে দেশে কীভাবে পৌঁছবে! কবিখ্যাতি পাবেন ভেবে তিনি খুশিও ছিলেন। আজ লুইকে তিনিও চাইছিলেন। সোমরস ও কামরসের মিলনেই তো নির্বাণমার্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কিন্তু একী! লুই-এর এ কী ধরনের কথাবার্তা! ফলে লুই-এর প্রতি তাঁর সেই প্রাথমিক মুগ্ধতা অন্তর্হিত। নারী, অবমাননায় ধরা দিতে প্রস্তুত থাকে না।
লুই স্খলিত স্বরে তাঁকে কিছু বলছিলেন, হঠাৎ এক গর্জন শুনে দু-জনেই সচকিত হয়ে উঠলেন। কুটিরের কোণ থেকে লুই এর পার্শ্বদেশ থেকে ফণা তুলে সুশীলার প্রতিই যেন এগোতে চায় এক বিশাল বিষধর। লুই সন্তর্পণে সরে এসে সেই মহাসর্পের সম্মুখে তাঁর এক হাঁটু গেড়ে বসে অন্য হাঁটুটি নাড়াতে লাগলেন। সাপটিও তার তালে দুলছে। লুই কিছু শুকনো মহুয়া ফুল পাত্র থেকে তুলে ছুড়ে দিলেন সাপটির বামদিকে। সাপটি সেদিকে ঘুরতেই লুই ক্ষিপ্রগতিতে তার মাথা তালুবন্দি করলেন।
এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো লুই-এর কীর্তি দেখছিলেন সুশীলা। সন্ত্রস্ত কিন্তু সাহসী লুই-এর সবল শরীরের পেশির নড়াচড়া সাপের ফণার মতোই সম্মোহক। উত্তেজনায় পুরুষটির সারা শরীর ঘর্মাক্ত। আবার তাঁর নেশাগ্রস্ত মনে লুইপা-র জন্য আকর্ষণ জেগে উঠছে! বিশাল সাপটির দুই মাথা ধরে লুই বললেন, “এটি শঙ্খচূড়। এসব পাহাড়ি এলাকায় থাকে। তীব্রবিষ সর্প। এই দেখুন, এর কত বড়ো বিষদন্ত”—বলতে-বলতে সেই মহা বলশালী পুরুষটি সাপের মুখটি উঁচিয়ে ধরে সুশীলার প্রতি দু-এক পদ অগ্রসর হলেন।
ত্রস্তে লাফিয়ে পিছোলেন সুশীলা, “আপনার তো সাংঘাতিক দুঃসাহস! যদি সাপটি আপনাকে দংশন করত?”
হা-হা করে হেসে উঠলেন লুই—“ভয় পেলেন নাকি? আপনি তো জানেন বৌদ্ধ মঠে আত্মরক্ষার কৌশলও শিক্ষা দেওয়া হয়। সেসবের মধ্যে বিষধর সর্পকে নিয়ন্ত্রন করাও একটি শিক্ষা। আমি দীর্ঘকাল তিব্বত ও নেপালের গুম্ফায় শাস্ত্রের পাশাপাশি এসবও শিখেছি। দেখুন আজ কেমন কাজে লেগে গেল। এখন চলুন ভদ্রে, আপনার কুটিরের পিছনের জঙ্গলে এটিকে ছেড়ে দিয়ে আসি।”
“আমার কুটিরের পিছনের জঙ্গলে...মানে আবার যদি...”
“ভয় নেই। বেশ কিছুটা অরণ্যের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে তবেই এটিকে ছাড়ব, যাতে এদিকে আর না-আসতে পারে।”
লুই-এর বাম পার্শ্বে চলেছেন সুশীলা। তাঁর ভেতরটা গুরগুর করছে। কী বিশাল সর্প! এখানকার ভাষায় ‘রাজগোখরো’। যদি তাঁকে কামড়াত! লুই-এর অসমসাহস!
সুশীলা ভয়ে কুঁকড়ে থাকায় প্রায়ই সঙ্গী পুরুষটির দেহে তাঁর স্তন স্পর্শ করছে। একটি মাত্র চীরবাসের আবরণ তাঁর বিপুল ঊরু ও নিটোল স্তনকে যেন অন্তরালে রাখতে পারছে না।
সুশীলার কুটির পাহাড়ঘেঁষা। এই লাঢ়ভূমে আর যা-ই হোক, ছোটো-বড়ো টিলা বা পাহাড়ের অভাব নেই। ঢেউখেলানো সমতল প্রায় বৃক্ষবিহীন হলেও পাহাড়ের পাদদেশ থেকেই ঘন অরণ্যের শুরু। সেখানেই দু-জনে প্রবেশ করলেন। সুশীলার হাতে সেই কুপির আলো। তা পড়ে অরণ্যের নিবিড়তা যেন আরও ভয়ংকর মনে হচ্ছে। গা ছমছম করছে সুশীলার। বারবার তাঁর ইচ্ছে হচ্ছে লুই-এর হাত আঁকড়ে ধরতে। কিন্তু সংকোচ এবং একটু আগে তাঁর পদ সম্বন্ধে লুই এর বিরূপ মন্তব্য—দুই যুগপৎ নেতির আক্রমণে সুশীলার মন ঈষৎ বিপর্যস্ত। খানিক এগোনোর পর লুই সাপটিকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। মাটি পাওয়ার পরও সে একবার প্রায় বুকের উপর ভর দিয়ে ফণা তুলে সুশীলার প্রতি ক্রোধিত গর্জন করছিল। লুই সুকৌশলে একটি শুষ্ক বৃক্ষশাখার স্পর্শে সেটির গতিপথ পরিবর্তিত করে দিতেই সেটি জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। লুই, কিছুটা নিষ্প্রভভাবে সুশীলার দিকে দৃকপাত করে বললেন, “তবে আসি ভদ্রে।”
একঝলক উত্তুরে বাতাস সুশীলার শরীরে কাঁপুনি ধরাল। তিনি বুঝলেন, সুর কেটে গেছে। হয়তো মহাসর্পের উপস্থিতি, হয়তো নিজের দ্বিধা তাঁর মুখ-চোখে ফুটে উঠেছে।
৩
সুশীলার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে সাক্ষাৎ করে গেছেন লুইপা। তিনি তাঁর দেশ গঙ্গাতীরে ফিরে যাচ্ছেন। শবরপা-র নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ, পদ রচনা সবই করেছেন। এবার শবরপা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন আপন এলাকায় ফিরে গিয়ে সহজিয়া ধর্মের প্রচার করতে।
সুশীলার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। শবরপা তাঁকে দীক্ষা দেননি। বলেছেন, “এ পথ বড়ো বন্ধুর, এ নারীর পক্ষে অনুপযুক্ত।’’
সুশীলার মনে হচ্ছে, ভুসুকপা ঠিকই লিখেছিলেন, ‘অপনা মাঁসে হরিণা বৈরী’। তিনি আজ নারী না হলে তো এ সমস্যা হত না। বড়ো বাসনা ছিল সহজিয়া ধর্ম গ্রহণ করবেন, পদ রচনা করবেন। এ জীবনে সে-আশা আর পূর্ণ হল না। শবরপা প্রস্তাব দিয়েছিলেন কোনো সাধকের নর্ম-সহচরী হিসাবে জীবন যাপন করতে। সুশীলা সম্মত হননি।
বাবা-মা সাধ করে নাম রেখেছিলেন সুশীলা, একটি শিষ্ট মেয়ে হিসাবে জীবন পার করবে তাঁদের কন্যা, এই আশায়। “তোমাদের আশা পূর্ণ করতে পারলাম না, ক্ষমা কোরো তোমরা। তোমাদের মেয়ে প্রতিবাদই করে গেল সারা জীবনভর, তাই হয়তো তাকে অতৃপ্ত জীবনযাপন করতে হচ্ছে।”
যদি তিনি সহজযানে দীক্ষা পেতেন, মন-প্রাণ ঢেলে পদ লিখতেন, শিশু ভাষাটিকে মায়ের স্নেহ যত্নে স্বাবলম্বী করে তুলতেন। দিতেন মাধুর্য, তর্কের খর গতি, আবেগের ঝোড়ো বাতাস। তাঁর সন্তান হয়নি, এই ভাষাকেই তিনি সন্তানবৎ লালন করতেন। নারী তো সৃষ্টির আধার। তারাই তো পারে কাব্যের প্রকৃত ফুল ফোটাতে, কারণ তাদের মধ্যে আছে চূড়ান্ত আবেগের বিস্ফার, যা একটি সৃষ্টিশীল কাজ দাবি করে। তাদের মধ্যে আছে গড়ে তোলার ধৈর্য আর মমত্ব। শুধু পুরুষের জগতে প্রবেশাধিকার পেলেন না বলে স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল।
তবু তিনি মনে মনে সহজযানকে বরণ করেছেন, নিজেকে ভেবেছেন সহজিয়া। একদিন হয়তো কোনো নারী তার কবিত্বশক্তি প্রকাশের সুযোগ পাবে। তিনি নিশ্চিত তেমন দিন আসবে। তাঁর রচিত পদদুটি হাতে নিলেন সুশীলা। ভুর্জপত্রদ্বয় নিক্ষেপ করলেন জ্বলন্ত চুলায়। যাক, ওগুলো আর দরকার নেই। এই পুরুষপ্রধান সমাজ তাঁকে স্বীকৃতি দেবে না কিছুতেই। তখন পশ্চিম দিগন্তে নির্বাপিতপ্রায় সূর্য থেকে অঝোরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।
(লেখকের কৈফিয়ত: না, সুশীলা নামে কোনো কবি চর্যাপদের সময় কোথাও ছিলেন না; অন্তত ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর লেখার নমুনা যেটুকু দিয়েছি তা-ও লেখকের স্বকল্পিত। কিন্তু যদি বঙ্গভাষা সৃষ্টির আদি যুগে কোনো মানবী সহজিয়া সাধনের পথে গিয়ে কাব্যচর্চা করতে চাইতেন, তাহলে কেমন হত তাঁর চিন্তাভাবনা? কেমনভাবে তাঁকে গ্রহণ করতেন সমকালীন পুরুষ কবিরা? ইতিহাসের আধারে এই সুশীলা-র কাল্পনিক চরিত্র স্থাপন করে দেখতে চেয়েছি সেটাই।)
তথ্যসূত্র:
১. হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ভাদ্র ১৩৮৮ মুদ্রণ)
২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১১৮-১৯৭, (মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮২)
৩. নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব। (দে’জ পাবলিশিং, অষ্টম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪২০)
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
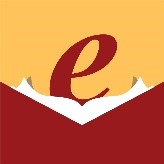

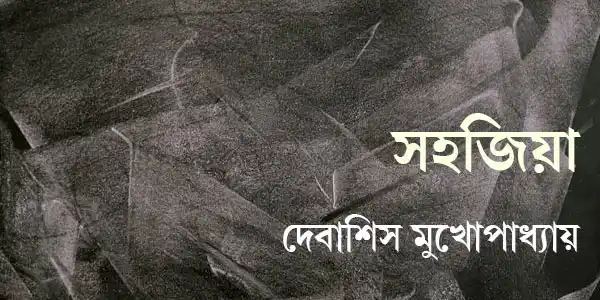
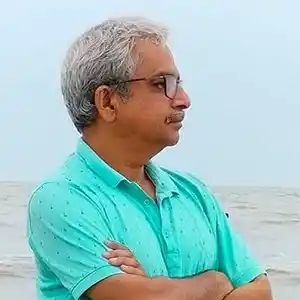



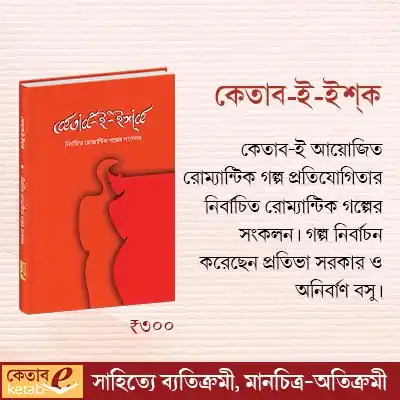
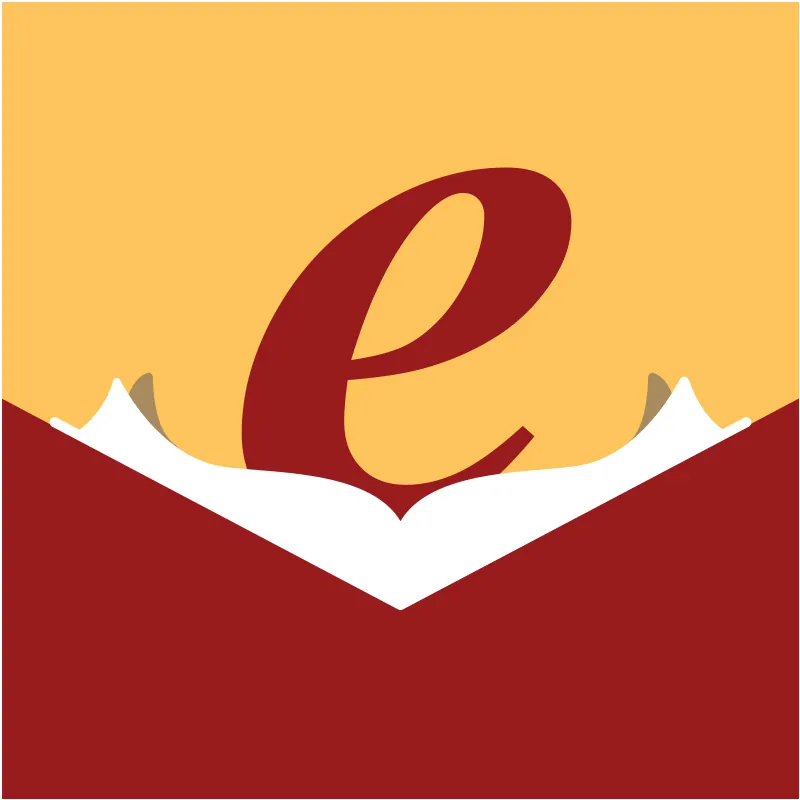
Debasis Mukhopadhyay
4 মাস আগে@Saswati Lahiri গল্প সম্পর্কে আপনার মতামতের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। এ ধরনের সমীক্ষা লেখক হিসেবে আমাকে অবশ্যই উৎসাহ দেয়।
Sagorika Goswami Banerjee. অপূর্ব লেখনী। বাংলা ভাষায় লেখক
4 মাস আগে@Debasis Mukhopadhyay
Debasis Mukhopadhyay
4 মাস আগে@Sagorika Goswami Banerjee. অপূর্ব লেখনী। বাংলা ভাষায় লেখক অনেক ধন্যবাদ।
Saswati Lahiri
4 মাস আগেসুন্দর , সংহত ও অতি বাস্তব আপনার কল্প - রচনাটি। সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে আপনার গল্পে বৌদ্ধ ধর্মের সহজযান - এর উল্লেখ, তৎকালীন চরিত্রগুলি, তাঁদের মননের প্রবণতা, নারীদের সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি সবই খুব চেনা ও পঠিত জন্যে লেখাটি মনকে তৃপ্ত করল। নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনার যে অনেকটাই পড়াশুনা রয়েছে সেটিও অনুভব করলাম। গল্পের কাহিনীর মাধ্যমে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে --- এক, বুদ্ধ পরবর্তী , সাধন প্রক্রিয়ার ছলে এই সহজযানের হাত ধরেই বৌদ্ধধর্মের মাৎস্যন্যায় দশা ও পতনের সম্ভাব্যতার প্রাক - ঘটমানতা, দুই, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের অবস্থানগত দিনযাপনে, নারীগণের অনুভব - ঋদ্ধ মহাসত্যের নির্মম অবদমন যা কিয়ৎপরিমানে আজও নেই নেই করে যথেষ্টই বিদ্যমান । লেখাটির জন্যে লেখক হিসেবে আপনাকে অভিনন্দন। নমস্কার ।