...এই নাম নিয়ে ওকে কেউ কখনো সম্বোধন করেনি। ছেচল্লিশ বছরে পৌঁছে বিগত যৌবনা হিসেবে নিজেকে ভাবতে অভস্ত্য হয়ে পরা রুপালির শিরায় শিরায় মৃদু সুনামির আভাস লাগল, ভিতরে ভিতরে শিরশিরানি, এই বয়েসে এসে যেটা খুব স্বাভাবিক হয়তো নয়, তবুও কেমন একটা শরীরী ভালোলাগা পেয়ে বসছিল নিজের অজান্তেই, সেই কম বয়েসে যেমন হত, কিংবা বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে পরে সৃজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় যেমন হত! আড়ষ্টতা ভেঙে আর কিছু লিখতে চায়নি রুপালি, সেদিনের মতো একদম বেরিয়ে এসেছিল ফেসবুক থেকে, লগ আউট করে।...
শুরু হল সুদীপ সরকারের দুই পর্বের উপন্যাসিকা ‘রামধনু’। আজ প্রথম পর্ব।
গতকাল একবারের জন্যেও মেসেঞ্জার খুলে দেখেনি রুপালি, পরশুদিন রাতে খানিকটা সময় চ্যাট করার পরেই লোকটা সেই যে লিখল কথাগুলো, তারপর থেকেই খানিক সিঁটিয়ে গেছে। ওকে এই নামে একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ ডাকেনি কোনোদিন। তাহলে ও কী করে এত সাবলীল ভাবে লিখে বসল, “তুমি আগের থেকেও আরও সুন্দর হয়েছ আপেল। তোমাকে দেখে এখন আমার ধারণা আরও পরিষ্কার হয়েছে, বয়েসের সাথে সাথে মহিলাদের গ্ল্যামার বাড়ে!” রুপালির জন্মের আগে ওর বাবা মা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল, ফেরার পরে পরেই নাকি মা কনসিভ করে, রুপালি হওয়ার পর ঠাকুমা নাম দিয়েছিল আপেল। তবে সেই নামে একমাত্র বাবা ডাকতেন ওকে, বাকিদের কাছে ও ছিল রুপু, রুপা ইত্যাদি। এই নাম নিয়ে ওকে কেউ কখনো সম্বোধন করেনি। ছেচল্লিশ বছরে পৌঁছে বিগত যৌবনা হিসেবে নিজেকে ভাবতে অভস্ত্য হয়ে পরা রুপালির শিরায় শিরায় মৃদু সুনামির আভাস লাগল, ভিতরে ভিতরে শিরশিরানি, এই বয়েসে এসে যেটা খুব স্বাভাবিক হয়তো নয়, তবুও কেমন একটা শরীরী ভালোলাগা পেয়ে বসছিল নিজের অজান্তেই, সেই কম বয়েসে যেমন হত, কিংবা বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে পরে সৃজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় যেমন হত! আড়ষ্টতা ভেঙে আর কিছু লিখতে চায়নি রুপালি, সেদিনের মতো একদম বেরিয়ে এসেছিল ফেসবুক থেকে, লগ আউট করে। তৃণা মাঝে মাঝে ফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে, আজকাল তো হোয়াটসঅ্যাপে স্যার ম্যাডামরা কমিউনিকেট করেন সবসময়, বন্ধুরাও নোট চালাচালি করে, তাই একদম ফোনে হাত দেবে না বললেও সমস্যা। মেয়ে বড়ো হয়েছে, ফেসবুক খুলে বসলে মায়ের চ্যাট চোখে পড়বে না সেই নিশ্চয়তা নেই। এদিকে সবসময় চোখ দিয়ে আগলে আগলে রাখাও সম্ভব নয়। চিনচিনে ভালোলাগার মধ্যেও কোথাও একটা বিরক্তিও ছিল বোধহয়, ফট করে চেনাজানা নেই, কোনো মহিলাকে এইসব লেখার মতো রুচি কেন হবে কোনো ভদ্রলোকের! তবে লোকটা খুব কাছ থেকে না জানলে ওর ‘আপেল’ নামটাই-বা জানল কী করে! ধন্দ নিয়ে সারারাত ভালো ঘুম হয়নি, অনেক ভেবেও লোকটা কে হতে পারে আন্দাজ করতে পারেনি রুপালি। নামের জায়গায় ‘আমি ইরোস’ আর ডিপি তে একটা গ্রিক পুরাণের ছবি দেখে পরিচয় জানার কোনো উপায় নেই। রুপালি জানে, ইরোস আসলে গ্রিক দেবতা, প্রেমের দেবী এফ্রদিতির পুত্র, নিজেকে গোপন রেখে এই ধরনের আলাপচারিতা মোটেই ভালো লাগে না ওর। গতকাল একবারের জন্যেও আর ফেসবুকে উঁকি দেয়নি রুপালি, কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠান ছিল কাল, এমনিতেই অনেক দায়িত্ব ছিল, সারাদিনের ধকলে আর এসব মনেও আসেনি সেভাবে। রাতে বিছানায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ রাতে বিছানায় শুয়ে অভ্যেসবশত আবার ফেসবুকে উঁকি দিল রুপালি। এই সময়টা নিজের মতো করেই কাটায় ও। তৃণা অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে, শুতে শুতে প্রায়ই রাত দেড়টা-দুটো হয়ে যায়, আর কিছুদিনের মধ্যেই পরপর পরীক্ষা রয়েছে। বাবা মা অনেক করে বুঝিয়েছে, “একবার নিট বা জয়েন্টটা ক্লিয়ার করতে পারলে তোমার সামনে সমস্ত এভিনিউ খুলে যাবে; ওয়ান্স ইউ সাকসিড, ইওর লাইফ ইস সেটেল্ড, এন্ড ইফ ইউ মিস দা অপারচুনিটি, ইউ মিস ইট ফর এভার।” তৃণা জানে, বাবা মায়ের প্রচুর এক্সপেকটেশান কিন্তু ও জানে ও নিজের মতো যা করার করবে, ডাক্তারি পড়ার মতো বোকামি আর কিছু হয় না, অন্তত দশ বছর না ঘষলে কিস্সু হবে না, শ্রেয়ার দাদা ডাক্তারি পাশ করে এখন অবসাদে ভুগছে, “ডাক্তারি পড়ে মেধাবি ছেলে-মেয়েরা শেষপর্যন্ত ওষুধ কোম্পানির তাবেদারি করছে, তাদের দয়ায় বিদেশ ভ্রমণ করছে আর ওষুধের দাম বেড়ে বেড়ে আকাশ ছুঁয়েছে, সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবে না, মানুষের ভালো করবে ভেবে কেউ ডাক্তার হয় না এখন, এটাই বাস্তব”, একদিন বলছিল রাকেশ। রুপালি বারণ করেছে এসব ছেলেদের সাথে মিশতে, এরা রাজনীতির মেটেরিয়াল, এদের ভাবনা মাথায় ঢুকলে সর্বনাশ। তৃণার যদিও ভালোই লাগে রাকেশের যুক্তিগুলো, ভুল তো কিছু বলে না তেমন। মাঝে মাঝে একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে এই যা, তখন মনে হয় সব কিছুই পালটে ফেলতে চায় ওরা, ভ্রান্ত সমাজব্যবস্থা থেকে শুরু করে পড়াশোনার চলতি মডেল, সব কিছু। মায়ের কথামতো কারুর সাথে বেছে বেছে মেশা যায় না, আর রাকেশ ছেলেটা এমনিতে বেশ ভালো, দিলখোলা, পরোপকারী, তৃণা এত বাছবিচার করতে পারে না, বাড়িতে অবশ্য এসব নিয়ে আলোচনা করে না কখনো। বিছানায় শরীর এলিয়ে স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে আলতো করে চাপ দিল রুপালি, রোমাঞ্চকর একটা অনুভূতির স্বাদ পাওয়ার আশায় মেসেঞ্জারে উঁকি দিল সচেতনভাবেই। ইরোস যেন অপেক্ষায় ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই স্ক্রিনে ফুটে উঠল লেখাগুলি, “কাল তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, জানি তুমি টায়ার্ড ছিলে, তবু ভাবলাম, যদি অনলাইন হও। যাক, কাল কলেজে যাওয়ার সময় দেখলাম তোমাকে, সত্যি, কী দারুণ লাগছিল, টিয়া রঙের শাড়িতে যেন গড অফ লাভ…।” রুপালির ভিতরে সুনামি আছড়ে পড়ল, পুরো শরীরটা একবার উত্তেজনায় কেঁপে উঠল বোধহয়, কী এক অদ্ভুত ভালোলাগায় ভেসে যেতে ইচ্ছে করল, তাহলে কি এখনও যথেষ্ট আবেদন আছে ওর? সৃজন তো আজকাল নিজের কাজ নিয়েই আত্মমগ্ন থাকে, বউকে দেওয়ার মতো সময় নেই বললেই চলে! তা ছাড়া সৃজন ঠিক তেমন মানুষও নয়, ওকে বহিরঙ্গের রূপের থেকে অন্তরের মাধুর্য বেশি আকর্ষণ করে। শিল্পী মানুষের দেখার চোখ আলাদা, সাধারণের থেকে অনেকটাই ভিন্ন তার প্রকারভেদ। শরীর যেন আড়মোড়া ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছে, নিজেকে সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবল রুপালি, তারপর লিখল, “আপনার এই ধরনের কথায় আমি খুবই বিরক্ত হচ্ছি। কিন্তু সবার আগে বলুন আপনি কে? আপনি কি আমাকে ফলো করছেন? আপনার উদ্দেশ্য কী?”
তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল ইরোস, “আরে আরে, আমি তো তোমার গুণমুগ্ধ ইরোস, এই যে তুমি আপেলের মতো মিষ্টি, সেটা বললে কি ভুল বলা হয়? তুমি শিক্ষিত, জানো তো, আই এম দা গড অফ লাভ, আমি সৌন্দর্যের পূজারি। হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করতে পারি তোমার জন্যে, সমস্যা হল, আমি জীবনানন্দের মতো কবিতা লিখতে পারি না, নইলে একশো কবিতা লিখে ফেলতাম তোমায় নিয়ে।” রুপালির হাত কেঁপে উঠল একবার, কিছুদিন আগে একবার সৃজন কাছে আসতে চেয়েছিল, রাজি হয়নি রুপালি, এখন আর এসব ভালো লাগে না তেমন, শরীর ঝিমিয়ে গেছে ভিতরে ভিতরে। সৃজন কিছু মনে করেনি, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কুড়ি বছরের দাম্পত্যে আর অবশিষ্ট আছেই-বা কি! অথচ এক অচেনা আজানা লোকের সামান্য ইশারায় শরীর নদীর কূলে কূলে জোয়ারের হাতছানি! তবে কি মন সাড়া দিচ্ছে বলেই শরীরময় ঢেউয়ের আভাস? শরীর বলে আসলে কিছু হয় না, মনই সব? একবার ঘাড় ঘোরাতে নজরে এল, সৃজনের ঘরে আলো জ্বলছে এখনও, কাজ করছে মানুষটা, রিডিং রুমে তৃণা পড়ছে নিশ্চয়ই, এই পাগলের পাল্লায় পরে আজকের ঘুমটাও মাটি হবে নিশ্চিত, সব রহস্য এত তাড়াতাড়ি উন্মোচন হওয়ার দরকারই-বা কি; কোনো উত্তর না দিয়ে লগ আউট করল রুপালি।
নতুন কাজে হাত দেওয়ার আগে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করে সৃজন, বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কাজ করলে তাতে ভাবনার প্রতিফলন আসে না, কাজের স্বকীয়তা বজায় থাকে না। নতুন ব্র্যান্ডিং-এর কাজটা নিয়ে ও বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে। কাজটার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ আছে, গতানুগতিক প্রোডাক্ট ব্র্যান্ডিং-এর মতো নয় বলেই, সৃজন নিজেও এটাকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। এড এজেন্সিগুলো নিজেদের মধ্যে যেভাবে রেষারেষি করে তাতে কাজের মান এবং উৎকর্ষতা কোথাও হয়তো পিছনের সারিতে চলে যায়, চটকদার জিংগল বা উন্মুক্ত নারী শরীরের ছবি দিয়ে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতেই সবার আগ্রহ। সৃজন কিছুটা ব্যাতিক্রমী কাজ করতে পছন্দ করে, এই বয়েসে এসে ওর কাছে অর্থের চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষের পরিতৃপ্তি। একটা সময় ছিল যখন ওর সমস্ত কাজের প্রাথমিক বিশ্লেষণ করত রুপালি; ছবির আঙ্গিক, ভঙ্গিমা এবং তার পরিমিতি বোধ পর্যন্ত সব কিছুই খুঁটিয়ে দেখত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। সৃজনের সৃষ্টিশীলতায় মুগ্ধ হয়ে যেত রুপালি, কত স্বাভাবিক অথচ দৃঢ় ওর ক্যাচলাইন, এড এজেন্সিগুলো রীতিমত হত্যে দিত সৃজনের সময়ের জন্য, ও তখন ফ্রিল্যান্সিং করতেই স্বচ্ছন্দ ছিল। কিন্তু বিয়ের আগে শশাঙ্কবাবুর বেশ সংশয় ছিল, মেয়ের জীবন নিয়ে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষপাতী নন তিনি, বাবা হিসেবে মেয়ের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবা তো স্বাভাবিক; ছেলে যত ভালোই হোক, ধরাবাঁধা চাকরি না করলে চলে? রুপালি বেঁকে বসেছিল, “বিয়ে করলে ওকেই করব, সারাজীবন একঘেয়ে দশটা পাঁচটার চাকরি তো সবাই করে, সৃষ্টিশীল মানুষ ক-জন হয়? তা ছাড়া, ওর মান্থলি ইনকাম যে-কোনো উচ্চ পদে কাজ করা সরকারি আধিকারিকের চাইতে বেশি। অসুবিধা কোথায়!” বাড়িতে অভিভাবক হিসেবে ঠাকুমা প্রভাবতী সায় দিয়েছিলেন, ছেলেকে বুঝিয়েছিলেন, “দেখ বাবা, রুপু কে ছোটো থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, ও যেটা চাইছে সেটাই হোক, ওর বিচার বোধের ওপর আমার পুরো ভরসা আছে।” এদিকে মেয়ের মুখে এমন যুক্তি শুনে অনেকেই ভেবেছিল বিয়েটা বোধহয় ও নিজেই ঠিক করেছে। রাঙামাসি তো কানাঘুষো শুরুও করে দিয়েছিল, “রুপালি যে তলে তলে এই ছোকরার সঙ্গে প্রেম করত আমি আগেই বুঝেছি।” বড়োমামা প্রতিবাদ করেছিল, “বাজে কথা বলা তোদের অভ্যেস হয়ে গেছে। যোগাযোগ করলাম আমি আর তোরা সব জেনে ফেললি এর মধ্যেই? আমার কলিগ আশুতোষের খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে সৃজন, যেটুকু জেনেছি, একদম খাঁটি ছেলে, আর্ট কলেজের কৃতি ছাত্র, মেধাবী এবং বিরাট সম্ভাবনাময় আর সব থেকে বড়ো কথা খুব ভদ্র এবং রুচিশীল। প্রেম করার মধ্যে আমি কোনো কিছু খারাপ দেখি না, তবুও এটা বলতেই হয় যে প্রেম করে বেড়ানোর মতো মেয়ে আমাদের রুপালি নয়।” বিয়ের তোড়জোড় চলতে-চলতেই রুপালি নিজেও কলেজের চাকরিতে ঢুকে পড়েছিল। বউয়ের চাকরি নিয়ে দ্বিধা ছিল সৃজনের মায়ের, “চাকরি-বাকরি নিয়ে থাকলে ঘর-সংসার করবে কখন? তা ছাড়া আমাদের তো অভাব কিছু নেই, দরকার টা কী?” সৃজন মায়ের সাইকোলজি ফিলসফি ভালো বোঝে, মাকে বুঝিয়ে রাজি করাতে অসুবিধে হয়নি তেমন, “পড়াশোনা করা মেয়েরা ঘরে বসে থাকলে সেটা সম্পূর্ণভাবে ওয়েস্টেজ অফ পোটেনশিয়াল, আর কলেজের চাকরি কেউ ছাড়ে নাকি? সময় তো অনেক এগিয়েছে মা, তোমার চিন্তাভাবনা তো এমনিতে অনেক প্রগতিশীল, তাহলে কেন…” এর পরে আর আপত্তি করেননি মা। বিয়ের পরে পরে কয়েকটা বছর কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে কেটেছে সৃজনের, হয়তো অনেকেরই তা-ই হয়, কিন্তু ওই কয়েকটা বছরে ওর শিল্পীসত্তার চূড়ান্ত বিচ্ছুরণ ঘটেছিল, অসাধারণ কিছু কাজ করেছিল সৃজন। এড এজেন্সির বাইরে এসে শিল্পী হিসেবে ছবি নিয়ে কাজ করার তাগিদ জুগিয়েছিল রুপালি। ওর উৎসাহে বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে নিয়মিত প্রদর্শনী করা শুরু করেছিল সৃজন। মুম্বাই, জয়পুর বা দিল্লীতে এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে ওপার বাংলার ঢাকাতেও প্রদর্শনী করেছে সৃজন। সব জায়গায় যেতে না পারলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঙ্গে থেকেছে রুপালি। গত একুশ বছরে অনেক কিছুই বদলেছে, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি পালটেছে, ভাবনার বিন্যাস ওলটপালট হয়েছে, সৃষ্টিশীলতার পরতে পরতে জমেছে পলি, সৃজন এখন এড এজেন্সির নিশ্চিন্ত চাকরিতে স্থিতধী। রুপালি নিজের কলেজ, গবেষণা আর তৃণাকে নিয়ে ব্যস্ত, সৃজনের কাজ নিয়ে এখন আর ভাবনার সময় নেই। তৃণা এবার উচ্চ মাধ্যমিক দেবে, মেয়ের যা মেধা তাতে নিট ক্র্যাক করা উচিত, শহরের দামি কোচিঙে পড়াতে কোনো কার্পণ্য করেনি সৃজন। রুপালি চায়, মেয়ে ডাক্তার হোক, মেয়েদের ডাক্তারি প্রফেশানটা বেশ ভালো লাগে ওর। স্টিরিয়োটাইপ সাবজেক্ট নিয়ে কলেজে পরে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, রুপালি জানে, কলেজে পড়াশোনার মান, গবেষণার উৎকর্ষতা সব কিছুই এখন নিম্নমুখী, জীবনে সফল হতে গেলে, প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে বিস্তর লড়াই করতে হবে মেয়েকে।
২
দুপুরের দিকে রেস্তোরাঁটায় তেমন ভিড় নেই। উইকেন্ডে নিশ্চয়ই এত ফাঁকা থাকে না, সপ্তাহের মাঝখানে, কাজের দিন হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই লোক কম। একটা টেবিল বুক করে বসেছে রাকেশ, ঋতু, তৃণা, দোলা আর বুদ্ধ। স্কুলের ফেয়ারওয়েল শেষ করেই ওরা চলে এসেছে এখানে। আজ অনেকটা সময় নিয়ে আড্ডা দেবে ওরা, স্কুলের শেষে কে কোথায় চলে যায় তার ঠিক কি! রাকেশ যেমন ঠিক করেই ফেলেছে, অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করবে, তারপর রাজনীতির পাঠ নেবে হাতে-কলমে। কলেজের ছাত্র সংসদ থেকেই তো ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতাদের উত্থান। ও বন্ধুদের প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, “সারা দুনিয়া কিসের ভিত্তিতে চলে বলত?” রাজনীতি নিয়ে ওর উৎসাহ, সমাজব্যবস্থা নিয়ে ওর ভাবনা সবার জানা, সবাই তাই নির্দ্বিধায় উত্তর দেয়, “রাজনীতির নিয়মে দুনিয়া চলে।” রাকেশের বক্তব্য খুব স্পষ্ট, “তোরা ভুল বলছিস, অর্থনীতির নিয়ম মেনে সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়, রাজনীতি নিজেকে সেই নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। সুতরাং অর্থনীতি না জানলে, রাজনীতির এ বি সি ডি বোঝা মুশকিল।” ওর কথা তৃণা চট করে বুঝতে পারে না, হেসে বলে, “এত কঠিন কঠিন কথা কী করে বলিস বলত? কথার মারপ্যাচ আর কী সব জাগরণ, বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদ আরও কী সব বলিস!” ঋতু ফুট কাটে, “এই বয়েসেই দাস ক্যাপিটাল, চে গুয়েভারা পড়ে ফেলেছে ছেলেটা, ওর মাথায় শুধু শ্রেণি সংগ্রাম আর বুকে বিপ্লবের স্বপ্ন।”
“বাজে বকিস না, দাস ক্যাপিটাল পড়ার সময় পেলাম কই; তবে পড়ার ইচ্ছে আছে সেটাও সত্যি, কখনো সুযোগ পেলে পড়ার চেষ্টা করব বটে, তবে আমি কোনো দলবাজির মধ্যে নেই ভাই, রাজনীতির পাঠ নিতে গেলে পড়তে হয়, বুঝতে হয়, জাস্ট সেটাই করার চেষ্টা করি। এই দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থা বদলে দিতে হলে, সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হলে গতানুগতিক ধরাবাঁধা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। বামপন্থা বা দক্ষিণপন্থা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল মানুষ, মানুষের ন্যূনতম অধিকার সুরক্ষিত রাখাটাই সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ, এটাই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে এই স্থবিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সবাইকেই দায়িত্ব নিতে হবে, শুধুমাত্র সমাজ কর্মীরা লড়াই করবে আর তোমরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে শুধু কাড়ি কাড়ি টাকা রোজগার করবে, সেটা হবে না। সম্পদের অসম বণ্টন থেকেই তো বিভাজনের সূত্রপাত, শ্রেণী শত্রুর জন্ম।” তৃণা গলা নামিয়ে বলল, “আমি একেবারেই ওইদিকে যাচ্ছি না, বাবা-মা জোর করে আমাকে ডাক্তার বানাতে চাইছে, আমি কী চাই-না-চাই সেটা একবারও জানতে চাইল না ওরা। শুধু শুধু একগাদা টাকা নষ্ট করে দামি কোচিং সেন্টারে ভরতি করে দিল।” ঋতু ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “তুই তাহলে কী করবি ভাবছিস? আমরা তো সবাই জানি তুই ডাক্তারি পড়বি। আঙ্কেল আর আন্টি তো তোর পড়াশোনা নিয়ে বেশ কনসারন্ড।” “আমার মা বাবার কথা বেশি না বলাই ভালো”, বলল তৃণা, “দুটো মানুষ, কোনো ব্যাপারে মিল নেই অথচ বিশটা বছর কেমন একসাথে কাটিয়ে দিল ভেবে অবাক লাগে! মা আমাকে নিয়ে যত-না ভাবে তার থেকে বেশি ভাবে সোশ্যাল স্ট্যাটাস নিয়ে, মেয়ে ডাক্তার হলে সামাজিক সম্মান বাড়বে বলেই মায়ের বিশ্বাস। ইটস নট দ্যাট ডক্টরস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারস আর দা অনলি সাকসেসফুল পিপিল ইন ওয়ার্ল্ড। এই কথাটা মাকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না। সোজা কথা, এই rat রেসে আমি নেই, নিট ফিট সব দেব কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ছাড়া। এত গাঁতিয়ে পড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু মাকে বলে কোনো লাভ নেই। বাবা নিজের পেইন্টিং, অফিসের এসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত, আমার কথা কে শুনবে? আমার ভবিষ্যৎ প্ল্যান মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি, টুয়েলভের পর মিডিয়া সাইন্স নিয়ে পড়ব, সিনেমাটোগ্রাফি, জারনালিজ়ম সব নিয়ে নতুন মডিউলে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স। বেসিকালি প্রফেশানাল কোর্স কিন্তু রেলিভ্যান্ট। শ্রেয়ার দাদার কথা জানিস তো, ডাক্তার হয়েও কি চূড়ান্ত ফ্রাস্ট্রেশান! তাহলে কি লাভ বল?”
রাকেশ মুচকি হাসল, চশমাটা মাথার ওপর তুলে বলল, “তুই তো একদম আমাদের আগের ইয়ারের দেবমাল্যদার মতো বলছিস, ও বেচারির একদম হাঁসফাঁস অবস্থা, অঙ্ক ভালো লাগে না, ইনফ্যাক্ট মাথায় ঢোকে না, কিন্তু বাড়ির চাপে ইঞ্জিয়ারিং পড়তে গেছে বেঙ্গালুরুতে। বাবার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সামলাতে হবে তাই ইঞ্জিনিয়ার না হলে চলবে কেন! ফাস্ট ইয়ারেই ফেল করতে করতে কোনোক্রমে উতরেছে ছেলেটা কিন্তু ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে এই ইঁদুর দৌড়ে ছোটার পরিণতি যে কী ভয়ংকর হতে পারে সেটা ভাবছে না ওর বাবা মা। অন্যদিকে ডাক্তারি এখন আর নোবেল প্রফেশান নেই, স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোটাই ব্যাবসায়ীদের দখলে চলে গেছে। উই আর অনলি গিনিপিগস নাউ।”
ঋতু তৃণার বাড়িতে প্রায়ই যাওয়া আসা করে, দু-জনে একসাথে কোচিং সেন্টারে পড়তেও যায়। মেয়ের বন্ধুদের কয়েকজনকে চেনে রুপালি কিন্তু ঋতু ছাড়া বাকিরা খুব একটা বাড়িতে আসে না। ওর নম্বর নিয়ে রেখেছে রুপালি, বলা যায় না, কখন কী দরকার পরে, আজকালকার ছেলে-মেয়েদের কোনো ভরসা নেই, এই বয়েসটাও খুব গোলমেলে। মেয়েকে চোখে চোখে রাখাটা জরুরি, তবে কলেজ বাড়ি সব একসাথে সামলানো সহজ নয়। তা ছাড়া নিজের জন্যেও কিছুটা স্পেস রাখতে হয়, সব সময় মেয়ের ওপর চোখ দিয়ে বসে থাকা অসম্ভব। উলটোদিকে সৃজন আবার মেয়েকে কিছুটা ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী, “সবসময় আগলে রাখলে ও বড়ো হবে কী করে! ওকে জগতের ভালো-মন্দ বুঝতে দিতে হবে তো নাকি!” রুপালি আন্টিকে বেশ লাগে ঋতুর, ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব, স্মার্ট, কলেজে পড়ান, এককথায় পুরো একমপ্লিশড উওম্যান! কথায় কথায় ঋতু জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা তোদের বাড়ির সেই ছেলেটা, সানি না কী নাম যেন, কী খবর রে?”
তৃণা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে তাকাল ঋতুর দিকে, ভ্রূ কুঁচকে বলল, “আমাদের বাড়ির ছেলেটা মানে? সানি আমাদের কাজের মাসির ছেলে। তোর আবার তার খবরে কী দরকার?”
“না, রুপালি আন্টি একদিন বলেছিল, ছেলেটা না কি পড়াশোনায় খুব ভালো। আমাদের সঙ্গেই টেন প্লাস টু কমপ্লিট করবে”, বলল ঋতু।
“হ্যাঁ, আমিও তা-ই জানি, আর মা তো মাঝে-মাঝেই তুলনা টেনে বলতে থাকে এর তার কথা, বিরক্ত লাগে জানিস তো! কাজের মাসির ছেলে যদি আমার থেকে ভালো রেজ়াল্ট করে বসে তাহলে মুখ দেখাতে পারবে না বলে মায়ের চিন্তা বেশি।” এক ঢোঁক জল খেয়ে বলল তৃণা।
এই নিয়ে আর কথা বাড়ায় না তৃণা, ও জানে সন্ধ্যা মাসির ছেলে সানি পড়াশোনায় বেশ ভালো, দুই-একবার দেখেছে ছেলেটাকে। খুব লাজুক টাইপ, একবার সন্ধ্যা মাসির শরীর খারাপ হয়েছিল, আসতে পারবে না বলে খবর দিতে এসেছিল ওদের বাড়িতে। রুপালি রাগের চোটে বেশ কিছু কথা শুনিয়েছিল কিন্তু ছেলেটা কোনো উত্তর করেনি, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। ছেলেকে নিয়ে সন্ধ্যা মাসির বেশ গর্ব, সানি নাকি ধরণী সেন বয়েস স্কুলের ফার্স্ট বয়। কেউ ভালো করলে তৃণার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা হল, যখন-তখন রুপালি এই নিয়ে কথা শোনাতে শুরু করে। এদিকে সানিকে রুপালি মোটেই পছন্দ করে না, সেটা হাবেভাবে বোঝে তৃণা। সন্ধ্যা মাসিকেও মা খুব একটা ভালো চোখে দেখে না, জানে ও।
“এদের জীবনে স্যাঙ্কটিটি বা চ্যাস্টিটি বলে কিছু নেই, যখন-তখন যার-তার সঙ্গে…। মেয়েটার স্বভাব একদমই ভালো না, একটা বিহারী ছেলের সঙ্গে এদিক-ওদিক চলে যায় মাঝে-মাঝে। ছেলেটা বোধহয় খালাসি বা ড্রাইভার কিছু হবে, ওর খাইখরচা, সাজগোজের খরচ দেয়, ব্যাস তাতেই খুশি। অথচ দেখো, ওর বর নিতাই লোকটা কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ, ব্যবহারও বেশ ভালো, ফোন করলে চলে আসে, নিয়ে যায় আমাকে ওর রিকশায় করে; দোষের মধ্যে একটাই, ব্যাটা গাঁজা টেনে পড়ে থাকে অর্ধেক সময়। দু-জনের বয়েসের ফারাকটাও বোধহয় একটু বেশি। সন্ধ্যা যেমন তড়বড়ে মেয়ে, জোয়ান বয়েস, ও আর আটকে থাকে? তবে এত বড়ো ছেলে থাকতে এই সব মেনে নেওয়া যায় না।” রুপালি একদিন বলছিল সৃজনকে, তৃণা শুনেছে। সৃজনের ভাবনা খানিক আলাদা, রুপালির সঙ্গে একমত হয়নি ও, “শোন, এই স্যাঙ্কটিটি, পিওরিটি ব্যাপারগুলো রেলেটিভ, কোন পারস্পেক্টিভে দেখছ তার ওপর নির্ভর করে। এই যেমন ধর, শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট ভার্যা নিয়ে কত গবেষণা, এদিকে সেই রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতীদের পিছনে ফেলে দিল রাধা যে কিনা আবার আয়ান ঘোষের বৈধ স্ত্রী। অথচ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে কতভাবে, কত যুগ ধরে গ্লোরিফাই করে আসছি আমরা। অন্যদিকে দ্রৌপদী তার পাঁচ-পাঁচটা স্বামীকে নিয়ে ঘর করছে, প্রত্যেকের ঔরসে তার গর্ভে একটি করে পুত্র সন্তান, পঞ্চপাণ্ডব যে যখন এই রমণীকে স্বামী হিসেবে পেল, সে তখন পূর্ণ সামাজিক অধিকারে তার রূপ যৌবন ভোগ করল। সুতরাং, বেদব্যাস-এর অন্তত স্যাঙ্কটিটি বা চ্যাস্টিটি নিয়ে ছুঁতমার্গ ছিল বলে মনে হয় না। আসলে বিবাহ নামক ইন্সটিটিউশানটি সমাজ গঠনে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে বলে আমরা এইভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই এক্ষেত্রে সন্ধ্যার কোনো দোষ আমি দেখছি না। ওর মন যা চায়, যাকে চায় তার সঙ্গে সময় কাটানোর অধিকার আছে বই-কি! ধরো এর মধ্যে যদি শুধু শারীরিক ব্যাপারটাই থাকত, তাহলে তো ও কোনো গুজরাতি মাড়োয়ারি বা উড়িয়া ছেলের সঙ্গেও ঝুলে পড়তে পারত, ওই বিহারী ছেলের সঙ্গে জুড়ে আছে মানে কোথাও একটা মনের টান আছে সেটা অস্বীকার করা যাবে না।” রুপালি বিরক্ত হয়ে উঠে পড়েছিল, সৃজনের ভাবনাচিন্তা কোনোদিনই ওর সঙ্গে মেলে না। তৃণা বাবার সব কথা বোঝেনি, কিন্তু কান খাড়া করে শুনেছে সবটা। মেয়ের সামনে খোলামেলা আলোচনা করতে রুপালি ইতস্তত করে কিন্তু সৃজনের এই নিয়ে অত ঢাকঢাক গুরগুর নেই, ওর সাফ কথা, ‘মেয়ে বড়ো হয়েছে, আতুপুতু অনেক হয়েছে, এবার ওকে বড়ো হতে দাও, দিস আর হার্ড রিয়ালিটিস, শি শুড নো।’
তৃণাকে থামিয়ে রাকেশ বলল, “তবে আমার ভাই বাড়িতে কোনো চাপ নেই, ইকনমিক্স পড়ব, সেই সিদ্ধান্ত আমার নিজের, ইঁদুর বাঁদর হওয়ার কোনো শখ আমার নেই, আমি কোনো রেস-এর মধ্যে নেই।”
বুদ্ধ মুখ খুলল এবার, হাতজোড় করে বলল, “ভাই, তোর বাবার মতো ক্যাপিটাল থাকলে আমিও বলতাম আমার বাড়িতে কোনো চাপ নেই। যতই পালটে দেব, বদলে দেব বলিস না কেন, ভবিষ্যতে বাবার বিশাল ব্যাবসা তো সামলাতে হবে তোকেই, তখন ওই পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী মার্কা ভাষণগুলো ঝাড়তে পারবি তো? সবার তো বাবার ব্যাবসা নেই, আমাদের কিছু একটা জোটাতে হবে, নাহলে খাব কি?”
“আমি চাইনিজ খাব”, মাঝে পড়ে বলল দোলা, “এবার তোরা খ্যামা দে, এখানে শুধু গ্যাঁজালে বসতে দেবে না, অর্ডারটা কর তাড়াতাড়ি।” রাকেশ তাকাল বুদ্ধর দিকে, গলা নামিয়ে বলল, “বস, বিয়ার হবে তো? আবার কবে বসা হবে কে জানে! কে কোথায় ছিটকে যাব!”
“একদম, ওই জন্যেই তো এলাম”, বলল বুদ্ধ, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, “তোরা নিবি তো? দু-গ্লাসের বেশি পাবি না কিন্তু! আর মনে রাখিস, আমরা কিন্তু সবাই এইটিন প্লাস, আঠেরোর নীচে আবার লিকার সেল করার নিয়ম নেই।” চাপা হাসির রোল উঠল ওদের মধ্যে।
কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।
৩
সকাল সকাল একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। অসময়ের বৃষ্টিতে ঠাণ্ডার ছোবল তীব্র হয়ে উঠেছে। কলকাতায় বেশ কয়েক বছর এত ঠাণ্ডা পরেনি, মাঘের শীত এবার সত্যি সত্যি বাঘের গায় লাগার মতো পরিস্থিতি। খদ্দরের চাদরটা দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে নিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল ছন্দা, হাঁটুর ব্যথাটা একটু কমেছে মনে হল। শীতের সময় এমনিতেই পুরোনো ব্যথাগুলো চাগাড় দেয়। কনকনে ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, তবু সামনের রাস্তার দিকে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল ছন্দা, ঘন কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক, বেলা না বাড়লে রোদের দেখা মিলবে না। ঝাপুর আসার সময় পেরিয়ে গেছে, আজকে আর আসবে কি না কে জানে! এমনিতে রোজ সারে সাতটার ভিতরেই চলে আসে, কুয়াশায় আটকে গেছে হয়তো। একবার ফোন করলেই ঝামেলা মিটে যায় কিন্তু ছন্দার ইচ্ছে করল না ফোন করতে, একবার না বলে দিলেই তো শেষ, তবু তো আসবে আসবে ভেবে একটা আশা জিইয়ে থাকে! ছেলেটা বেশ ভালো, চটপটে, বকরবকর করে কত কথা বলে, কোনো ভনিতা নেই, অসুস্থ বাবার কথা, প্রেমিকা মধুমিতার কথা, সে কীভাবে ওকে কথায় কথায় বোকা বানায় আর ও কীভাবে প্রতিবার নিজেকে বুদ্ধিমান প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেও ফেল মারে, কবে বিয়ে করবে মধুমিতাকে, নিজের একটা ছোট্ট ক্লিনিক খুলবে তার আগে, শুনে শুনে প্রায় সব কিছুই জানা হয়ে গেছে ছন্দার, তবু ভালো লাগে, নিজের মতো করে কেউ তো সব কিছু বলছে, এটাই তো মানুষকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসে, রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে। ঝাপু মোটামুটি আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট থাকে, মেশিন দিয়ে স্টিমুলেট করে হাঁটুতে, কখনো আলট্রা সাউন্ড দেয় ব্যথার জায়গায়। ডক্টর মিত্র ওকে পাঠিয়েছিলেন মাস তিনেক আগে। অর্থোপেডিকস-এর ট্রিটমেন্টে ফিজ়িয়োথেরাপি এখন অপরিহার্য। ব্যথা বাড়লে ঝাপুকে ডেকে নেয় ছন্দা, দিন পনেরো থেরাপি করে একটানা। ডাক্তারবাবু বলেই দিয়েছেন, “যে ক-দিন চলে চলুক, আলটিমেট সলিউশান মাইট বি নি রিপ্লেসমেন্ট, ভয়ের কিছু নেই, দিস ইস সো কমন নাউ।” ছন্দা জানে সার্জারিতে ঝামেলা অনেক, পোস্ট অপারেটিভ হ্যাজারডস নিয়েই চিন্তা বেশি। এই বয়েসে সেসব ঝক্কি সামলানো মুশকিল। বাড়িতে মানুষ বলতে তো ওই চামেলির মা, সে-ও বিকেল পর্যন্ত, তারপর থেকে ছন্দা প্রায় একাই বলা ভালো, রঞ্জন তো থেকেও না-থাকার সমান। দোতলায় আজকাল আর ওঠে না ছন্দা, বিশেষ করে সুমনা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে একদমই ওপরে ওঠা বন্ধ করে দিয়েছে। ডাক্তারবাবুও বলেছেন সিঁড়ি না ভাঙতে, হাঁটুর ক্ষয় যতটুকু আটকে রাখা যায়! দোতলাটা ছন্দা করেছিল ছেলে, ছেলের বউয়ের কথা ভেবে। মেয়ে হিসেবে সুমনা বেশ ভালো, ভালো পরিবারের শিক্ষিত মেয়ে, নিজে চাকরি করে, স্বাবলম্বী কিন্তু অত্যন্ত মিশুকে আর ঘরোয়া। বিয়ে রঞ্জন নিজে পছন্দ করেই করেছিল। ছন্দা কোনো কিছুতেই অন্তরায় হয়নি, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু রঞ্জনের নির্দয় আচরণ, নেশার বাড়বাড়ন্ত সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল, সুমনা চেষ্টা করেও পারেনি মানিয়ে নিতে, বছর দুয়েক পর বাধ্য হয়েই ঘর ছেড়েছে। ছন্দার মাঝে মাঝে নিজের ওপরেই রাগ হয়, নিশ্চই কোথাও কোনো ত্রুটি থেকে গেছে ওর দিক থেকে নাহলে ভালো স্কুলে পড়াশোনা করে, ঝকঝকে ক্যারিয়ার তৈরি করে একজন মানুষ এতটা নীচে নামতে পারে কীভাবে! প্রথাগত, পুথিগত শিক্ষা পেলেই কি মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে, না কি সব কিছুই নিয়তি, বুঝে উঠতে পারে না ছন্দা! নির্ঝরের আকস্মিক চলে যাওয়াটা কোনোদিন মেনে নিতে পারেনি ছন্দা, রঞ্জন তখন সবে ক্লাস সেভেনে, সেই থেকেই একা হাতে সব কিছু সামলেছে ও। যথার্থ চেষ্টা করেছে বাবার অভাব পূরণ করতে, যখন যেটা প্রয়োজন দিতে দু-বার ভাবেনি, কার্পণ্য করে কোনো কিছুতেই পিছপা হয়নি কখনো। বাবার অভাব পূরণ করতে গিয়ে হয়তো মায়ের কর্তব্যেই কোথাও গাফিলতি থেকে গেছে, মনের দিক থেকে সংবেদনশীল হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে ছেলেকে! অথচ সেইসব দিনগুলি কত অসহায়ভাবে কেটেছে সেটা শুধু মাত্র জানে ছন্দা নিজে। প্রবল আত্মসম্মান আর মনের জোরে নিজের লড়াইটা নিজেই লড়বে ঠিক করে নিয়েছিল ও, কোনো আত্মীয়স্বজনের কাছে সাহায্য চাইতে যাওয়ার কথা মাথায় আনেনি কখনো। মৃত্যুজনিত সুযোগসুবিধে পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে অনেকেই এগিয়ে এসেছিল কিন্তু অলিখিত শর্ত হিসেবে ফিরতি সুযোগের দাবি ছিল তাদের। সদ্য স্বামী হারা যুবতি মহিলার সম্পদের ভাগ নেওয়ার তাগিদ প্রায় সমস্ত পুরুষ মানুষের মধ্যেই লক্ষ করেছিল ছন্দা। নাবালক সন্তান নিয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যেও কাঠিন্য বজায়ে রেখে নিজের প্রয়োজন মতো সমস্ত কাগজপত্র একত্রিত করে জমা করেছিল অফিসে। তবে পাঁকের মধ্যেও যেমন পদ্ম ফোটে, তেমনি নিঃস্বার্থভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শশাঙ্ক চক্রবর্তী। গহীন দমবন্ধ করা গুহা পথের শেষে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছিল ছন্দা। শশাঙ্ক চক্রবর্তী ছিলেন নির্ঝরের অফিসের বড়ো সাহেব। মূলত ওঁর চেষ্টাতেই কিছুদিনের মধ্যেই সরকারি চাকরির নিয়ম মেনে ছন্দা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল দফতরে। সেই কৃতজ্ঞতা কোনোদিন মেটাতে পারেনি ছন্দা, কোনো দাবি ছিল না শশাঙ্কবাবুর দিক থেকেও। ধীরে ধীরে সম্পর্কের একটা জাল বুনে উঠেছিল নিজেদের অজান্তেই, পরবর্তীতে যা আবেগের গভীরতা ছুঁয়েছিল শিকড় পর্যন্ত কিন্তু শ্রদ্ধার বেড়াজাল টপকে তা কখনোই শরীরী ভালোবাসার স্তরে নেমে আসেনি। শশাঙ্কবাবু অত্যন্ত মার্জিত এবং সুস্থ রুচির মানুষ ছিলেন, বিপত্নীক মানুষ, একমাত্র মেয়েকে দায়িত্ব নিয়ে মানুষ করেছেন, আত্মীয় বন্ধুদের অনেক অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করেছেন নির্দ্বিধায়, দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেননি শুধুমাত্র মেয়ের কথা ভেবে। অভিভাবক বলতে ছিলেন শুধু মা, মূলত ঠাকুরমার কাছেই বেড়ে ওঠে ছোট্ট মেয়েটি। ঠাকুরমা আদর করে নাম রেখেছিলেন আপেল, যদিও ওই নামে মেয়েকে ডাকতেন শুধু শশাঙ্কবাবু নিজেই, বাকিদের কাছে সে ছিল রুপালি। খুব অল্প বয়েসে স্ত্রীর মৃত্যুতে ভেঙে পরেছিলেন শশাঙ্ক বাবু, কোলকাতায় বাড়ি কিনে থাকার সখ ছিল স্ত্রী মুক্তারানির। পুরোনো কলকাতায় মুরারিপুকুরে একটা বাড়ি দেখাও হয়ে গিয়েছিল, আড়াই কাঠার ওপর বেশ ছিমছাম বাগান ঘেরা ছোট্ট একতলা বাড়ি। বায়নার দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার আগেই হঠাৎ করে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন মুক্তারানি, দু-দিনের জ্বরে সব শেষ হয়ে গেল। সেভাবে চিকিৎসার সুযোগটুকু মেলেনি, হাসপাতাল বলেছিল, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া, মাল্টি অর্গান ফেইলিওর। ছোট্ট আপেলকে বুকে জাপটে সব কিছু ভুলতে চেয়েছেন শশাঙ্কবাবু। সারাজীবন সরকারি আবাসনে কাটিয়েছেন, রিটায়ারমেন্টের আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন জাঁকজমক করে। তারপর ঝাড়া-হাত-পা হয়ে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মেয়ে ছাড়া সব থেকে কাছের মানুষ বলতে ছিল ছন্দা, কিন্তু আশ্চর্যভাবে এই সম্পর্কের কথা কোনোদিন কেউ জানতে পারেনি ঘুণাক্ষরেও। ছন্দাও মনের মানুষ হিসেবে মেনে নিয়েছিল শশাঙ্কবাবুকে। এত বছরে কোনোদিন কেউ কারুর বাড়িতে আসেনি, যেটুকু দেখাসাক্ষাৎ হত অফিসের লাইব্রেরিতে নয়তো অফিসের বাইরে ধর্মতলার কাছে চারু কেবিনে। ছেলে মেয়েদের একা রেখে সম্ভব ছিল না দু-জনে একত্রে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার। ছন্দা নিজেকে মেলে ধরতে চেয়েছে কখনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে, ইচ্ছে হয়েছে সভ্যতার বেড়াজাল টপকে অকৃত্রিম আদিমতার স্বাদ নিতে, অদমিত যৌবনের বাঁধভাঙা উচ্ছাস সংবরণ করতে করতে হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছিল ভিতরে ভিতরে কিন্তু শশাঙ্কবাবু সম্মত হননি, তিনি ছন্দাকে এক অনন্য সাধারণ মহিলা হিসেবে দেখতেন, এই সম্পর্কটা ওঁর কাছে ছিল অন্য মাত্রার, একে তিনি কখনোই ঠুনকো শরীরী চাহিদার পানা পুকুরে নিমজ্জিত করতে চাননি। সংযমী শশাঙ্কবাবু বলতেন, “দেখো ছন্দা, একে বলে স্টোইক লাভ, দুটো সম্পৃক্ত মনের অনন্ত মিল হলে শরীরী চাহিদা নেহাতই তুচ্ছ হয়ে যায়, আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসি কিন্তু শ্রদ্ধা করি তার থেকেও বেশি। নিজেকে শাসন করতে পারি বলেই তো আমরা মানুষ, পশু নই।” শশাঙ্কবাবুর মৃত্যুর পর থেকে ছন্দা মানসিকভাবে একা হয়ে পড়েছে। রঞ্জন থেকেও নেই। নামি স্কুলের কৃতি ছাত্র, গর্ব করার মতো ক্যারিয়ার তৈরির পর বহুজাতিক কোম্পানির চাকরি, এইপর্যন্ত সব কিছু ঠিকই ছিল কিন্তু মানুষ যে কারণে মানুষ বলে বিবেচিত হয়, রঞ্জন সেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়েছে একটা একটা করে। চেষ্টা করেও ছেলেকে শোধরাতে পারেনি ছন্দা। মাসে দুই থেকে তিন দিন দোতলায় মজলিস বসিয়ে ফুর্তি করাটা প্রায় নিয়মে পরিণত করেছে রঞ্জন, ছন্দার নিষেধ কানে তোলেনি কোনোদিন। চেষ্টা কম করেনি সুমনা নিজেও কিন্তু হাল ছাড়তে হয়েছে তাকেও, মন থেকে যে মানুষ চেতনা খুইয়েছে, যার মনুষ্যত্ব বোধ নষ্ট হয়ে গেছে, তেমন মানুষের সঙ্গে একসাথে থাকা চলে না। অতিরিক্ত নেশা আর লাগামহীন নারীসঙ্গ মেনে নিতে পারেনি সুমনা। এদিকে টাকার চাহিদা পূরণের তাগিদে মায়ের জমানো টাকা পর্যন্ত সব তুলে নিয়েছে কায়দা করে। ছন্দার সম্বল বলতে এখন শুধু এই দোতলা বাড়ি আর পেনশানের টাকা। পেনশানের টাকা আর এম আই এস থেকে যা পাওয়া যায় তাতে ছন্দার চলে যায় অনায়াসে। বয়েসকালে চাহিদাগুলো এমনিতেই কমে আসে, ডাক্তার আর ওষুধ ছাড়া খরচা তেমন একটা নেই প্রায়। আজকাল অবশ্য ঝাপুর জন্য একটা টাকা ধরে রাখতে হয়। সুমনা বাড়ি ছাড়লেও ছন্দার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি, মাঝে মাঝেই ফোন করে খবর নেয় ছন্দার, “টাকাপয়সা লাগলে জানাবে, একদম হেজ়িটেট করবে না কিন্তু, আমাকে তো তুমি…।” গলা ধরে আসে সুমনার। ছন্দা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, “তুই তো আমার মেয়েই, তোর কাছে আবার লজ্জা কী, দরকার হলে বলব নিশ্চয়ই, ভালো থাকিস মা।” ছন্দার গলা ধরে আসে, নিজের অকাল বৈধব্যর কষ্ট বুকে চেপে কাটিয়েছে সারাটা জীবন কিন্তু এই মেয়েটার তো সব কিছু থেকেও নেই, সুমনার কষ্টটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয়না ছন্দার। মানুষের জীবন বড়ো বিচিত্র, বিধাতা পুরুষ প্রত্যেকের জীবন আলাদা আলাদা চিত্রনাট্যের ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন। দুনিয়ায় শশাঙ্কবাবুর মতো মানুষও আছেন যাঁরা সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী আবার রঞ্জনের মতো মানুষও আছে যারা শুধু ভোগবিলাসেই জীবনের মানে খুঁজে পায়। আসলে হয়তো-বা কিছুই পায় না, অন্ধ গলির শেষ প্রান্তে পৌঁছে সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ করে পরিশ্রান্ত হয়ে হারিয়ে যায় জীবন থেকেই। অনিয়ন্ত্রিত জীবনে টাকার অভাব কখনো মেটে না, তবে রঞ্জন যে এত নীচে নামবে সেটা ভাবেনি ছন্দা। মাসখানেক হল, মায়ের কাছে হাজার বিশেক টাকা চেয়েছিল রঞ্জন। ছন্দা রাজি হয়নি টাকা দিতে, এমনিতেও হঠাৎ করে এত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না, ঘরে টাকা যেটুকু থাকে তা সামান্য, মাসের শুরুতে হিসেব করেই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনে ছন্দা। আর রঞ্জনকে টাকা দেওয়া মানে ওকে আরও সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া। সেদিন রাতে ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছিল, একটু আগেই রাতের খাওয়ার খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছিল ছন্দা, ঘুমিয়েও পড়েছিল চটপট কম্বল মুড়ি দিয়ে। রঞ্জনও কিছুটা আগেই বাড়ি ফিরেছিল সেদিন, সোজা দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ছন্দা এখন ছেলের কোনো ব্যাপারেই থাকে না, একই বাড়িতে দুটি বিচ্ছিন্ন মানুষের মতো জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পরেছে ধীরে ধীরে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কিছু খেয়াল করেনি, ঝাপু আসার পর ব্যাপারটা নজরে আসে ছন্দার। সাত দিন পরে পরে ঝাপুর হাতে টাকা দিয়ে দেয় ছন্দা, ও নিতে চায় না, বলে, “থাক না আন্টি, এক মাস করি, তার পরে দিয়ো।” ছন্দা ধমক লাগায়, “তুমি কি চাইছ বলো তো? আমি দিনের পর দিন থেরাপি করতে থাকি আর তুমি ক্লিনিকের টাকাটা আন্টির থেকেই তুলে নাও?” তারপর হেসে বলে, “এত টাকা একসাথে দিতে গায় লাগে বাপু, সাত দিন পরে পরে দিয়ে দিলে বোঝা কমে যায়।” ঝাপুকে টাকা দেওয়ার জন্য আলমারি খুলতেই ছন্দা বুঝতে পারে লকারে থাকা কাগজপত্রগুলো কেউ ঘেঁটেছে ইচ্ছেমতো। ছোটো পার্সে রাখা টাকাগুলো বেচে গেছে ঠিকই তবে বেশ কিছু দরকারি কাগজ, যার মধ্যে একটি দরকারি নথি আর একটি চিঠি ছিল, খোয়া গেছে লকার থেকে। ছন্দার বুঝতে বাকি থাকল না এটা কার কাজ, রাতের দিকে নিশ্চয়ই ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিল রঞ্জন, টাকার জন্য ছেলেটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। শেষে এটাই বাকি ছিল। মরমে মরে গেল ছন্দা, ঝাপুকে কিছু বুঝতে দেওয়া যায় না, ওর হাতে টাকাটা দিয়ে ওকে ছেড়ে দিল সময়ের আগেই। লকারটা ভালো করে খুঁজে দেখল ছন্দা, দরকারি কাগজপত্রের মধ্যেই চিঠিটা আর দরকারি নথিখানা গুঁজে রেখেছিল ছন্দা, শশাঙ্কবাবুর নিজের হাতে লেখা চিঠি। ছন্দার মাথা দপদপ করে উঠল, ওই চিঠিটা রঞ্জনের হাতে পড়া মানে একপ্রকার অনর্থ বলা যায়! এই বয়েসে এসে কোনো কিছুতেই আর ভয় পায় না ছন্দা, শশাঙ্কবাবু মারা গেছেন তাও প্রায় বছর চারেক হল আর ওঁর সঙ্গে সম্পর্কের যে সুতোয় বাঁধা ছিল ছন্দা তাতে শুধুই পারিজাতের পবিত্রতা। এতদিন পরে কেউ সেসব নিয়ে প্রশ্ন তুললেও তাতে কিছু এসে যায় না ওর। লকারের আনাচে-কানাচে তন্নতন্ন করে খুঁজেও চিঠিটা পেল না ছন্দা, সঙ্গের নথিটাও উধাও। মনটা খারাপ হয়ে গেল, মানুষটার শেষ স্মৃতিটুকুও ছাড়ল না রঞ্জন; ভয় হোল, সব কিছু করায়ত্ত হওয়ার পর কী করবে রঞ্জন! কিছু একটা করতে হবে যাতে ওকে ঠেকানো যায়। অনেক ভেবে রাইটিং প্যাডটা নিয়ে বসল ছন্দা, ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা লিখতে হবে গুছিয়ে, দেখা যাক কতটা কী করা যায়!
কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।
এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।
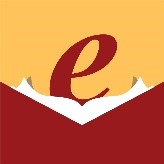






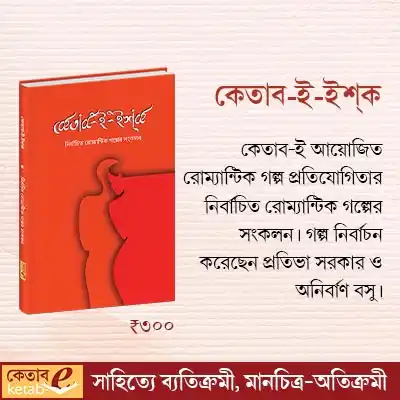
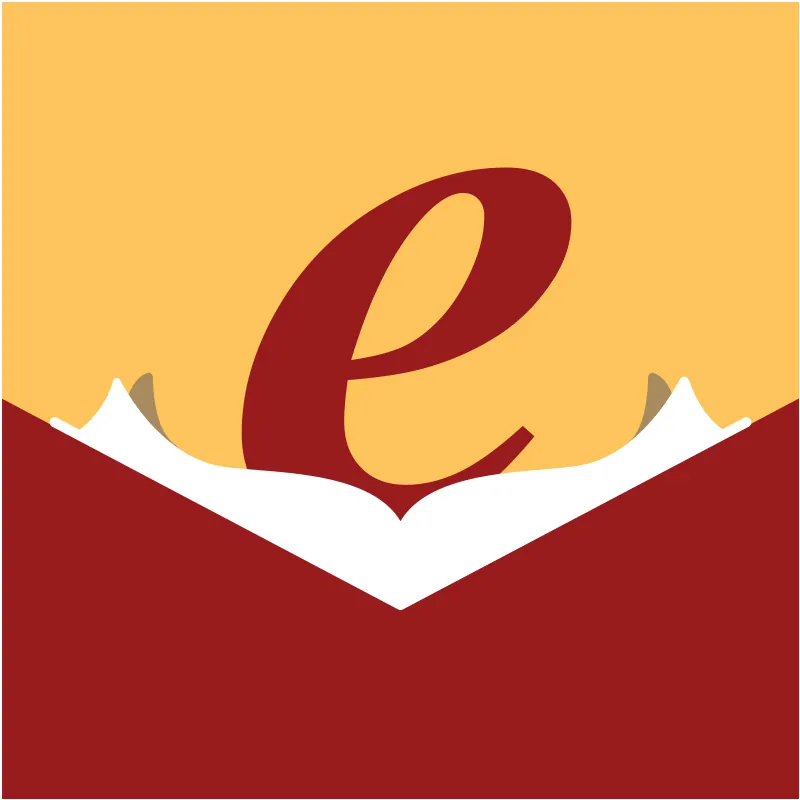
Pramit Kumar Ganguly
6 মাস আগেস্যার, অসাধারণ। পরের পর্ব কোথায় পাবো?
Srabani das
5 মাস আগেরুপুর চরিত্র টা খুব মনে ধরানো এবং প্রতি টা শব্দ খুবই মনোগ্রাহী।